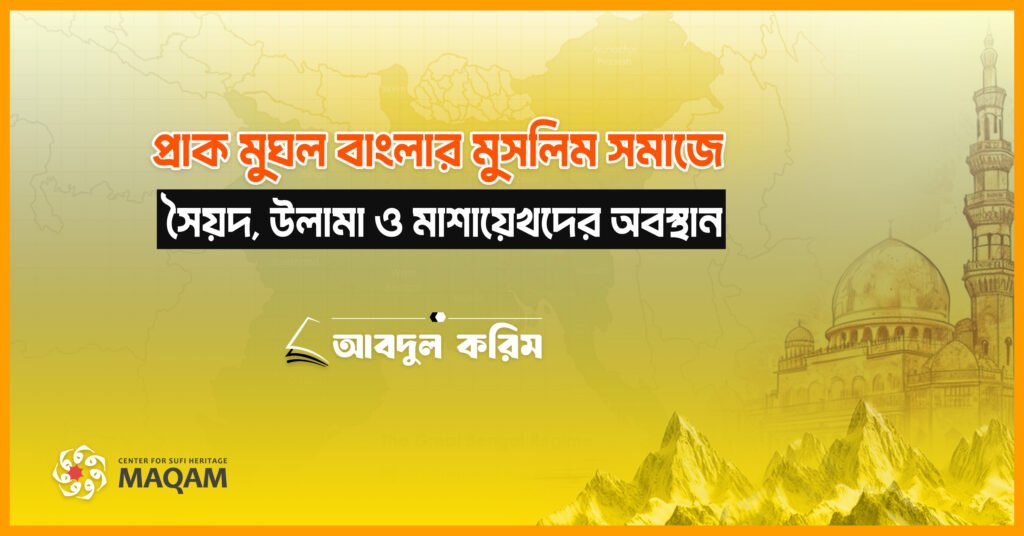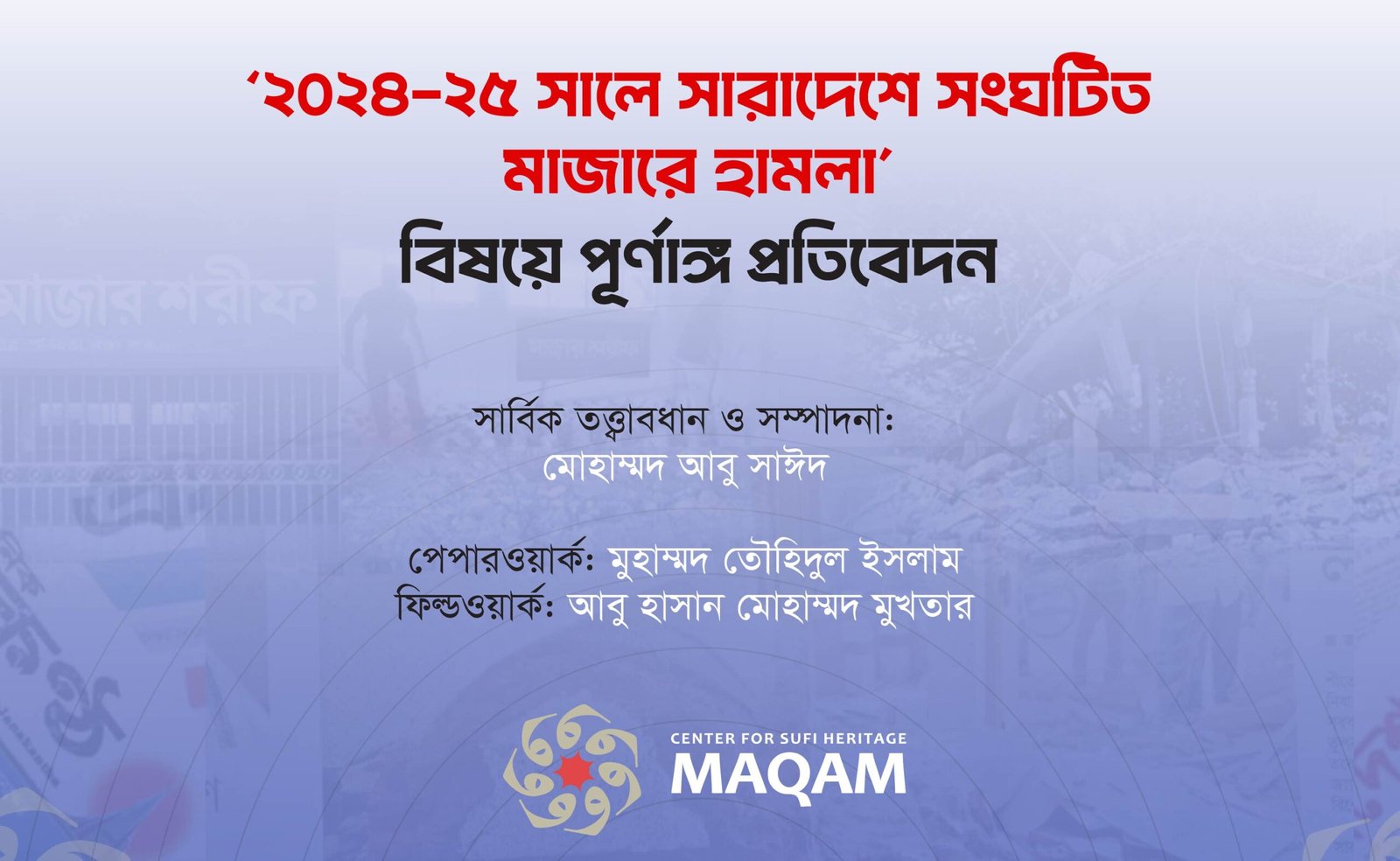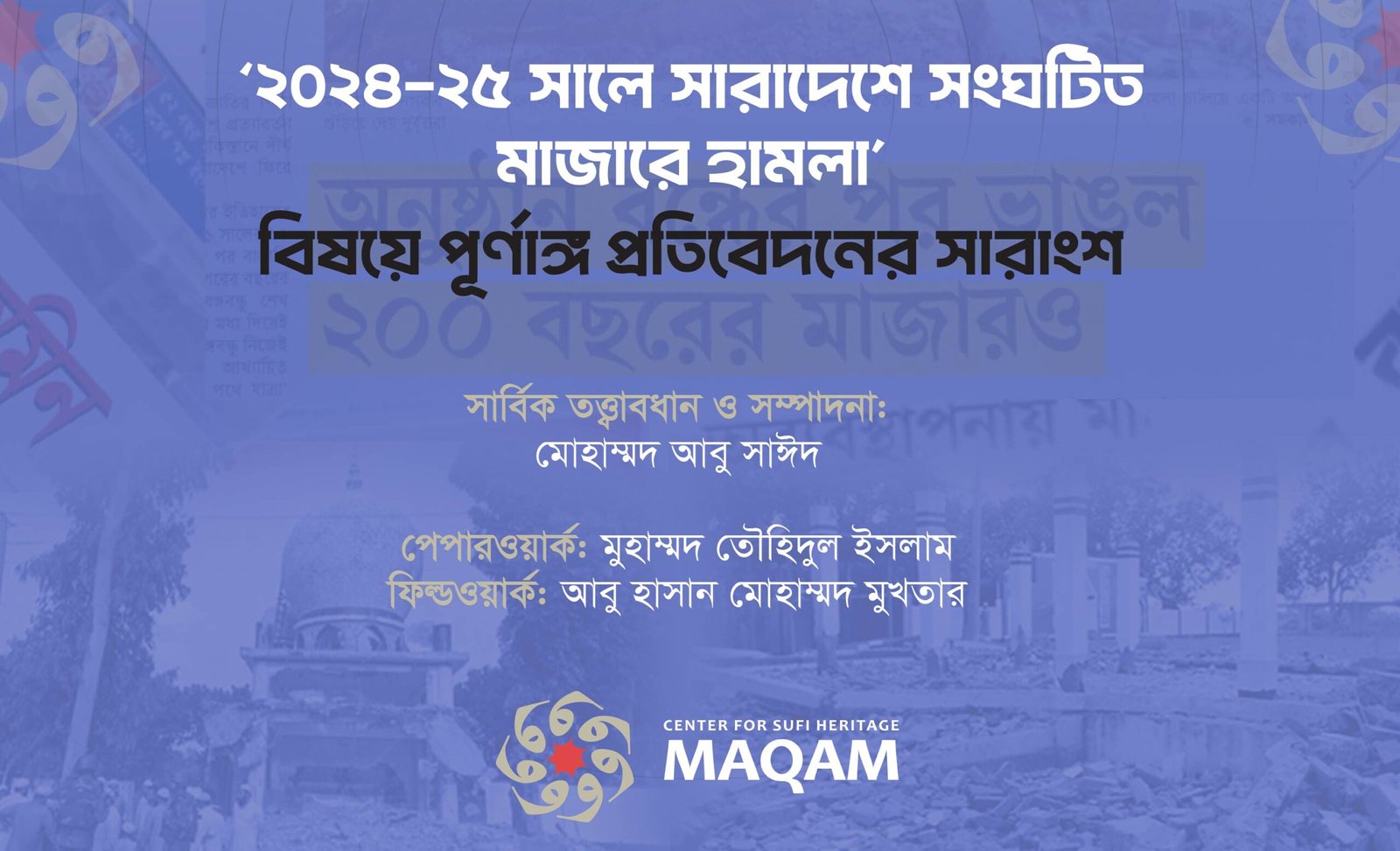সম্পাদকের নোট:
১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে একটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে অধ্যাপক আবদুল করিম The Sadat, Ulama and Mashaikh in Pre-Mughal Muslim Society of Bengal শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইতোপূর্বে এই প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো।
অক্ষরের চেয়ে ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আবদুল করিম প্রদত্ত রেফারেন্স হুবহু রাখা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে, মূল বক্তব্য ঠিক রেখে প্রাঞ্জল অনুবাদের। বাকিটা পাঠক ভালো বলতে পারবেন।
***
বাংলায় মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠা একটি সুদীর্ঘ ও ধারাবাহিক বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার ফলাফল। বাংলার মাটিতে প্রথম যে মুসলিম জনগোষ্ঠী পদার্পণ করেন, তারা ছিলেন আরব বণিক, যারা তাদের বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক অভিযাত্রার সূত্রে অষ্টম শতাব্দী থেকে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে—বাংলাসহ—আগমন করতে থাকেন। তবে এই আরব মুসলিম বণিকেরা বাংলার অভ্যন্তরে কতটা প্রবেশ করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।
মাহিসাওয়ারসহ একদল মুসলিম সাধকের সমুদ্রপথে আগমন এবং মুসলমান শাসনের পূর্ববর্তী যুগে ইসলাম প্রচারের নানা কাহিনী এদেশে জনপ্রিয় হলেও, এর সত্যতা যাচাই বা কোনো নির্দিষ্ট কালপঞ্জিতে স্থান নির্ধারণ করা কঠিন। সমসাময়িক দেশীয় সাহিত্য ও শিলালিপিতে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকায় এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এমনকি যদি এসব কাহিনীতে কোনো সত্যতা থেকেও থাকে, তবে ঐ যুগের সুফিদের প্রভাব সমাজে খুব সীমিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।
তবে পরবর্তী সময়ে ইসলাম বাংলার সমাজের সামাজিক-ধর্মীয় জীবনে এক নতুন এবং শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়—বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি বিজয়ের ফলে। তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার পর বহু মুসলমান এই নব-অধিকৃত ভূখণ্ডে ভাগ্যের সন্ধানে আসেন। বিজেতাদের বহরে আগত সৈনিকেরা, তাদের পরিবার-পরিজন ও বিশ্বস্ত সহচর, দিল্লি থেকে আগত গভর্নরবৃন্দ ও অনুসারী অনুচর—সবাই এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা শুরু করেন।
পাশাপাশি সম্পূর্ণ বেসামরিক উদ্দেশ্যে আগমন করেন সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখ; বাণিজ্যিক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের মুসলিম বণিক; কারিগরি ও হস্তশিল্পে পারদর্শী মুসলিম শিল্পী ও কারিগররাও জীবিকার সন্ধানে বাংলায় এসে বসতি গড়েন। এ-সকল গোষ্ঠীর মিলনের ফলেই বাংলার সমাজে মুসলিম উপাদানের ভিত্তি গড়ে ওঠে।
সময়ের সঙ্গে সমাজ আরও দুটি উপাদানে পরিপুষ্ট হতে থাকে—স্থানীয় ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠী এবং আন্তঃবিবাহের পরিবার/সন্তানসন্ততি। প্রাথমিকভাবে বাংলার মুসলিম সমাজে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখ—এই তিন গোষ্ঠীকে আমরা নির্বাচন করেছি প্রাক-মুঘল বাংলায় তাঁদের অবস্থান নিরূপণের উদ্দেশ্যে।
প্রশ্ন হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে সামাজিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হলো? ইসলামি নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, একজন মুসলমান ও আরেকজন মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদরেখা থাকার কথা নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: “হে মানবজাতি, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাত।”[1] অতএব, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয় তাকওয়ার মাত্রা এবং জাতি বা গোত্রের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে। এই পার্থক্য আধুনিক সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থে শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করে না, কিংবা হিন্দুধর্মে প্রচলিত জাতিভেদব্যবস্থার অনুরূপও নয়।
তবে বাস্তব জীবনে অভিন্ন স্বার্থ বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কিছু গোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। বাংলায় এ ধরনের গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইনশা-ই-মাহরু–তে, যেখানে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের একটি ঘোষণাপত্র সংরক্ষিত আছে।[2] এই ঘোষণাপত্রে পান্ডুয়ার একদল জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয় যেন তারা সুলতান ফিরোজ শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী—বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে দিল্লির সুলতানের সহায়তায় এগিয়ে আসে। ঘোষণাপত্রটি নিম্নোক্ত গোষ্ঠীসমূহকে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত হয়েছিল:
১) সৈয়দ, উলামা, মাশায়েখ এবং সমমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ;
২) খান, মালিক, উমারা, সদর, আকাবির ও মারিফ;
৩) ২ নং-এর দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ;
৪) জমিদার, মোকাদ্দাম, মাফরুজমাউ, মাদকান ও অনুরূপ শ্রেণির লোক;
৫) সন্ন্যাসী ও সাধু।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের এই ঘোষণাপত্র একটি সরকারী স্মারক; রাজধানীর জনগণকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভাজনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দলিলে আমরা এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণির পরিচয় পাই, যারা রাজকীয় ঘোষণায় স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। তারা ছিলেন সেইসব মানুষ, যাদের সহায়তা ও সহযোগিতা দিল্লির সুলতান বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে চেয়েছিলেন। অতএব স্পষ্টতই এই গোষ্ঠীগুলিই সমাজের উচ্চশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতো। এ দলিলের সহায়তায় সমাজে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব।
দলিলে প্রদত্ত অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও, ১, ২ ও ৩ নং শ্রেণী প্রসঙ্গে ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে “তাদের জায়গীর, গ্রাম, ভূমি, ভাতা, মজুরি ও বেতন” বৃদ্ধি করা হবে। পরিষ্কারভাবেই এগুলো ছিল বর্ণিত ব্যক্তিদের আয়ের মূল উৎস। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আমরা সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখদের সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারি; অর্থাৎ যাদের সাধারণত আহল-ই-কলম বা আহল-ই-সৈয়দ নামে অভিহিত করা হতো।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদেরকে একত্রে একই গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সমাজের অন্যান্য উচ্চশ্রেণির সদস্যদের তুলনায়—এমনকি খান, মালিক, উমারা প্রভৃতিরও ঊর্ধ্বে—তাদের অগ্রগণ্য মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। অন্যকথায়, সমাজের যেসব গোষ্ঠী সাধারণত আহল-ই-তেগ বা আহল-ই-দাওলত নামে পরিচিত ছিল, তাদেরও উপর সৈয়দ, উলামা ও মাশায়েখদের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল।
মুসলিম সমাজের উচ্চশ্রেণি সম্পর্কে অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাস রচিত মনসা বিজয়া গ্রন্থে, যা রচিত হয় ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে।[3] সাতগাঁও অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি যেসব গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো:
১) মঙ্গোল, পাঠান এবং মুকাদ্দিম (মখদুম);
২) সৈয়্যদ, মোল্লা এবং কাজী।
এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ, যা একজন হিন্দুর লেখা থেকে এসেছে, যার মুসলিম সমাজের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার কথা ছিল না, তিনি রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু দূর থেকে এ দৃশ্যটি দেখতে পেতেন। কবি এই সমস্ত লোককে সাধারণ শব্দ ‘যবন’ বলে অভিহিত করেছেন এবং মঙ্গোল, পাঠান এবং মাখদুমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মঙ্গোল এবং পাঠানরা ছিল ক্ষমতার অধিকারী, অর্থাৎ যারা আহল-ই-দৌলত বা আহল-ই-তেগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দুদের কাছে, তারা আরও শক্তিশালী ছিল, সম্ভবত ভয়ঙ্করও ছিল। শেখদের আরেকটি নাম মাখদুম, হিন্দু কবির কাছে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী ছিল, কারণ, তাদের ধর্মান্তরিতকরণের কাজে মাখদুমরা অমুসলিমদের কাছাকাছি এসেছিলেন। মাখদুমদের উপর আরোপিত অতিমানবীয় (কারামত) শক্তিও তাদের অমুসলিমদের কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মাখদুম, সৈয়দ ও মোল্লা (‘আলেম’ বোঝানোর জন্য আরেকটি শব্দ) সহ ফিরোজ শাহের ঘোষণার প্রথম শ্রেণীতে পাওয়া লোকদের একই দল ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট যে, বিপ্রদাস বাংলার মুসলিম সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং মঙ্গোল ও পাঠান ছাড়া বাকি সকল দল অর্থাৎ সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখরা আহলে-ই-কলমদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সৈয়দরা ছিলেন নবীর বংশধর, উলামা বা আলেমরা ছিলেন ইসলামী বিজ্ঞান বা ধর্মতত্ত্বে সুপরিচিত। উলামারা ছিলেন মুসলিম আইন, যুক্তি, আরবি লিপি এবং হাদিস, তাফসির ও কালামের মতো ধর্মীয় সাহিত্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মাশায়েখ বা শেখরা ছিলেন সুফি-দরবেশ যারা তাদের আধ্যাত্মিক অর্জন সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। তুর্কি বিজয়ের শুরু থেকেই এই দলগুলি বাংলায় এসেছিল। মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং মুসলিম সমাজের বিকাশের সাথে সাথে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লি সালতানাতের মুসলিমদের ধর্মীয় শ্রেণীর মধ্যে, কানওয়ার মুহাম্মদ আশরাফ লিখেছেন, “মুসলমানদের ধর্মীয় শ্রেণী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যেমন ধর্মতত্ত্ববিদ, তপস্বী, সৈয়দ সৈয়দ, পীর এবং তাদের বংশধর। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মতত্ত্ববিদ যারা রাজ্যের বিচার বিভাগীয় এবং অন্যান্য ধর্মীয় অফিসগুলিতে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছিলেন। তারা সম্মিলিতভাবে দস্তর-বন্দ বা পাগড়ি পরিধানকারী নামে পরিচিত ছিল, কারণ তাদের সরকারী পোশাক ছিল পাগড়ি। সৈয়দরাও একটি স্বতন্ত্র পাগড়ি, কুলাহ বা সূক্ষ্ম টুপি ব্যবহার করতেন এবং তারা কুলাহ-দারান বা টুপি পরিধানকারী নামে পরিচিত ছিলেন। এই দুটি গোষ্ঠীর পোশাকেই স্বতন্ত্র পাগড়ি অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ তারাই মূলত ইসলামের প্রবক্তা।”[4] বাংলায়, সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা এবং অন্যান্য দলিলের অভাবে আমরা সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখদের সামাজিক বা সরকারী অবস্থানের কোনও স্পষ্ট চিত্র তৈরি করতে পারছি না। তবে পরিস্থিতি খুব বেশি আলাদা হতে ছিল না। কারণ, প্রায় দুইশ বছর ধরে দিল্লি এবং বাংলার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যখন বাংলা প্রায়শই দিল্লি সালতানাতের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি যখন বাংলা স্বাধীন হয়েছিল তখনও দিল্লিতে মুসলমানদের অবাধ যাতায়াত ছিল। শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত লোকদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য ছিল। সমসাময়িক বিভিন্ন বর্ণনায় বাংলার মুসলমানদের পরিধেয় হিসেবে পাগড়ি এবং টুপির উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকের কবি বিজয় গুপ্ত মোল্লাদের পাগড়ি পড়া বর্ণনা করেছেন।[5] বিদেশী ভ্রমণকারীরাও পাগড়িকে মুসলমানদের পাগড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছেন; চীনা ভ্রমণকারীরা এবং পর্তুগিজ ভ্রমণকারী বারবোসাও উচ্চপদস্থ মুসলমানদের ব্যবহৃত সাদা সুতির পাগড়ির কথা বলেছেন।[6] অন্যদিকে, মুকুন্দ রাম একটি নির্দিষ্ট বসতির বর্ণনা দিয়ে ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন মুসলমানদের পোশাকের বর্ণনায় দশটি টুপির কথা বলেছেন।[7] সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মাওলানা মুজাফফর শামস বলখীকে একটি পাগড়ি উপহার দিয়েছিলেন। মাওলানা একজন মহান ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন, কিন্তু উপহার গ্রহণের সময় তিনি শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরীর শিষ্য ও একজন মহান সাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[8] শেখরা সাধারণত খালি পোশাক পড়তেন, সাধারণত তারা কালো কাপড় ব্যবহার করতেন। শেখ জালাল-উদ্দিন তাবরিজি কালো পোশাক পরে বাংলায় এসেছিলেন, মাথায় পাগড়ি এবং হাতে একটি আসা (লাঠি) ছিল।[9] কৃষ্ণ দাস কবিরাজ একটি নির্দিষ্ট তুর্কি বংশের কথা উল্লেখ করেন যেখানে পীর কালো পোশাকে নেতৃত্ব দিতেন।[10] তাই কেবল উলামা বা উলামাদের অফিসিয়াল ক্লাসই নয়, বরং পীর-মাশায়েখরাও পাগড়ি ব্যবহার করতেন। অতএব, এটা বলা সম্ভবত সঠিক নয় যে পাগড়ি বা দস্তর একটি অফিসিয়াল বিষয় ছিল। আজ যেমন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাবর্তন নামে একটি সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান হয়, তেমনি ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, যারা সফলভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করেন তাদের দস্তর বা পাগড়ি প্রদানের জন্য একটি দস্তরবন্দ অনুষ্ঠান হয়। যে কেউ তার শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাগড়ি গ্রহণ করতেন। তিনি পরবর্তী জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করুন না কেন তা ব্যবহার করার অধিকার তার ছিল।
সৈয়দরা ছিলেন নবীর বংশধর এবং তারা জন্মগতভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তারা যদি ইসলামী বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করতে পারতেন অথবা আধ্যাত্মিকভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারতেন তাহলে তারা আলেম বা শেখ হতে পারতেন। একইভাবে আলেমরাও নবীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন অথবা তাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের সাথে শেখ হতে পারতেন। শেখরাও সৈয়দ হতে পারতেন, অর্থাৎ নবীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন এবং তারা সাধারণত সকলেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন। তাই তাদের শান্তিপূর্ণ সাধনায় সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখ এই তিনটি দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সূক্ষ্ম; অবশ্যই, যদি তারা সরকারী এবং বেসরকারী শ্রেণীর হন তবে অবস্থান ভিন্ন ছিল। তবে দিল্লির ক্ষেত্রে আহলে-তেগ বা উমারা গোষ্ঠীর তুলনায় তারা সাধারণত আহলে-ই-কলম নামে পরিচিত ছিলেন, যেমনটি উমারা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে হয়েছিল।
বাঙালি সুলতানরা দেশ-বিদেশের সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দিল্লিতেও প্রবাসী মুসলমানদের স্বাগত জানানো হয়েছিল; যারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাদের যথাসম্ভব উপযুক্ত কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছিল।[11] বাংলার প্রথম বিজয়ী বখতিয়ার খলজী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীরাও একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আলী মর্দান খলজীর রাজত্বকালে, কাজী রুকনুদ্দীন সমরকান্দি ছিলেন তার কাজী যিনি একজন মহান আলেম এবং সুফি ছিলেন; তিনি কামরূপের একজন যোগী ব্রাহ্মণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তিনি যোগি গ্রন্থ অমৃতকাণ্ডকে ফারসি ও আরবি ভাষায় বাহার-উল-হায়াত এবং হাউজ-উল-হায়াত শিরোনামে অনুবাদ করেছিলেন।[12] ইওয়াজ খিলজির রাজত্বকালে জামালউদ্দিন গজনবীর পুত্র মাওলানা জালালউদ্দিন লখনৌতিতে আসেন। সুলতানের সভাকক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। সুলতান এবং তার অভিজাত সভাসদরা তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন।[13]
নবীর বংশধর হওয়ায় সৈয়দদের সাধারণ জনগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজী সৈয়দ, আলেম এবং শেখদের পেনশন এবং ভাতা দিতেন। খুলনা-যশোর অঞ্চলের প্রথম মুসলিম বিজয়ী বাগেরহাটের খান জাহান নিজেকে `নবীর বংশধরদের প্রেমিক’ বলে দাবি করেন।[14] উনিশ শতকের চট্টগ্রামের ইতিহাসবিদ মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বলেছেন যে, নবীর পরিবারের একজন আরব ব্যবসায়ী আলফা হুসাইনি তার অনুসারীদের নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন এবং বাংলার রাজা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[15] চারজনের সমন্বয়ে গঠিত সৈয়দ রাজবংশ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাংলা শাসন করেছিল। শিলালিপিতে প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী, এই শাসকরা তাদের জন্মের/বংশের জন্য গর্বিত ছিলেন: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কেবল নিজেকে সৈয়দ বলেই দাবি করেননি বরং ‘সৈয়্যদের সৈয়দ’ (সৈয়দুস সাদাত), ‘নবীর সঙ্গে সংযুক্ত’ (আল মানসুবি ইলা হাজরাতি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেও দাবি করেছেন।[16] এমনকি নুসরত শাহের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা সৈয়দ ফখরুদ্দিন আমুলির পুত্র সৈয়দ জামালউদ্দিন নিজেকে ‘সৈয়দের আশ্রয়স্থল’ এবং ‘নবীর বংশধরদের গর্ব’ বলে গর্ববোধ করেছেন।[17] ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন বাঙালি কবি সৈয়দ সুলতান বাংলা ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন।[18] এতে প্রতীয়মান হয় যে, সৈয়দরা কেবল এই দেশে বসতিই স্থাপন করেননি বরং স্থানীয় ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। এভাবে সৈয়দরা বিভিন্ন সময়ে বাংলায় এসেছিলেন। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানরা যে কোনো ক্ষেত্রেই তাদের যথাযথ সম্মান করতেন।
আলেম শব্দের অর্থ জ্ঞানী, কিন্তু পারিভাষিক অর্থ হল এমন ব্যক্তি যিনি ধর্মতত্ত্ব বা ইসলামী বিজ্ঞানে সুপরিচিত। যে ধর্মতত্ত্বে দক্ষতা অর্জন করতে পারত তাকে আলেম বলা হত। বলা হয় যে, একজন যোগী ব্রাহ্মণ ইসলামী বিজ্ঞান এত ভালোভাবে শিখেছিলেন যে মুসলিম ধর্মগুরুরা তাকে আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন।[19] সাধারণত আলেমরা শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতেন। সৈয়দ সুলতান একজন আলেমের নিম্নলিখিত কর্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন:
দেসে ত য়ালিম থাকি জদি না জানাএ।
সে য়ালিম নারকে পড়িব সর্বথায়।।
নর সবে পাপ কৈলে য়ালিমেক ধরি।
য়াল্লার সাক্ষাতে মারিবেন্ত বেড়াবাড়ি।।[20]
অন্য এক জায়গায় সৈয়দ সুলতান ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি বাংলায় লেখেন। তিনি বলেন যে, বাংলায় বসবাস করা মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্য। তারা আরবি ভাষা জানে না, তারা কিতাব ও কুরআনও বোঝে না। তাই, আলেমদের উপর নির্ভর করে বাংলায় ধর্মীয় বিষয়ের উপর বই লেখা যাতে বাঙালি মুসলমানরা সেগুলো বুঝতে পারে। সৈয়দ সুলতানের জীবন ও পরিবেশের প্রতি অবশ্যই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তিনি এবং তাঁর সময়ের আরও অনেকেরই এমন একটি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা ছিল না যা আধুনিক যুগেও অনেকে ‘পৌত্তলিকতা’ বলে মনে করতেন। সেই সময়ের মুসলমানরা যে ভাষাই পাওয়া যায় না কেন, শিখতে দ্বিধা করতেন না। এমনও উদাহরণ আছে যে আলেমরা নিজেরাই মাদ্রাসা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষাদান করতেন। মাওলানা তাকিউদ্দিন আরাবী মাহিসুনে একটি মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন; তার প্রধান শিষ্য মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও মাদ্রাসায় পড়াতেন। অনেক ছাত্র তার পাঠদানে অংশ নিতেন এবং তার প্রধান শিষ্য ছিলেন শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরি।
তবকাত-ই-নাসিরিতে বখতিয়ার খলজী এবং তার উত্তরসূরীদের দ্বারা মাদ্রাসা নির্মাণের সাধারণ উল্লেখ ছাড়াও, এমন কিছু শিলালিপি রয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটি রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে কাজী নাসির মুহাম্মদ, দ্বিতীয়টি শামস-উদ্দিন ফিরোজের রাজত্বকালে এবং শেষ দুটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল।[21] এই মাদ্রাসাগুলোতে বিদ্বান আলেমদেরকে নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল।
আইনে পণ্ডিত আলেমদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত করা হত। তারা কাজী, শায়খ-উল-ইসলাম বা সদর বা সদর-উস-সুদুর’র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[22] ফিরিশতার মাধ্যমে জানা যায় যে, সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ’র সময়ে সময়ে আলেমদেরকে ডেকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে কোনও পক্ষপাতিত্ব না করার জন্য সতর্ক করা হতো।
এছাড়াও, কিছু রাষ্ট্রীয় কর্তব্য রয়েছে যেখানে সুলতানের উলামাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। দিল্লি সালতানাতের ক্ষেত্রে এগুলি নিম্নরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:
“আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মধ্যে: ধর্মীয় বাইয়াত (ইমাম বা ধর্মীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ) এর ধরণ বজায় রাখা হয়েছিল; প্রধান মসজিদের মিম্বর থেকে খুতবা পাঠের মাধ্যমে পরিবর্তিত আদেশের মাধ্যমে রাজার রাজত্ব শুরু হতো এবং মুদ্রায় একটি উপযুক্ত বাণী খোদাই করা হতো। সুলতান সাধারণত একজন মাশাফ-বরদার (কুরআন বহনকারী) নিযুক্ত করতেন যিনি পবিত্র গ্রন্থকে মর্যাদার সাথে বহন ও পাঠ করতেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে দান করা হতো এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[23] বাংলার সুলতানরাও এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে তারা ইয়ামিন-উল-খিলাফাত, নাসির আমিরুল-মুমিনিন ইত্যাদি উপাধি খোদাই করে খলিফার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পরে কয়েকজন সুলতান নিজেদের জন্য ‘খলিফা’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু এটি একটি আইনি বিষয় ছিল, তাই সুলতান অবশ্যই উলামা বা ধর্মতাত্ত্বিকদের অনুমোদন নিয়ে এই উচ্চ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক খলিফাতুল্লাহ উপাধি গ্রহণের প্রশ্নে ড. গফুর লিখেছেন, “রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুব বেশি দূরে নয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জৌনপুরের শাসক মিশরে আব্বাসীয় খলিফার নাম ব্যবহার করতেন। বাংলার সুলতান এই আইনি কৌশল দ্বারা তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে যান। আইনি ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে, বাংলার সুলতান নিজেকে খলিফা বা আমির-আল-মুমিনিন বলার পরিবর্তে নিজেকে খলিফাতুল্লাহ দাবি করেছিলেন। এই আইনি দক্ষতার জন্য বাংলার উলামাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি সাংবিধানিক সমস্যা ছিল। বাংলার উলামাদের সমর্থন ছাড়া এর সমাধান সম্ভব ছিল না।”[24] বাংলার সুলতানরা মসজিদ ও মাদ্রাসাও নির্মাণ করেছিলেন এবং সুফি-দরবেশদের মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি দান করেছিলেন। এমন রাষ্ট্রীয় উচ্চতর কাজ ও অনুষ্ঠানগুলোতে সুলতানের উলামাদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উলামাদের প্রধান কর্তব্য ছিল সুলতানের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক সমর্থন উৎপাদন করা। দিল্লি সালতানাতে উলামাদের কাজের এই দিকটি সম্পর্কে মন্তব্য করে কে. এম. আশরাফ লিখেছেন: “উলামারা তাদের পক্ষ থেকে সুলতানের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক সমর্থন উৎপাদন ও যোগানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যার ফলে দিল্লির সুলতানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত ‘আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বে আছেন তাদের আনুগত্য করো’- এই আয়াতের ব্যাখ্যাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। দিল্লির শাসক সুলতানদেরকে ‘তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বে আছেন’ (উলুল-আমর-ই-মিনকুম) বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নবীজির হাদীসগুলিকেও একইভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল যে, একজন ইমামের (এই ক্ষেত্রে সুলতানের) আদেশের প্রতি আনুগত্য রাসুলের আদেশ বা আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্যের অনুরূপ… উলামারা এই মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন যে, সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিটি প্রতিরোধই সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি অপরাধমূলক কাজ, যদিও সুলতান কাজেকর্মে অত্যাচারী ছিলেন এবং একেবারে স্পষ্টতই ভুল ছিলেন। একইভাবে, আলেমরা রাষ্ট্রকে সামরিক জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে জনগণের কাছ থেকে যে-কোনো সম্পত্তি বা অর্থ বাজেয়াপ্ত করে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে, উলামারা এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন, ‘যে সুলতানের আনুগত্য করে, সে দয়ালু প্রভুর আনুগত্য করে’।”[25] দিল্লির ঐতিহাসিকরা সুলতানের অপকর্মে সমর্থনকারী উলামাদের উলামা-ই-আখিরাত এর বিপরীতে উলামা-ই-দুনিয়া বা উলামা-ই-সু বলে অভিহিত করেন।[26] উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায়ও উলামা-ই-আখিরাত এর পর্যায়ভুক্ত আলেমরা বিশেষ করে পীর-মাশায়েখরা উলামা-ই-দুনিয়া-ভুক্ত আলেমদের পছন্দ করতেন না। বাংলার সুলতানদের মুদ্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উলামারা মুদ্রায় সুলতানদের মহিমান্বিত করার মতো অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি খোদাই করতে পেরেছিলেন। ধারণা করা হয়, বাংলার উলামাদের একটি অংশও সুলতানি শাসনের সমর্থন হিসেবে কাজ করেছিল। মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লিতে মুদ্রা জারি করেছিলেন, যার উপর খোদাই করা ছিল ‘যে সুলতানের আনুগত্য করে সে খোদার আনুগত্য করে’; একই বাক্য বাংলার সুলতানদের মুদ্রাতেও পাওয়া যায়।[27] বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় খোদাই করা উপাধিগুলি উল্লেখযোগ্য; তন্মধ্যে কয়েকটি হল, ‘তাঁর সাম্রাজ্য এবং রাজ্য চিরকাল স্থায়ী হোক’, ‘সেই সুলতান যিনি নির্বাচিতদের আলোয় আলোকিত ঐশ্বরিক যিনি জাগরণ ও ধ্যানে নিবেদিতপ্রাণদের সুলতান উপাধি পেয়েছেন’; ‘খোদার পথে যোদ্ধা’; ‘দয়ালুর (খোদার) সাহায্যে শক্তিশালী’; ‘দয়ালুর (খোদার) সাহায্যে আত্মবিশ্বাসী’ ইত্যাদি। আমাদের কাছে এমন কিছু নথিও রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই যে, একজন আলেম ও শেখ বাংলার সুলতানকে প্রশাসনিক নীতিমালার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। এই নথিগুলি হল বিহারের শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরীর শিষ্য মাওলানা মুজাফফর শামস বলখীর কিছু চিঠি যা বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে লেখা হয়েছিল।
চিঠিগুলো মূলত সুলতানকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল যাতে মাওলানা, তার বন্ধুবান্ধব এবং অনুসারীরা মক্কায় হজ করতে যেতে পারেন। চিঠিগুলো থেকে জানা যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মাওলানার কাছে পরামর্শ চেয়ে চিঠি চেয়েছিলেন। সুলতানের কাছে ধর্মীয় বিষয়ের পরামর্শে চিঠিগুলো পরিপূর্ণ। একটি চিঠিতে, মাওলানা অমুসলিম আমলাদের গভর্নর এবং মন্ত্রীর মতো উচ্চপদে নিয়োগের নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “একজন কাফেরকে কিছু কাজের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে ওয়ালি (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা গভর্নর) করা উচিত নয় যাতে সে মুসলমানদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং তাদের উপর তার কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে পারে… পরাজিত কাফেররা মাথা নিচু করে তাদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাদের জমি পরিচালনা করে। কিন্তু তাদেরকে নির্বাহী কর্মকর্তাও নিযুক্ত করা হয়েছে এমন ঘটনা ঘটা উচিত নয়।”[28] শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রাজা এবং শাসক শ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “যদিও সুলতান তাদের অত্যাচারী কর্মকাণ্ড এবং তাদের দ্বারা নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্তপাতের জন্য বিচারের দিনে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু তাদের সৎকর্ম এবং উদারতা তাদের অপকর্মের চেয়েও বেশি হতে পারে। কারণ তারা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তারা বিশ্বের শান্তি বজায় রাখার জন্য সহায়ক এবং তাদের তরবারির ভয়ে অবিশ্বাসী এবং চোররা তাদের লুণ্ঠনের কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে না।” অন্য একটি চিঠিতে মাওলানা বলখী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যার অর্থ ‘এক ঘন্টার ন্যায়বিচার ষাট বছরের প্রার্থনা এবং নিষ্ঠার চেয়ে উত্তম’। অতএব, এটি বলা যেতে পারে যে, উলামা শ্রেণী দিল্লি সালতানাতের মতো বাংলায় মুসলিম সালতানাতকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।
মোল্লা শব্দটির ব্যাপারে আরও স্পষ্ট করে বলা দরকার। মোল্লা শব্দের অর্থ একজন শিক্ষক, একজন ডাক্তার, একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, একজন বিচারক এবং পুরোহিত। আমাদের এখানে মোল্লাদের উলামা বা ধর্মতত্ত্ববিদদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু আজকাল মোল্লা শব্দটি দ্বারা মুসলিমদের একটি অর্ধশিক্ষিত পুরোহিত শ্রেণীকে বোঝানো হয়ে থাকে যারা নিরক্ষর মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাঙালি কবিদের দ্বারা চিত্রিত মোল্লা আধুনিক মোল্লাদের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ভালো নয়। এমনকি নুসরত শাহের একটি শিলালিপিতেও মোল্লাকে সামাজিকভাবে সন্দেহভাজন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে, শিলালিপিতে বলা হয়েছে, “মসজিদটি ওয়াকফের… যেহেতু মোল্লা এবং আরবাব (জমিদার বা কর্মকর্তা?) আওকাফ প্রতারণার ক্ষেত্রে (ওয়াকফ সম্পত্তি) আল্লাহর অভিশাপের আওতায় পড়ে, তাই গভর্নর এবং কাজীদের এই ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধ করা আন্তরিক কর্তব্য, যাতে বিচারের দিন তারা তাদের খারাপ কাজের জন্য ধরা না পড়েন।”[29] শিলালিপির ভাষা মোল্লা এবং জমিদার বা কর্মকর্তাদের (?) প্রতারকদের একটি শ্রেণী হিসেবে সন্দেহ প্রকাশ করে। বিজয় গুপ্ত তাকি নামে এক মোল্লা সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি কিতাব (ধর্মীয় নীতি) সম্পর্কে সুপরিচিত এবং কাজী যখনই কোনও ভোজের আয়োজন করেন তখন তাকে মুরগি জবাই করতে বলা হয়। তিনি কাজীর দৈনন্দিন জীবনেও তার পরামর্শদাতা ছিলেন। যখন কাজীর এলাকা সাপে ভরা ছিল, তখন খাস বা ইখলাস নামে আরেক মোল্লা, যাকে কাজীর শিক্ষকও বলা হয়, তিনি কাজীকে সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ নেয়ার পরামর্শ দেন।[30] ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের কবি মুকুন্দ রাম আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মোল্লাকে নিকা ও বিয়া (বিবাহ) অনুষ্ঠানের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং তিনি চার আনা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। মুরগি ও ছাগল জবাইয়ের জন্যও মোল্লাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। একটি মুরগি জবাইয়ের জন্য দশ গন্ডা কড়ি এবং একটি ছাগল জবাইয়ের জন্য এক টুকরো এবং জবাইকৃত ছাগলের মাথাও দেওয়া হয়েছিল।
এখানে আমরা এমন একজন মোল্লার ধারণা পাই যা সাধারণত বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক সময়ে গ্রামাঞ্চলে যা দেখা যায় তারচেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। ধর্মীয় নীতিমালা, বিশেষ করে ইসলামের দৈনন্দিন রীতিনীতি সম্পর্কে মোটামুটি পারদর্শী মোল্লার সাথে সাধারণত সাধারণ কম শিক্ষিত মুসলমানরা পরামর্শ করতেন। অতএব, গ্রামের মুসলিম সমাজে তার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, কারণ সমস্ত অনুষ্ঠান ধর্মীয় আদেশ, রীতি-নীতি অনুসারে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হতো। এই অনুষ্ঠানগুলোর কিছু বর্ণনা বিজয় গুপ্ত এবং মুকুন্দ রাম করেছেন, কারণ তারা দূর থেকে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। মোল্লারা তাদের শ্রম এবং সময়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ফি নিতেন এবং এক জায়গায় ফি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল বলে মুকুন্দ রাম উল্লেখ করেছেন। সেই সময় স্থানীয় জনগণকে পীর-মাশায়েখ এবং উলামারা ইসলামে ধর্মান্তরিত করছিলেন এবং এই ধর্মান্তরিত জনগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না। সম্ভবত এই কারণেই মোল্লাদের সেবা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। যারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন কিন্তু অন্যান্য উচ্চতর পেশায় নিয়োজিত হতে পারেননি, হয় এই ধরণের সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে অথবা কোনো বিষয়ে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনের অভাবের কারণে, তারা এমন একটি পেশার দিকে ঝুঁকেছিলেন যা কম লাভজনক কিন্তু যাদের সাথে তারা কাজ করতেন তাদের দ্বারা অবশ্যই সম্মানিত ছিলেন। যেহেতু বেশিরভাগ মুসলিম এলাকায় একই ধরণের কাজ সম্পাদন করতে হতো, ফলস্বরূপ মোল্লাদের সংখ্যা এবং সমাজে তাদের আধিপত্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোল্লারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতেন। তারা নিজেরাই একটি শ্রেণী গঠন করেছিলেন কি-না তা বলা খুব কঠিন। অর্থনৈতিকভাবে তারা সচ্ছল ছিলেন না। বিজয় গুপ্তের দেওয়া মোল্লাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তারা ধর্মীয় বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন এবং এমনকি কাজীও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। তারা সমাজের একটি শক্তি ছিল এবং ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হতে সাহায্য করতেন।
‘শেখ’ শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে এর অর্থ মুসলিম আইন ও ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত ব্যক্তি। এই অর্থে তারা আলেম কিন্তু শেখরা হলেন সেইসব আলেম যারা নিজেরা আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করেন এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দেন। শেখ শব্দটি বাংলার প্রায় সকল সুফির নামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ সুফিরা প্রকৃতপক্ষে তাদের রহস্যময় পরিবেশনার পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন। সুফিদেরকে মাখদুমও বলা হয় অর্থাৎ যার সেবা করা হয়। তাই শেখ এবং মাখদুম শব্দ দুটি সেই সুফি-দরবেশদের বোঝায় যারা বাংলার মুসলিম সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও পালন করছেন। শেখরা বিভিন্নভাবে মুসলিম রাজ্য এবং মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিছু সুফি স্বাধীনভাবে অথবা শাসক শ্রেণীর সহযোগিতায় অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছেন বলে জানা যায়। অভিবাসী মুসলিমদের মধ্যে, সে সুফি হোক বা সাধারণ মানুষ, বংশ পরম্পরায় এই দেশে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুসলিম ক্ষমতার বিস্তারে শাসক শ্রেণীর সাথে সুফিদের সহযোগিতাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ তারা মনে করত ইসলামের জন্য লড়াই করা একটি জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধ। মুজাফফর শামস বলখীকে দেখা যায় যে, তিনি কোনো ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। তিনি বলেন, “আমি একজন দরিদ্র মানুষ যার রাজার সেবার জন্য কিছুই নেই, এমনকি দুটি সুসজ্জিত ঘোড়াও নেই যাতে আমি রাজার জন্য যুদ্ধ করতে পারি… আমি জানি যে, খোদার পথই খোদার যোদ্ধাদের পথ।” এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সিলেট বিজয়ে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সাথে শাহ জালালের সহযোগিতা, কামরূপ ও উড়িষ্যা বিজয়ে রুকনুদ্দিন বারবক শাহের সাথে শাহ ইসমাইল গাজীর সহযোগিতা, অথবা চট্টগ্রাম বিজয়ে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের সাথে শাহ বদর ও শাহ কাত্তালের সহযোগিতা বিচার করা উচিত।
এমনও ঐতিহ্য রয়েছে যেখানে দরবেশরা নিজেরাই ইসলামের জন্য যুদ্ধে নেমেছিলেন। অন্যদিকে, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা বিপরীত ধরণের তথ্য সরবরাহ করে, অর্থাৎ প্রকৃত সৈন্য এবং বিজয়ীদের ইন্তেকালের পরে তাদের দরগাহ বা মাজারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বাগেরহাটের খান জাহান এবং ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী হলেন এমনই দুজন সৈনিক যাদেরকে এখন সুফিসাধক হিসেবে গণ্য করা হয়।
শেখরা সুলতানদের এবং দেশের শাসক শ্রেণীকেও প্রভাবিত করেছিলেন। সুলতানরা সাধারণত সুফিদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, সুলতানরা শেখদের সম্মানে তাদের সাহায্য করেছিলেন, তাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন এবং এমনকি শেখদের দরগাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ জমিও দিয়েছিলেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ, এমনকি তার প্রতিপক্ষ ফিরোজ তুঘলকের আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েও অবরুদ্ধ একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে শেখ রাজা বিয়াবানীর জানাজায় যোগ দিয়েছিলেন।[31] উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে অমুসলিমদের নিয়োগের বিষয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে মাওলানা মুজাফফর শামস বলখীর পরামর্শের কথা আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহয়া মানেরিও সুলতান সিকান্দর শাহের সাথে চিঠিপত্রে যুক্ত ছিলেন। সিকান্দর শাহও শেখদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু একই শাসক শেখ আলাওল হককে পান্ডুয়া থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত নির্বাসিত করেছিলেন। কথিত আছে যে, সুলতান শেখের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন কারণ শেখ ভিক্ষুক, দুস্থ এবং মুসাফিরদের খাওয়ানোর জন্য এত টাকা ব্যয় করতেন যে, রাষ্ট্র রাজকোষ এত বিশাল ব্যয় বহন করতে পারত না। এই কারণটি সন্তোষজনক নয় এবং মনে করা হয় যে, রাজধানী পান্ডুয়ার অভিভাবক-দরবেশকে নির্বাসনের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুলতানের অবশ্যই উপযুক্ত কারণ থাকতে হবে। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহকে মাওলানা মুজাফফর শামস বলখীর পরামর্শ এবং বাংলার পরবর্তী ইতিহাস বিবেচনা করে যেখানে একজন অমুসলিম, অর্থাৎ রাজা গণেশ মুসলিম শাসকদেরকে পরাস্থ করেছিলেন সেখানে আমরা মনে করি, শেখ আলাওল হক অবশ্যই রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে বা সুলতানের কিছু রাষ্ট্রীয় নীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যে কারণে সুলতান এই অস্বাভাবিক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে শেখ নূর কুতুব আলমের আগমন, যখন তিনি জৈনপুরের একজন রাজাকে অত্যাচারী রাজা গণেশকে দমন করার জন্য বাংলা আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই ঘটনা এতটাই সুপরিচিত যে এর পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।
শেখদের প্রধান অবদান ছিল তাদের ধর্মপ্রচারমূলক কর্মকাণ্ডে। তারা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শেখের মতো অন্য কেউ, এমনকি উলামা সম্প্রদায়ের কেউই মানুষের এতটা আকর্ষণ করতে পারেননি। মানুষের তাদের প্রতি অটল ভক্তি ছিল এবং বিপদ ও অসুবিধার সময়ে তাদের দোয়া কামনা করত। তারা বিশ্বাস করত যে, শেখরা দরিদ্র, অসুস্থ এবং দুঃস্থদের ত্রাণ দেওয়ার মতো অতিমানবিক মনের অধিকারী ছিলেন। খানকাগুলি সকল দরিদ্র, দুঃস্থ, ভবঘুরে এবং ভ্রমণকারীদের খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঐতিহ্য ছাড়াও, সমসাময়িক বেশ কয়েকটি শিলালিপি এই মতামতকে সমর্থন করে। শেখদের দরগাগুলিকে ‘পৃথিবীতে বিশ্রামদানকারী ভবন’ হিসাবে বিবেচনা করা হত, ‘যেখানে মানুষ তাদের ইচ্ছা পূরণ করে’।[32] শিলালিপিতে কিছু শেখের কথা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা লক্ষণীয়। শায়খ আলাওল হককে `দানশীল ও শ্রদ্ধেয় শায়খ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর দয়ায় যার সৎকর্ম ব্যাপক এবং মহৎ, তার হৃদয় ঐশী আলোয় আলোকিত হতে পারে।[33] শায়খ নূর কুতুব আলমকে বর্ণনা করা হয়েছে (ক) হযরত শায়খুল ইসলাম, উম্মাহর মুকুট, শায়খদের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ, যারা আল্লাহর সাথে একীভূত হয়েছেন, (খ) হযরত, শায়খদের বাদশাহ, কুতুবুল-আকতাব (মেরুদের মেরু), (গ) আমাদের শ্রদ্ধেয় মাখদুম, ইমামদের ইমাম, জমায়েতের জান, ঈমানের উত্তরাধিকার, ইসলাম ও মুসলমানদের সাক্ষ্য, যিনি দরিদ্রদের উপকার করেছেন, সাধুদের এবং যারা পথপ্রদর্শন করতে চান তাদের পথপ্রদর্শক, (ঘ) দ্বীনের সূর্য এবং সত্যের চাঁদ, আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক।[34] আরেকটি শিলালিপি অনুসারে, “জালালুদ্দীন শাহ তাবরিজি আল্লাহর কাছে গৃহীত, ফেরেশতাদের মতো স্বভাব এবং দুনিয়ায় ধর্মের সুলতান।”
মানুষ সত্যিই বিশ্বাস করত যে, শায়খদের এই ধরণের যোগ্যতা ছিল, তারা আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তাদের হৃদয় আলোকিত হয়েছিল, ঐশ্বরিক উপলব্ধি অনুসারে তারা ছিলেন সত্যের পথিক। এই সমস্ত কিছুই ছিল এই সত্যের কারণে যে, শেখরা সরলতা এবং কঠোরতার জীবনযাপন করতেন। তারা তাদের শিক্ষকদের নির্দেশে নীচু কাজ করতে দ্বিধা করতেন না, এমনকি ঝাড়ুদার হিসেবেও কাজ করতেন। তাদের চরিত্র, সরলতা এবং কঠোরতা, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে উচুঁ-নীচু, দরিদ্র ও নিঃস্ব সকলের প্রতি তাদের ভালোবাসাই স্থানীয় জনগণকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং তারা বাঙালি জনগণের মন জয় করেছিল। শেখ এবং তাদের দরগাহগুলি বাংলায় মুসলিম সমাজের বিকাশে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য। উত্তর ভারতে, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অধীনে ছিল সেখানে ইসলাম কেবল নগর কেন্দ্রগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ব-দ্বীপীয় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ সমাজে ইসলামের জয়জয়কার। এই অবস্থানের একটি কারণ পীর-মাশায়েখদের ধর্মপ্রচারমূলক কার্যকলাপ এবং সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মাজার, দরগাহের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।
মুসলিম এলাকার বর্ণনায় মুকুন্দ রাম পীরকে শিরনি প্রদানের কথাও উল্লেখ করেছেন। ব্যুৎপত্তিগতভাবে পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, তবে এটি সাধারণত সেই শিক্ষকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যাদের কাছ থেকে মানুষ আধ্যাত্মিক নির্দেশনা গ্রহণ করে। “পীর হল সুফি বা ইসলামের মধ্যে একজন আধ্যাত্মিক ডাক্তার বা পথপ্রদর্শককে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ। তারা শেখ, মুর্শিদ, উস্তাদ নামেও পরিচিত। পীর একটি ফারসি শব্দ, তবে এটি ভারত এবং তুরস্কে সাধারণভাবে একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের জন্য ব্যবহৃত হয়; আমাদের বিশেষ অর্থে শেখ সমগ্র ইসলামে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, মুর্শিদও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে ভারতের চেয়ে তুর্কি বা আরবি ভাষাভাষী দেশগুলিতে বেশি ব্যবহৃত হয় আর উস্তাদ ব্যবহৃত হয় পারস্যে।”[35] তৎকালীন শিলালিপিতে শেখ এবং মাখদুম শব্দটি ব্যবহার করা হয়, পীর শব্দের উল্লেখ নেই। কিন্তু মুকুন্দ রাম’র উল্লেখ সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে, সেই সময়েও তারা পীর নামে জনপ্রিয় ছিলেন। মুকুন্দ রামের উল্লেখ অনুসারে শেখ বা পীরের উদ্দেশ্যে নেওয়াজ বা হাদিয়া প্রদান বাংলা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বা বর্তমানেও প্রচলিত। ইবনে বতুতা বলেছেন যে, তিনি সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষদের শাহ জালাল এবং খানকাহে তাঁর অনুসারীদের জন্য উপহার দিতে দেখেছেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ শেখ নূর কুতুব আলমের কাছে সুস্বাদু খাবার ভর্তি ট্রে পাঠাতেন। কিন্তু মুকুন্দ রামের শিরনির উল্লেখ সম্ভবত জীবিত পীরের কাছে নয় বরং দরগায় নজর, নেওয়াজ প্রদানের ইঙ্গিত বহন করে। তাই দরগায় শিরনি প্রদান বা ওরস অনুষ্ঠান, যা আজও খুবই জনপ্রিয়, সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। শেখ, মখদুম বা পীর, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সুফিরা ছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত মানুষ এবং ইসলামের মূল আদর্শের প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি আনুগত্য পোষণ করতেন। তারা তাদের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনে অটল থাকতেন এবং পার্থিব লাভের জন্য শাসক শ্রেণীর সাথে যোগাযোগ রাখা হতে বিরত থাকতেন। মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী নিজের সম্পর্কে বলেন, তিনি “পুত্র, পরিবার, কেউই পার্থিব কোনো জিনিসের খোঁজ করতেন না এবং পদ ও সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না।” শেখ নূর কুতুবুল আলম তার ভাই, উজিরে আজম খানের রাষ্ট্রীয় চাকরি গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[36]
শেখরা পার্থিব উলামাদের পছন্দ করতেন না, বিশেষ করে যারা `ইচ্ছাকৃতভাবে সুলতানের ইচ্ছা পূরণের জন্য কুরআনের অর্থ প্রসারিত করে’ ইসলামের ধর্মীয় আদেশ লঙ্ঘনে সুলতানদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। মাওলানা শেখ মুজাফফর শামস বলখী, যিনি নিজে একজন মহান আলেম, যিনি একসময় দিল্লিতে ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক নির্মিত কুশক-ই-লাল নামক আরবি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ‘সেই পার্থিব উলামাদের নিন্দা করেছিলেন যারা সুলতানের দরবারে গিয়ে তাদের জ্ঞানকে অপমানিত করেছিলেন এবং যাদের জ্ঞান তাদের কর্ম ও লেনদেনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না’। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, সুফিধারার এই বিশুদ্ধ ধারণাটি পরিবর্তিত হয় এবং পীরবাদ একটি বংশগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পীরের পুত্র অগত্যা পীর হয় না; একজন শেখের বংশধর বাস্তবে আধ্যাত্মিক বিকাশ অর্জন করতে পারে না। বাংলায় শেখ আলাওল হকের পরিবার কয়েকজন আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত সুফি তৈরি করেছিল, তবে এই উদাহরণ বিরল। সুতরাং পীরবাদের বংশগত প্রকৃতি সুফিবাদের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একজন পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, “যদি একজন সুফিসাধক তার জীবদ্দশায় দুনিয়াকে অবজ্ঞা করতে সক্ষম হন, তবে তার ইন্তেকালের পর তার পুত্র এবং উত্তরসূরীরা পার্থিব লাভ উপভোগ করতেন। পীরজাদা এবং মখদুমজাদারা অথবা পীর ও শেখদের বংশধররা, বিশেষ করে উলামাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে, আধ্যাত্মিক গুরুদের পদ দখল করতে শুরু করেছিলেন।”[37] মুকুন্দ রামের বর্ণনা অনুসারে, তিনি যে এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর পীরকে শিরনী প্রদান করেছিলেন, সম্ভবত এটিই ইঙ্গিত দেয় যে, মুঘল-পূর্ব যুগেই পীরবাদের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল।
ফিরোজ শাহ তুঘলকের ঘোষণাপত্রে মুসলিমদের সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখ বা আহলি-কালম গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন, “বর্ণবাদ কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে মুসলমানদের উপর সম্পূর্ণ ব্যবহারিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং উপ-বিভাগ তৈরি করে। আন্তঃবিবাহ এবং আন্তঃভোজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সহ সৈয়দ, শেখ, মুঘল এবং পাঠানরা আশরাফ (অভিজাত) শ্রেণী গঠন করেছিল কিন্তু আন্তঃবিবাহ কেবল তাদের মধ্যেই নয়, একই ক্রম অনুসারেও ছিল।”[38] এতে কোন সন্দেহ নেই যে সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখরা সমাজের উচ্চ এবং সর্বাধিক সম্মানিত শ্রেণী গঠন করেছিলেন। তাদের মধ্যে জন্মগত কারণে সৈয়দদের প্রাধান্য ছিল এবং এই অর্থে তারা ব্রাহ্মণদের সমান যারা তাদের জন্মের কারণে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণের তালিকার শীর্ষে। তবে সৈয়দ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্য কোনও মিল নেই। সৈয়দরা নবীর বংশধর এবং উলামা ও মাশায়েখরা তাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক অর্জনের জন্য, উচ্চ ও নিম্ন মুসলমানদের দ্বারা সর্বদা সম্মানিত ছিল এবং সর্বদা সম্মানিত হয়। নবীর প্রতি সালাত ও সালাম (যাকে দরুদ বলা হয়) প্রদানের জন্য কুরআনে একটি নির্দেশ রয়েছে এবং নবীর কিছু হাদীস রয়েছে যেখানে মুসলমানদের কেবল নবীর প্রতিই নয় বরং তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং সাহাবীদের প্রতিও শুকরিয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী মুসলমানরা দরুদ পাঠ করে এবং এটি সম্মান প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায়। শাসকদের কাছে সৈয়দদের এতটাই সম্মান ছিল যে, যখন আমির তৈমুর দিল্লির জনগণকে হত্যা করেছিলেন, তখন তিনি সৈয়দ এবং অন্যান্য ধর্মীয় মুসলিম গোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, এই লোকেরা কি এক ধরণের উচ্চতর জাতি গঠন করেছিলেন? আন্তঃবিবাহ এবং আন্তঃভোজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা- বর্ণ-প্রথার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, প্রাক-মুঘল মুসলিম সমাজে সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। শেখরা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ সৈয়দ এবং আলেমও ছিলেন, তারা খুব সরল জীবনযাপন করতেন: তাদের ধর্মপ্রচারমূলক কার্যকলাপে, তাদের খানকা উচুঁ-নীচ, দরিদ্র এবং নিঃস্ব সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তারা তাদের খানকাহে উপস্থিত লোকদের খাবার পরিবেশন করতেন। এই পরিস্থিতিতে আন্তঃভোজের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্ভব ছিল না। বিবাহের ক্ষেত্রে, কুফু বিবাহের বিধান রয়েছে অর্থাৎ একই বা সমান মর্যাদার পরিবারের মধ্যে বিবাহ। চুক্তিবদ্ধ পক্ষ বা পরিবারের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য কুফুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই বর্ণ ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায় না। উলামা এবং শেখরা তাদের মেয়েদের তাদের পদমর্যাদার বাইরের লোকদের সাথে বিবাহ করেছিলেন বা দিয়েছিলেন কি-না তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে কোনও তথ্যে উৎস নেই। তবে আমাদের কাছে সৈয়দ ও অ- সৈয়দের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সৈয়দ নুসরত শাহ’র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন সিকান্দার লোদি নামে একজন আফগান বংশধর; বাংলায় শেরশাহের গভর্নর খিজির খান, সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ রাঢ়ের কাজীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায় (কাজী একজন সৈয়দ ছিলেন কি-না তা অবশ্য জানা যায় না)। একই রাজা একজন পারস্য মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায় যার সন্তান রওশন আখতার বেগম কুতুবুল আশাগিনের সাথে বিবাহিত ছিলেন। ঈসা খানের পিতা কালিদাস গজদানী, যিনি সুলাইমান নামে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। সুলতানি যুগ বাংলায় মুসলিম সমাজের স্বর্ণযুগ। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসারের সাথে সাথে ইসলাম প্রচারিত হচ্ছিল। এ-সময়ে সৈয়দ, উলামা এবং মাশায়েখরাই সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, তারাই উচ্চশ্রেণী গঠন করেছিলেন। তাদের শ্রেণীকে অপশক্তি ও দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাদের কোনও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতএব বলা যায় যে, মুসলিম সমাজে সামাজিক বিধিনিষেধ, যেমনটি উনিশ শতকের আশরাফ এবং আজলাফ নামক শ্রেণী-পার্থক্যে দেখা যায়, বাংলার প্রাক-মুঘল মুসলিম সমাজে সেভাবে বিকশিত হয়নি।