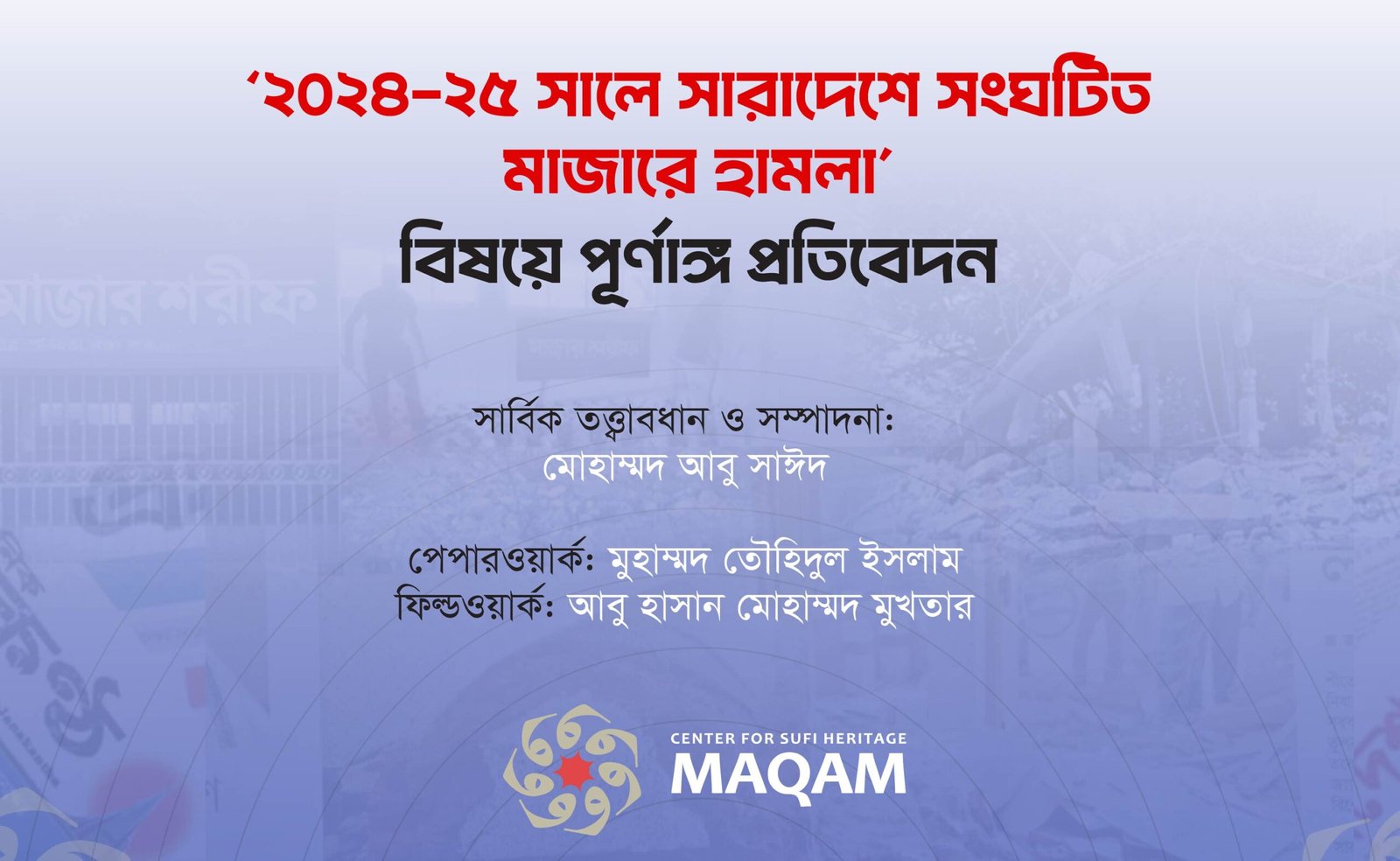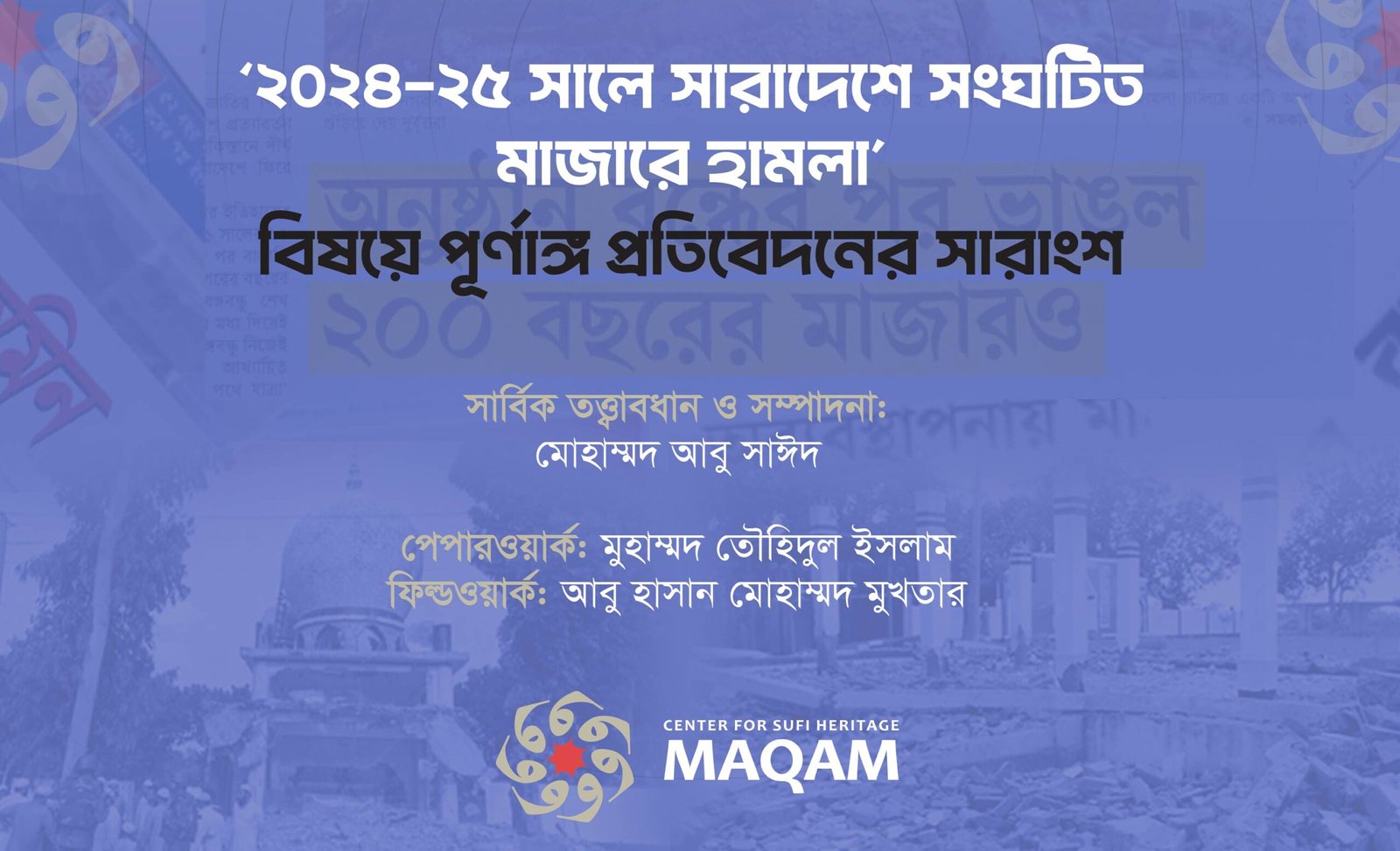ভূমিকা
বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা এমন এক ব্যক্তিত্ব যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার সন্তান হিসেবে চট্টগ্রামের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাইজভাণ্ডারের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার পাশাপাশি দরবারের ইতিহাস ও সাধকদের বিষয়ে বেশ ভালো জানাশোনাও তাঁর ছিল। যার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় উক্ত প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শাহিদা খাতুন সম্পাদিত ‘লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা’ নামক সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশে প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল: ‘মাইজভাণ্ডার: একটি অক্ষম পর্যালোচনা’ ; পরবর্তীতে তিনি নিজেই নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন: ‘অমৃতভাণ্ড মাইজভাণ্ডার’। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের বিষয়ে বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক লিখেছেন। কিন্তু তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে যে গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্য কারো লেখায় বা রচনায় পাওয়া যায় না। ফলত, জাতীয় পর্যায়ে বা আদর্শগত দিক থেকে সেক্যুলার মহলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ নিয়ে যে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা রয়েছে তাতে এই প্রবন্ধ নিশ্চিতভাবেই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।
***
মাইজভাণ্ডারের মহাপুরুষদের সাধনার প্রকৃতি এবং ধারাক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই। সুতরাং এই রচনায় আমি যা বলবো, সবগুলো বাইরের কথা। অধ্যাত্ম সাধনার এই বিশেষ তরিকাটি বিকশিত হয়ে উঠার ফলে ইসলাম ধর্মের নূতন একটি ব্যাখ্যা এই অঞ্চলে মূর্তিমানরূপ ধারণ করেছে। মাইজভাণ্ডার ছাড়াও আরো অনেক অনেক সাধু-পুরুষ ইসলামের সেবায় তাদের মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এই বাংলা মুলুকে ইসলামের প্রচার প্রসারে রাজানুগ্রহের চাইতে আউলিয়া দরবেশদের প্রচারের ভূমিকা যে অনেক বেশি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অঞ্চলে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে যে সকল প্রচারক ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের সকলের কর্মপদ্ধতি এবং সাধনার ধারা একরকম নয়। কেউ কেউ জেহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন। কেউ মানবিক সাম্যের ধ্বজা উর্ধ্বে তুলে ধরে বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের নিষ্পেষিত অংশের মধ্যে মানবিক মযার্দাবোধ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোনো কোনো সাধক জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মানবপ্রেম বিতরণ করার মধ্য দিয়ে ইসলামের সেবা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অলৌকিক কাণ্ড, কেরামতি এগুলোর কথা না হয় নাইবা বললাম।
মাইজভাণ্ডার তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা শাহ সুফী আহমদ উল্লাহর জন্ম ১৮২৬ সালে এবং তিনি ১৯০৬ সালে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর পড়াশোনা হয়েছিলো ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যশোহরে কাজির চাকুরি করেছেন। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তীকালীন সময়টির কথা বিবেচনায় আনলে একথা মেনে নিতে হবে তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মানুষ। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিনি সুফীপন্থী সাধক ছিলেন। বাংলাদেশে যখন থেকে সুফীদের আগমন ঘটতে থাকে তাঁদের বিশ্বাস এবং আকিদার মর্মবস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও একেক ঘরানা এবং একেক যুগের সাধকদের সাধনার ধারা, রস এবং রঙ একরকম নয়।
হজরত মাওলানা শাহ সুফী আহমদ উল্লাহ সাধনার যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার কতিপয় প্রনিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। মাওলানা সাহেব ইসলামের হুকুম আহকাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও মানব মুক্তির এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করেছেন, যেখানে ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ এবং সংঘাতের বদলে অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রশ্নটি অগ্রাধিকার লাভ করেছে। মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ সাহেবের ধর্ম সাধনার প্রকৃতিটি কী রকম ছিলো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে সে বিষয় একটা ধারণা গঠন করা সহজ হবে। একবার ধনঞ্জয় বড়ুয়া নামধেয় একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মাওলানা সাহেবের কাছে এসে আবেদন জানালেন, তিনি যেনো তাকে জাহেরি এবং বাতেনিতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মাওলানা সাহেব জবাবে বললেন, তুমি তোমার ধর্মে থেকে যাও, আমি তোমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলাম। ইসলামের যে, মর্মশাঁষ তার বিস্তার সাধন আর আক্ষরিক অর্থে টুপিধারি মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এক জিনিস নয়, এটাই হজরত মাওলানা আহমদ উল্লাহর ধর্ম সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি।
‘লাকুম দীনুকুম ওলয়াদিন’ অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম জোর-জবরদস্তি নেই। সুফী সাধকেরা কোরানের এই শিক্ষাটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁদের প্রায় সকলেই অহিংস পদ্ধতিতে প্রচার কাজ চালিয়ে গেছেন। আজমীরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহ্ আলাইকে বলা হয়ে থাকে হিন্দুস্থানের পয়গম্বর। কারণ তাঁর কাছ থেকেই প্রথম হিন্দুস্থানের মানুষ ইসলামের পাঠ গ্রহণ করেছে। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন- তোমরা গাছের মতো ছায়া দেবে, বহতা নদীর মতো করুণা বিলিয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত তাঁর তিরোধান দিবসে যে ওরস হয়, তাতে আমিষ জাতীয় কোনো খাদ্যদ্রব্য রান্না করা হয় না। নিশ্চয়ই খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে লক্ষ্য করেছিলেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে আমিষ বর্জন করে এই বিরোধের একটা আপাত সামাধান তিনি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন খাদ্যাভ্যাস এবং ধর্ম এক বস্তু নয়। মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে এই বিষয়টি যেনো প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়, সেই কারণে তাঁর স্মরনোৎসবে সব ধরনের আমিষ বর্জন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে, তথাপি একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। এই পর্যন্ত এই উপমহাদেশে যতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার শতকরা আশিভাগ দুটি মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘটেছে। একটি হলো গরু জবাই এবং অন্যটি মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো। এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে অবশ্যই ধরা পড়ার কথা হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক সময়ে হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম এবং খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ভেদ রেখাটি কি রকম স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কথা, কথা টেনে আনে। এইখানে আমার একটি উপলব্ধির কথা সসঙ্কোচে প্রকাশ করতে চাই। সসঙ্কোচে বললাম তার একটি কারণ আছে। আমার ধারণাটির সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থে আমি পাইনি। শুধু মরহুম হুমায়ুন কবীর একবার নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধসমূহের ভূমিকা লিখতে যেয়ে ভারতীয় উদারনৈতিক ধর্ম সাধনার ইতিহাসে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির যে একটি অনন্য ভূমিকা আছে সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। আমার বিচারে ভগবান বুদ্ধের পরে খাজা মঈনুদ্দীন হলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানববাদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা এবং কর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভারতীয় ধর্মসমূহের উপর এতোদূর ক্রিয়াশীল হয়েছে যে-কবীর, নানক, দাদু, তুকারাম, সাইদাস, রামদাস থেকে শুরু করে শ্রী চৈতন্য পর্যন্ত তাবত সাধকদের মধ্যে খাজা মঈনুদ্দীনের সাধনার সম্প্রসারিত রূপ অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা যায়।
মাইজভাণ্ডারের মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ যে সাধন পদ্ধতিটি প্রবর্তন করেছিলেন, মর্মবস্তুর দিক দিয়ে সেটা হজরত মঈনুদ্দীন চিশতির আরদ্ধ পন্থাটির চাইতে ভিন্ন নয়। তথাপি সময় এবং পরিস্থিতির বিচারে মাইজভাণ্ডারি তরিকার স্বাদ, রঙ এবং রস একটু আলাদা একথা বলা বোধ করি অন্যায় হবে না। সুফী সাধকদের সাধনার প্রকাশরূপের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ বর্তমান সেকথাও বলার অপেক্ষা রাখে না। বাইরের দিক দিয়ে দেখলে মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী থেকে শুরু করে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি এবং মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহর সাধন পদ্ধতির আঙ্গিকের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। তথাপি দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সুফী সাধকদের সাধনার রঙ এবং দাহিকাশক্তি একরকম নয়। মাওলানা হজরত আহমদ উল্লাহ, হজরত মঈনুদ্দীন চিশতির সাধনপন্থার সঙ্গে হজরত আবদুল কাদের জিলানির সাধনপন্থার একটি সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। এই দুই তরিকার সম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছে মাইজভাণ্ডারি তরিকা। কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশা বন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এই চারটি প্রধান তরিকার কথা প্রায়শ বলা হয়ে থাকলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তরিকার সংখ্যা অসংখ্য। তরিকা শাস্ত্রের সহজ অর্থ হলো পথ। প্রতিজন সাধকের আলাদা একটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রকাশের আলাদা একেকটি পন্থাও রয়েছে।
মাইজভাণ্ডারের সাধন পদ্ধতির গভীরতা এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কোনো গাঢ় অনুভবের কথা উচ্চারণ করার ক্ষমতা এবং অধিকার এই নিবন্ধ লেখকের থাকার কথা নয়। মধুর স্বাদ মিষ্টি এই ধারণা যেমন মধু খেয়ে দেখে অর্জন করতে হয়, তেমনি অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে ডুবে গিয়েই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। সাধনার নিরঞ্জন-স্বরূপ সম্বন্ধে বাইরের মানুষের কথা বলা অসম্ভব। মাইজভাণ্ডারের অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ ধারাটি সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে কী বিশেষ অবদান রেখেছে বড়োজোর, সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলা হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে।
হজরত মাওলানা আহমদ উল্লাহর সাধনার ধারা তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী কয়েক পুরুষ পরম্পরা অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল একদল সাধক পুরুষের জন্য সম্ভব করে তুলেছে মাইজভাণ্ডার। নিজ নিজ সাধনক্ষেত্রে সকলেই অনন্য এবং অধ্যাত্ম জগতে এক একটি মর্যাদার আসন অধিকার করে আছেন। হজরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারের উচ্চতম মহিমাশিখর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত মাওলানা গোলাম রহমানের স্থানও সাধক হিসেবে অনেক উঁচুতে। হজরত দেলোয়ার হোসেন এবং জিয়াউল হোসেন এই সকল ব্যক্তিত্ব মাইজভাণ্ডারি সিলসিলার পূর্বপুরুষের পবিত্রতার নিস্ক্রিয় অনুগ্রহভোগী ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না। সাধন মার্গের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে নিজ নিজ আলোক বিচ্ছুরিত করে গেছেন তাঁরা সকলে। ব্যক্তিগত পবিত্রতার ক্ষেত্রেও তাঁরা সকলেই একেকটি গৌরবময় আসনের দাবীদার।
কয়েক পুরুষ ধরে মাইজভাণ্ডারের সাধকেরা সারা দেশে ছড়ানো তাঁদের খলিফাবৃন্দ এবং অখ- অনুরাগে এমন একটি সাধনপস্থার মাধ্যমে জগত জীবনের-অর্থ সন্ধান করেছেন, তার মর্মভেদ, তার চিত্তদোলা আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে এক অচিন্তিতপূর্ব অধ্যাত্ম জাগরণের সূচনা করেছে। সাধনার এই ধারাটি অদ্যাবধি সজিব এবং সক্রিয়। যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার গতিবেগ তীব্রতা হারিয়ে বসেনি। অন্তত কোটিখানেক মানুষের অন্তরে মাইজভাণ্ডার ভক্তি সাধনার আহিতাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পুরুষানুক্রমিক অধ্যাত্ম সাধনার একটি নঞর্থক দিকের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। পীর নামধারী ব্যক্তিরা সকলেই সমান পবিত্র অগ্নির ধারক হতে পারেন না। অনেক সময়েই দেখা যায় একেকজন আলোকসামান্য সাধকের সাধনাকে মূলধন করে তার অপোগন্ড অলস উত্তরাধিকারির দল পুরুষানুক্রমিকভাবে বিনা মূলধনের ব্যবসাদারি পেতে বসে আছেন। মাইজভাণ্ডার তরিকার অনুসারীদের মধ্যে যান্ত্রিক ভক্তিবাদ এবং ভক্তি সর্বস্বতা আশ্রয় করেনি, এ কথা বললে ঠিক হবে না। পীর-মুরিদী সম্পর্কের তেজারতির প্রতিযোগিতায় মাইজভাণ্ডার তরিকার উত্তরাধিকারিদের অনেকেই আসল সাধনপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি অভ্যস্থ অভ্যাসে লোক ঠকানোর চমৎকার ক্রীড়ায় মেতে উঠেননি, তাও সব সময়ে সত্য নয়। বস্তুত বর্তমানে মাইজভাণ্ডারি তরিকার অনুসারীর দাবীদার উত্তরাধিকারিদের নানা শরিকের মধ্যে কে সঠিক পথে রয়েছেন, কে বিচ্যুত হয়ে জাগতিকতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন, পরখ করার উপায় কি? তবে একটি বিশেষ ব্যাপার আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই- মাইজভাণ্ডারের পীর বংশের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একেকজন ক্ষ্যাপা পুরুষের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে, যাদের মধ্য দিয়ে মাইজভাণ্ডারি তরিকার ভক্তি-সাধনা নূতন বেগ এবং আবেগ অর্জন করেছে।
মাইজভাণ্ডারি তরিকার ভক্তি-সাধনা এই অঞ্চলের সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে কিছু না বললে অন্যায় করা হবে। মাইজভাণ্ডারের পীরেরা এই অঞ্চলে ইসলামের একটি অভিনব ব্যঞ্জনা মূর্তিমান করে তুলেছেন। কোরান, হাদিসের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী সাধক পুরুষদের যে সাধনা, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে মাইজভাণ্ডারি তরিকা তার একটি অগ্রবর্তী সম্প্রসারণ মাত্র। একথা বললে অন্যায় করা হবে না। তথাপি ধর্মীয়বদ্ধ মত এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর পথ মাইজভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছে। ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবজনিত কারণে কিনা আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, ধর্মীয় আচারের কঠোরতা এই অঞ্চলের ইসলামকে অনেকদিন পর্যন্ত একটি জন-অচল কুঠুরিতে পরিণত করে ফেলেছিলো। তার প্রভাব মুসলিম সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, অদ্যাবধি তার জের সমাজে ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রাণহীন আচারসর্বস্বতা এবং নীরেট যান্ত্রিকতার মধ্য থেকে ইসলামের প্রেম-ধর্মের মর্মবাণী সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করাই হলো মাইজভাণ্ডারি তরিকার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের যখন বিচ্ছেদ ঘটে ধর্ম তখন প্রাণহীন আচারসর্বস্বতা এবং নিছক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। তখন সমাজে ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়। স্বতঃস্ফূর্ততার দ্যোতনা তখন ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না। মাইজভাণ্ডারি তরিকা এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে নতুনতরো একটি স্বতঃস্ফূর্ততার দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পেরেছে। ধর্মের সঙ্গে যদি আনন্দ সাধনার সংযোগ না ঘটে, ধর্ম বিধি-নিষেধের ছককাটা মৌমাছিতন্ত্রের রূপ নেয়। মাইজভাণ্ডার ধর্মের সঙ্গে আনন্দ ও রস-তৃষার সংযোগ ঘটিয়ে ধর্মের একটি ইতিবাচক অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছে। সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিলো বলেই ইসলাম একটি নতুন জীবনাবেগ নিয়ে জীবনের নতুন মহিমা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু সম্প্রদায়কে কখনো প্রধান করে তোলে না। রামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন ‘যত মত তত পথ’। ধর্মগুলোর অন্তর্নিহিত যে প্রেরণা তার মধ্যে একটা মর্মগত ঐক্য বিদ্যমান। এটা মুখে বলা সহজ বটে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে এই সত্য আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের মতোই দুরূহ এবং কঠিন। মাইজভাণ্ডারের সাধকেরা এই কঠিনের সাধনা করেছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিও লাভ করেছিলেন। কে কিভাবে নেবেন জানিনে, আমি মাইজভাণ্ডারকে নবদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করতে চাই। নবদ্বীপ, বৈষ্ণবদের ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজে যে একটি নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলো, বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশে তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। বৈষ্ণব সাধকদের লিখিত গীতি কবিতাগুলো বাংলার কাব্যলোকের এমন এক অক্ষয় সম্পদ, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার তুলনা মেলা ভার হবে। এই গীতি কবিতাগুলো কালের কণ্ঠে ইন্দ্রমনির হারের মতো দুলছে। বলা হয়ে থাকে প্রেমাবতার শ্রী চৈতন্যদেব স্বয়ং একটি বাক্যও না লিখে একটি বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তুলনা জিনিসটি ভালো নয়। তুলনার মাধ্যমে একটা সাদৃশ্যবোধ জন্মানো সম্ভব হলেও তাতে আসল সত্য পরিস্ফুট করা সম্ভব হয় না। প্রতিটি প্রজন্মের বংশধরের যেমন একটি নিজস্ব জীবন রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অন্দোলন এবং জাগরণের একটি নিজস্ব প্রাণপ্রবাহ এবং প্রেক্ষিত রয়েছে। তথাপি আমি মাইজভাণ্ডারের সঙ্গে নবদ্বীপের তুলনা করেছি যাতে চট করে একটা ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়।
মাইজভাণ্ডারের পীরেরা কেউ সরাসরি সাহিত্যচর্চা বা সঙ্গীতসাধনা করেননি। কিন্তু তাঁদের সাধনাকে উপলক্ষ করে সঙ্গীতের এমন এক বিপুল সঙ্গীতভাণ্ডার রচিত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা কতো হবে অদ্যাবধি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। মাইজভাণ্ডারকে উপলক্ষ করে উর্দু ফার্সি ভাষায় গজল, কাওয়ালি গান যেমন অজগ্র লেখা হয়েছে, তেমনি সরল গ্রাম্য মানুষের বোধ এবং অনুভবগম্য বাংলা ভাষায়, এমনকি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাতেও হাজার হাজার গান লেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়ানো ছিটানো সুফী সাধকদের খানকাহ এবং মাজারে যে গজল, যে কাওয়ালি গান সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই প্রাথমিক দিকে মাইজভাণ্ডারেও উর্দু ফার্সি ভাষায় গজল, কাওয়ালি লিখিত হয়েছে এবং গীত হয়েছে। এ কথাতো নতুন নয় মুসলিম সুফী সাধকদের সাধনার সঙ্গে কাওয়ালি গানের একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। কাওয়ালি প্রথম চালু করেছিলেন হজরত আমির খসরু, ফার্সি ভাষায়। পরে উর্দু ভাষায় কাওয়ালি লিখিত এবং গীত হতে থাকে। সুফী-সাধনা পদ্ধতির এই আদিরূপটি মাইজভাণ্ডারেও অনুসৃত হয়েছে, তাতে অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, চট্টগ্রামে কালু, পেয়ারু এবং আবু কাওয়াল এই সকল জনপ্রিয় কাওয়ালি গায়কের যে আবির্ভাব ঘটেছিলো তার সঙ্গে মাইজভাণ্ডারের একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে-আজকের দিনে ধর্ম জিজ্ঞাসু জনগোষ্ঠীর বাইরে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মাইজভাণ্ডারের যে প্রসার এবং পরিচিতি, মাইজভাণ্ডারের সাধনরীতিকে উপলক্ষ করে লেখা হাজার হাজার বাংলা গানই তার মুখ্য কারণ। এই গানগুলিতে মাইজভাণ্ডারের একটি নতুন ভাবমূর্তি সকলের সামনে উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছে। গান দিয়ে মাইজভাণ্ডারের সাধনা এবং গানেই মাইজভাণ্ডারের পরিচয়। মাইজভাণ্ডারি গানের একটি বিশেষ গায়িকা শক্তি, একটি অন্তরাবেগ, একটি বিশেষ সুর, এবং বিশেষ ধরনের তাল-লয় রয়েছে। যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেনো মাইজভাণ্ডারি গানে বাঙ্গালি সঙ্গীত চিন্তার একটি বিশেষ রসময়ধারা বাণীমূর্তি লাভ করেছে। মাইজভাণ্ডারি গানের কথা বাদ দিলে বাঙ্গালির সঙ্গীত সাধনার প্রতি সুবিচার করা কখনো সম্ভব হবে না। এটা তর্কাতীত সত্য যে, মাইজভাণ্ডারি গান বাংলার সঙ্গীতকে আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মাইজভাণ্ডারি গানের ভাব, ভাষা, বাণী, সুর এবং তাল সবদিক দিয়ে অভিনব ও একক পরিচয়ে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।
নন্দনতাত্ত্বিক মানদণ্ডে মাইজভাণ্ডারি গানের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি এখনো শুরুই হয়নি। মাইজভাণ্ডারি গানের উপযোগবাদিতার দিকটিই সকলের সামনে আসতে পেরেছে। যেহেতু অধিকাংশ গান লিখেছেন মাইজভাণ্ডারের ভক্তবৃন্দ, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকারের বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। কাদের উদ্দেশে এই গানগুলো লিখিত হয়েছে সেকথাও স্মরণে রাখতে হবে। অতি সাধারণ গ্রাম্য সরল মানুষের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ মাইজভাণ্ডারি গান লিখিত হয়েছে। এই গানে ভাবটাই প্রধান। ভাষাগত উৎকর্ষ বা প্রকাশভঙ্গী মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তারপরেও একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই সরল স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের ভক্তির উত্তাপের আতিশয্য- কোনো কোনো গানে এমন দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠেছে সেগুলো অমরতার দাবী করতে পারে। ভাববাণীতে সমৃদ্ধ এরকম শত শত গান মাইজভাণ্ডারকে উপলক্ষ করে লিখিত হয়েছে।
মরমী সাধক মনোমোহন দত্ত প্রথম মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকেই গান রচনার পুলকিত প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অবিস্মরণীয় সংগ্রামী কবিয়াল রমেশ শীল সারাজীবন শুধু মাইজভাণ্ডারি গান রচনা করেই ব্যয় করেননি , মাইজভাণ্ডারি তরিকার আদর্শ তাঁর সমগ্র জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পেরেছিলো। জীবনান্তেও এই আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রচনাটির এখানেই ইতি টানলাম।
(লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা: শাহিদা খাতুন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮, ৪৩-৮ পৃষ্ঠা থেকে প্রবন্ধটি সংগৃহীত।)