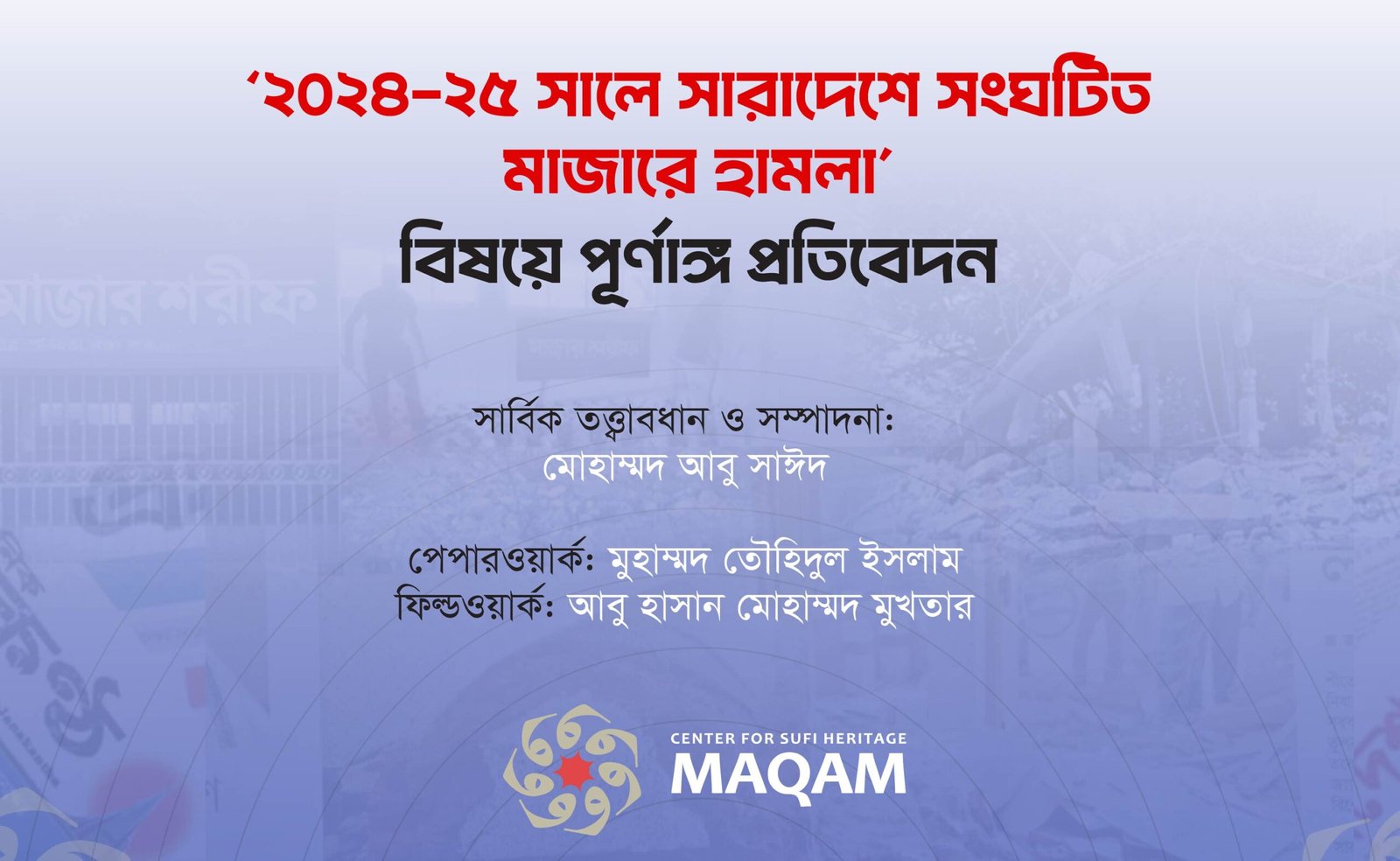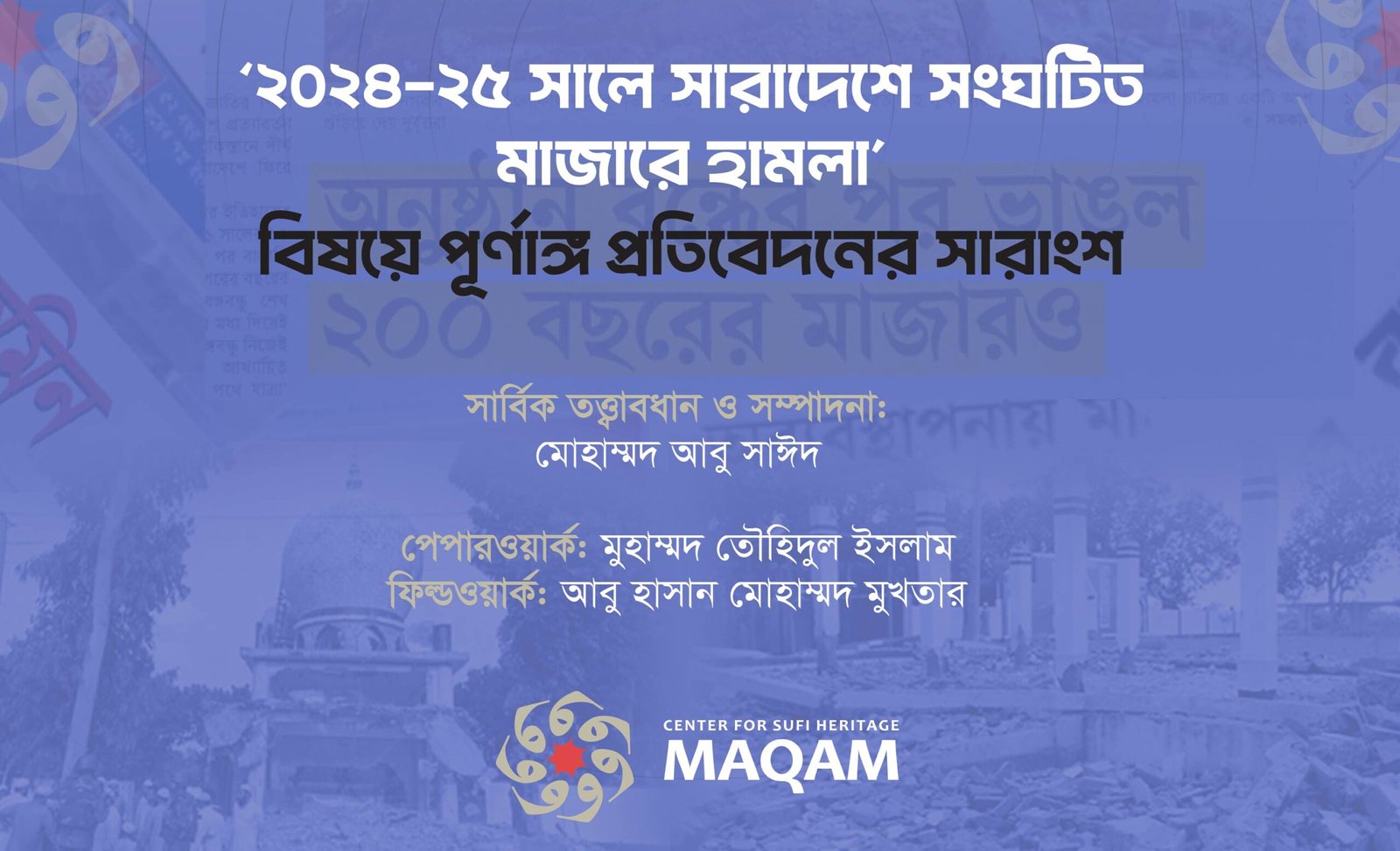সম্পাদকীয় নোট:
১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মোজাম্মেল হকের Some Aspects of the principal Sufi orders in India নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ও চিশতিয়া তরিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ও চিশতিয়া তরিকা সম্পর্কিত অংশটির বাংলা অনুবাদ পাঠক সমীপে পেশ করা হলো।
ইতিহাসের কিছু সূত্র ধরে খাজা গরীবে নেওয়াজ বিষয়ে আলোচনা করায় লেখাটি গবেষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে খাজা গরীবে নেওয়াজের আগমনকাল নিয়ে লেখাটি একটি রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
***
খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ও চিশতিয়া তরিকা
মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
চিশতিয়া তরিকা প্রথমে চিশতিয়াতেই বিকশিত হয়, সেখান থেকে খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতে এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর দ্বাদশ বংশধর। আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের ধারায় তিনি ছিলেন শায়খ আবু ইসহাক শামী চিশতীর নবম বংশধর। শায়খ মুইনুদ্দীন চিশতী ৫৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১৪২ সালে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা চিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[1] সম্ভবত প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাঁর পরিবার খোরাসানের নিশাপুরে হিজরত করেন। খাজা মুঈনুদ্দিন তখন শিশু ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, চিস্তানে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি খোরাসানে প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দীন আহমদ ১১৫৭ সালে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন।[2] তার মা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না, তবে তাঁর নাম ছিল বিবি উম্মুল ওয়ারা। যিনি সম্ভবত তাঁর স্বামী গিয়াসউদ্দীনের আগেই মারা যান। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, মুঈনুদ্দীন তাঁর ১৫ বছর বয়সে সম্পূর্ণ এতিম হয়ে পড়েন, যখন তাঁর পিতা মারা যান।[3]
কথিত আছে, একদিন তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাগানে কাজ করছিলেন, তখন ইব্রাহিম কান্দোজি নামে একজন সুফি সেখানে উপস্থিত হন এবং কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে বসে থাকেন। তাদের কথোপকথনের সময় তিনি নিজের মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিক আলোক অনুভব করেন। অন্তরাত্মা তাঁকে এই মায়ার জগতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে। তিনি তাঁর কোদাল ফেলে তসবিহ হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেন এবং উপার্জিত অর্থ দাতব্য কাজে দান করে দেন। অতঃপর একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সন্ধানে বিচরণকারী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন শুরু করেন। তিনি প্রথমে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় কিতাবাদি পড়েন এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও পারদর্শিতা অর্জন করেন। এরপর তিনি বুখারায় যান যেখানে তিনি মৌলানা শামসুদ্দিন বুখারীর ছাত্র হন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। কিছুদিন পর তিনি ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখানে যাওয়ার পথে খোরাসানের কাসবা-ই-হারুনে পৌঁছান এবং হারুনের একজন বিখ্যাত দরবেশ খাজা উসমানের সঙ্গে দেখা করেন। উসমান হারুনীর আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অভিভূত হয়ে তিনি বিশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন এবং এমনভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন যে তিনি কখনও নিজেকে বিন্দু পরিমাণ আরাম আয়েশের সুযোগ দেননি। তাঁর সঙ্গে থেকে তিনি সুফি আদর্শের গভীর বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে খিরকাহ-ই-খিলাফত অর্জন করেন। পূর্ববর্তী বেশিরভাগ দরবেশ সফরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার অংশ বলে মনে করতেন।[4] মুঈনুদ্দিন নিজেই সফরের জন্য খাজা ওসমান হারুনীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। তিনি বাগদাদ, তাবরিজ, ইস্পাহান ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন এবং আব্দুল কাদির জিলানীর মতো অনেক বিশিষ্ট সুফি শায়খের সঙ্গে দেখা করেন। যেমন: নাজমুদ্দিন কোবরা, শেখ দিয়াউদ্দিন আবু নাজিব সোহরাওয়ার্দী, শেখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ। পশ্চিমে তাঁর সফর শেষ করে তিনি মধ্য এশিয়ার দিকে এগুতে থাকেন এবং বল্খ পরিদর্শন করেন। বলখে তিনি হাকিম দিয়াউদ্দিন নামে একজনকে দীক্ষা দেন এবং বলখের জন্য তাঁকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। অবশেষে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন।
এটি সর্বজনবিদিত যে, সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পেশোয়ার তাঁর অধীনে ছিল এবং শীঘ্রই তিনি লাহোর দখল করেন। ভারতে মুসলিম শক্তির এই প্রতিষ্ঠা দিল্লি ও আজমিরের চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি মুসলিম সেনাপতিদের বিরুদ্ধে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার রক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন মুলতান এবং দিল্লির মধ্যবর্তী সমভূমি সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তবে, তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে এই বিরোধের অবসান ঘটায়। এর ঠিক আগে মুইনুদ্দিন চিশতি মক্কা, মদিনা, ইরাক, ইরান, সমরকন্দ, বুখারা, বল্খ ইত্যাদির উপর তাঁর সফর সম্পন্ন করেন এবং গজনীতে আসেন। যেখান থেকে বলা হয়, তিনি শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি কখন এবং কীভাবে ভারতে এসেছিলেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। প্রাচীন কিতাবাদি, যেমন মীর খুর্দের সিয়ারুল আউলিয়া, হাসান সিজ্জির ফাওয়াইদুল ফুয়াদ, হামিদ কালান্দারের খায়রুল মাজালিসে এমন কোনো উপকরণ নেই যা এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কিছু আধুনিক পণ্ডিত, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে দূরে সরে, প্রাচীন কিছু সুফি সাহিত্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন এবং সেগুলোর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক ইউসুফ হোসেন সিয়ারুল আওলিয়ার উপর নির্ভর করে বলেন যে, খাজা মুইনুদ্দীন চিশতি আজমিরে গিয়েছিলেন যেখানে রাজা পৃথ্বীরাজ শাসন করতেন। সেখানে একজন মুসলিমের সাথে সামান্যতম যোগাযোগকেও অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং কখনো কখনো খাজা গরীবে নেওয়াজকে পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়া হতো না। উচ্চপদস্থ পুরোহিতরা আজমিরের রাজার কাছে দাবি করেন যে, তিনি যেন খাজাকে নির্বাসিত করেন। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথ্বীরাজের জীবদ্দশায় এবং ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের আগেই গরীবে নেওয়াজ আজমিরে আগমন করেন। মৌলভী আব্দুল হক, যার আখবারুল আখিয়ারকে মুঘল আমলের অন্যান্য সুফি সাহিত্যের তুলনায় পণ্ডিতরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন, তিনি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে আজমিরে খাজাকে দেখতে পান এবং বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে খাজা পৃথ্বীরাজের উপর রাগান্বিত হয়ে একটি মন্তব্য করেন।[5] অতঃপর পৃথ্বীরাজকে শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির সেনাবাহিনী জীবিতাবস্থায় বন্দী করে।
অন্যান্য সুফি কিতাবাদিতেও প্রায় একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। মওলানা জামালীই সর্বপ্রথম খাজা গরীবে নেওয়াজের একটি বিশদ জীবনী লিখেছিলেন। লেখক হয়তো তাঁর রচনা— সিয়ারুল আরেফিনের জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি খাজার ইন্তেকালের প্রায় তিনশ বছর পরে এটি লিখেছিলেন, ফলত তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রামাণিক উৎস পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ১২০৫ সালে আজমিরে আসেন। তিনি আরও বলেন যে, খাজা লাহোরে দাতা গঞ্জে বখশের পূর্বসূরী শেখ হোসেন জানজানির সঙ্গে দেখা করেছিলেন।
সম্ভবত মাওলানা জামালির সূত্র ধরে আবুল ফজল আরও লিখেছেন যে, খাজা মুঈনুদ্দিন লাহোরে শায়খ হুসাইন জানজানির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন।[6] প্রকৃতপক্ষে হুসাইন জানজানির উত্তরসূরী দাতা গঞ্জে বখশ ১০৭২ সালে ইন্তেকাল করেন। অতএব, এই সমস্ত তথ্য কেবল ভুলই নয়, বরং অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। আবুল কাসেম ফিরিশতা আরও লিখেছেন যে, খাজা মুইনুদ্দীন চিশতি ১১৬৫ সালে আজমিরে এসেছিলেন। মোল্লা আব্দুল কাদির বদায়ুনি খাজার ভারতে আগমনের সময় ১১৯২[7] এবং আবুল ফজল ১১৯৩ উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনাগুলির মধ্যে আমাদের কাছে মিনহাজুস সিরাজের তবাকাত-ই-নাসিরি রয়েছে, যা সেই সময়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ যা থেকে আমরা ভারতে খাজার আগমন সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। এখানে দেখা গেছে যে, লেখক খাজার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে তরাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে শুনেছেন যেখানে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর সংখ্যাও তিনি বলেছিলেন। খাজা লেখকের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তিনি নিজে সুলতান-ই-গাজী অর্থাৎ সুলতান শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির (তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী) সেনাবাহিনীতে ছিলেন।[8] মিনহাজের এই বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয় এই কারণে যে, ১১৯২ সালে খাজার পক্ষে কোনও বাধাবিপত্তি ছাড়াই ভারতে আসা সম্ভব ছিল, যখন তিনি বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এবং তাদের নেতা অর্থাৎ শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির সঙ্গে ছিলেন। আমাদের মতামত এই যে, মিনহাজ কর্তৃক উল্লেখিত খাজা আজমিরের খাজা গরীবে নেওয়াজের চেয়ে ব্যতিক্রম কেউ ছিলেন না। তাবাকাত-ই-নাসিরির অনুবাদক রাভার্টিও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।
অতএব মিনহাজের বর্ণনা অনুসারে, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি ১১৯২-৯৩ সালে ভারতে আসেন। যদি এটি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, তিনি প্রথমে সরাসরি আজমির যাননি। বিভিন্ন তাজকিরা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি প্রথমে লাহোরে পৌঁছেছিলেন এবং দাতা গঞ্জে বখশের মাজারে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। সম্ভবত তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চিল্লাহ এবং মুরাকাবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। বলা হয় যে, জনমানুষ প্রথম দর্শনেই তাঁকে পছন্দ করত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কথায় মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত ১১৯৩ সালের শেষদিকে দিল্লিতে গিয়েছিলেন যখন সেখানে ইতোমধ্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লির বিপুল সংখ্যক হিন্দু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছিলো এবং তাঁকে মুর্শিদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। খাজা তাদের মন জয় করতে এবং তাদের মনকে আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে সফরের স্থান নির্বাচন নিয়ে তাড়াহুড়ো করেননি। অনুমান করা যায় যে, লাহোর এবং দিল্লিতে তিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবস্থান করেছিলেন। ফিরিশতা লিখেছেন যে, খাজা ১১৬৫ সালে আজমিরে এসেছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম গভর্নর মীর সাইয়্যেদ হোসেন মাশহাদি তাঁকে আজমিরে অভ্যর্থনা জানান। এই দুটি তথ্য পরস্পরবিরোধী। ফিরিশতার মতো একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে এই দুটি বিপরীত মতের সমন্বয় করা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। ১১৬৫ সালে আজমিরে খাজা মুইনুদ্দীন চিশতির আগমন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক নিযুক্ত আজমিরের মুসলিম গভর্নর মীর সাইয়্যেদ হোসেন মাশহাদি কর্তৃক তাঁর অভ্যর্থনা।অথচ, ১১৬৫ সালে তুর্কিরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তারা আজমিরকে তাদের অধীনে নিয়ে যাবে এবং আধিপত্য বিস্তার করবে। এই পরিস্থিতিতে এটা ভাবা যুক্তিসঙ্গত যে, ৫৯১ হিজরীর জায়গায় সম্ভবত ভুলভাবে ৫৬১ হিজরী লেখা হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, ১১৯৫ সালে পৃথ্বীরাজ মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং যখন তিনি আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা বুঝতে পারেন তখন তিনি তার পুরো বাহিনীসহ চিতায় আত্মাহুতি দেন। এরপর কুতুবুদ্দিন আইবেক আজমীরে প্রবেশ করেন, দখল করেন এবং সেখানে একজন মুসলিম অফিসার নিযুক্ত করেন।[9] তিনি আজমীরের প্রথম মুসলিম অফিসার ছিলেন কিন্তু কেউ তার নাম উল্লেখ করেনি। আমরা মনে করি, এই অফিসার আর কেউ নন, মীর সাইয়্যেদ হোসেন মাশহাদি যিনি ১১৯৫ সালে আজমীরে প্রবেশের সময় খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতীকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন।
সম্ভবত ফিরিশতা ৫৯১ হিজরি লেখার পরিবর্তে ৫৬১ লিখেছিলেন, আরবি সংখ্যার ৬/৯ কাছাকাছি হবার কারণে এটি ঘটতে পারে। আমাদের মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ফিরিশতা তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের তারিখ এবং আজমিরের একজন মুসলিম গভর্নরের নিয়োগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন। তিনি আরও জানতেন যে, তুর্কিদের দ্বারা বিজয়ী হবার আগে আজমিরে একজন মুসলিম গভর্নরের নিয়োগ অবাস্তব। অতএব, আমরা নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, হুসেন মাশহাদি ১১৯৫ সালে কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক আজমিরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী একই বছর আজমিরে আবির্ভূত হন।
আজমিরে বসতি স্থাপনের পর তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রামাণিক উৎস থেকে খুব কমই জানা যায়। সুফি সাহিত্যে তাঁর উক্তি এবং অলৌকিক কাজের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা আমরা স্কিপ করছি। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যথাসাধ্য শরীয়ত মেনে চলতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি জাগতিক বিষয়গুলোকে অবহেলা করতেন না। তিনি সম্পত্তির মালিক ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন এবং সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিবি আসমাতুল্লাহ, যিনি আজমিরের প্রথম মুসলিম গভর্নর সাইয়েদ হুসেন মাশহাদির চাচা ওয়াজিহুদ্দিন মাশহাদির কন্যা। তাঁর তিন পুত্র ছিল—খাজা আবু সাইদ, খাজা ফখরুদ্দিন এবং খাজা হুসামুদ্দিন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন আমাতুল্লাহ, একজন হিন্দু রাজপুত্রের কন্যা, যিনি কোনো যুদ্ধে বন্দী হয়ে খাজাদের কাছে হাজির হন এবং খাজা তাঁকে শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ করেন। তিনি বিবি জামাল হাফিজ নামে একটি কন্যা এবং দুই পুত্রের জন্ম দেন যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যান। জামাল হাফিজ বড় হয়ে ওঠেন এবং একজন বিখ্যাত মহিলা হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে সুফিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মহিলাদের মধ্যে মুরিদ করানোর অনুমতিও লাভ করেন। তিনি শায়খ রাদির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, যারা শৈশবেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে খাজার দরগাহের প্রাঙ্গণে দাফন করা হয় এবং তাঁর সন্তানদেরও একই দরগায় তাঁদের মায়ের কদম বরাবর সমাহিত করা হয়।
মনে হচ্ছে, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিলেন। ফুতুহ (অনাকাঙ্ক্ষিত দান) ছাড়াও তাঁর জমিদারি (লাখেরাজ) সম্পত্তি থেকে যথেষ্ট আয় হতো। বলা হয় যে, আজমিরে একটি গ্রাম জায়গির ছিল। সেই গ্রাম থেকে বার্ষিক আয় তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে আজমিরের রাজস্ব কর্মকর্তারা কিছু বাধাবিপত্তি তৈরি করেন। যে কারণে তিনি দিল্লি যান এবং তৎকালীন শাসক সুলতান ইলতুৎমিশের (১২১০-১২৩৬) কাছ থেকে তাঁর পুত্রদের পক্ষে একটি নতুন দলিল সংগ্রহ করেন।
খাজা খুবই সরল ও ধার্মিক জীবনযাপন করতেন। তিনি মোটা পোশাক পরতেন এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতেন। কথিত আছে যে, তিনি ৮ম দিনে পাঁচ গ্রাম ওজনের একটি শুকনো যবের রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতেন। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং কখনও আগ্রাসন প্রচার করতেন না। মুসলিম এবং হিন্দু উভয়ের কাছেই তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম পালন করতেন, তবুও তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁকে ফুতুহ (নজর, নেয়াজ)পাঠাতেন।
ভারতের এই মহান সাধক ১২৩৬ সালের ৬ই রজব ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি যে কক্ষে থাকতেন সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। মূলত তাঁর মাজারের উপরে কোনও পাকা সমাধি ছিল না। প্রায় তিনশ বছর ধরে আজমিরে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত করা হয়েছিল। খিলজিদের শাসনামলে তাঁকে জনগণের নজরে আনা হয়। কাজী হামিদুদ্দিন নাগোরির বংশধর মাখদুম খাজা হোসাইন নাগোরির নির্দেশে সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজি (১৪০৯-১৫০০) খাজার মাজারের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি পাকা স্থাপত্য/দরগাহ নির্মাণ করেন। সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য শাসকরা এতে ভবন যোগ করেন। সম্রাট আকবর দরগাহে আকবরী মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বাংলার যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত দুটি ঢোল মাজারে উপহার দেন। যুবরাজ জাহাঙ্গীরও বেশ কয়েকবার মাজার পরিদর্শন করেন এবং উপহার প্রদান করে খাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সম্রাট শাহজাহান সমাধিসৌধের উপরে একটি চমৎকার গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং দরগার পশ্চিমে সাদা মার্বেলের জামে মসজিদটি নির্মাণ করেন।
এই মহান সাধক আমাদের মাঝে নেই কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ প্রতিদিন তাকে স্মরণ করে, এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। প্রতি বছর উরসের সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ মাজার জিয়ারত করতে যায়। যারা ব্যক্তিগতভাবে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখেন না তারা দরগাহ শরীফে তাদের অনুদান পাঠাতে ভুল করেন না, তা যত কমই হোক না কেন। একজন অসাধারণ সুফি হিসেবে মুঈনুদ্দিন চিশতী ভারতীয় উপমহাদেশের সুফিধারায় স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ইবনুল আরাবীর ওয়াহদাতুল ওজুদ মতাদর্শ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইবনুল আরাবী বলতেন যে, প্রেমিকের হৃদয় সর্বদা প্রেমের আগুনে জ্বলে। ভেতরে যা আসে তা জ্বলে, কারণ প্রেমের আগুনের চেয়ে বেশি জ্বলন্ত আর কোনও আগুন নেই। এই সর্বেশ্বরবাদী ব্যবস্থায় তিনি প্রেমিক, প্রেয়সী এবং প্রেমকে এক বলে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এটি প্রচার করেছিলেন, যারা পালাক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে এটি প্রচার করেছিলেন এবং শায়খ আহমদ সিরহিন্দির উত্থান পর্যন্ত এর প্রচারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেছিলেন।
খাজা তাঁর মুর্শিদ উসমান হারুনীর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে এগুলো তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনটি জিনিস মানুষকে আল্লাহর ভালো বন্ধু করে তোলে: নদীর মতো উদারতা, সূর্যের মতো স্নেহ এবং মাটির মতো নম্রতা। তিনি অভাবীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দুস্থদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার, অসহায়দের চাহিদা পূরণ করার এবং দরিদ্রদের খাদ্য সরবরাহের জন্য চেষ্টা করতেন। এই কাজগুলোকে তিনি খোদার প্রতি ভালোবাসার সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।
সুফিদের মধ্যে চিল্লাহ নামে একটি প্রথা প্রচলিত আছে। চিল্লাহে থাকা ব্যক্তিকে চল্লিশ দিন ও রাত ধরে একটি গোপন ও নির্জন স্থানে ধারাবাহিকভাবে নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুশীলনে মশগুল থাকতে হয়। এটি মসজিদে, জঙ্গলে অথবা যে-কোনো সাধকের সমাধির আশেপাশে করা যেতে পারে। চিশতিয়া সুফিরা সাধারণত এই চিল্লাহ করেন। তারা চিল্লাহ-ই-মাকুস নামে পরিচিত ভিন্ন ধরণের একটি চিল্লাও করে থাকেন। এটি সাধারণত গাছে এবং কূপে করা হয়। এখানে সালিক তার পা শক্ত দড়ির এক প্রান্তে এবং গাছের ডাল অন্য প্রান্তে বেঁধে কূপের ভেতরে মাথা নিচু করে ঝুলে অজিফা আদায় করেন। এটি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অত্যন্ত কঠিন পদ্ধতি। বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকারই ছিলেন একমাত্র সাধক যিনি কখনো কখনো এই ধরণের চিল্লাহ সম্পন্ন করেছিলেন।
চিশতিয়া তরিকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সামা বা সঙ্গীত শ্রবণ। ইসলামে কখন এবং কীভাবে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। আমরা দেখতে পাই যে, এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতি সামার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বলা হয়, দেশে তীব্র খরার কারণে সুলতানসহ লোকেরা শায়খের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং বৃষ্টির জন্য তাঁর কাছে দোয়া কামনা করছিলেন। এরপর তিনি একটি সামার আয়োজন করেছিলেন এবং যখন সামার দলটি বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তখন এত প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছিল যে, লোকেরা শায়খের কাছে আবার বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তার দোয়ার ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। উলামাদের মতে, ইসলামে সামা বৈধ নয়, তবে সুফিরা এতে কোনও আপত্তি খুঁজে পান না। তাদের কাছে এটি বরং আনন্দের একটি উপায়। হজরত দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী বলেন, “যারা সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে তারা খোদার আদেশ পালন করার জন্য তা করে, তবে আলেমরা একমত যে বাদ্যযন্ত্র শোনা জায়েজ, যদি একে খোদার প্রেম থেকে বিমুখ করার জন্য ব্যবহার না করা হয় এবং মনকে খারাপ দিকে প্ররোচিত না করা হয়।” এই ধরণের যুক্তি চিশতীয়া তরিকার লোকেরা সামার পক্ষে ব্যবহার করেন। এই ধরণের সঙ্গীত উৎসবে তারা পরমানন্দে চলে যান এবং কখনো কখনো এটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, এতে প্রাণহানিও হতে পারে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতীর প্রধান খলিফা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি একবার সামার একটি পঙ্ক্তি শুনে হঠাৎ করেই আনন্দের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং চার দিন ধরে সেই অবস্থায় ছিলেন। পঞ্চমদিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিশতিয়া সাধকদের মধ্যে এখনও সামার প্রচলন রয়েছে।
চিশতিয়া সুফিরা যদিও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিলেন, তবুও তারা জাগতিক জগতের সাথে যোগাযোগ হারাননি। তাঁরা যে সমাজে বসবাস করতেন সে সমাজ ও জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজস্ব শ্রম দিয়ে অনুর্বর জমি চাষ করার এবং ফুতুহ গ্রহণ করার অনুমতি ছিল। কিন্তু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার এই বিষয়ে ভিন্ন মতামত ছিল। তিনি প্রধান খলিফাদেরকে সকল দুনিয়াবি বন্ধন পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সুলতান এবং তাদের কর্মকর্তাদের সাথে মেলামেশা করা উচিত নয় এবং তাঁদের জীবিকা নির্বাহেরও প্রয়োজন নেই। তাঁদের সম্পূর্ণভাবে খোদার উপর ভরসা করতে হয়েছিল। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন—“ক্ষুধার্ত থাকো এবং আল্লাহর মেহমান হও”। তাই ফুতুহই ছিল জীবিকার একমাত্র উপায় যার অনুমতি তিনি শিষ্যদের দিয়েছিলেন।