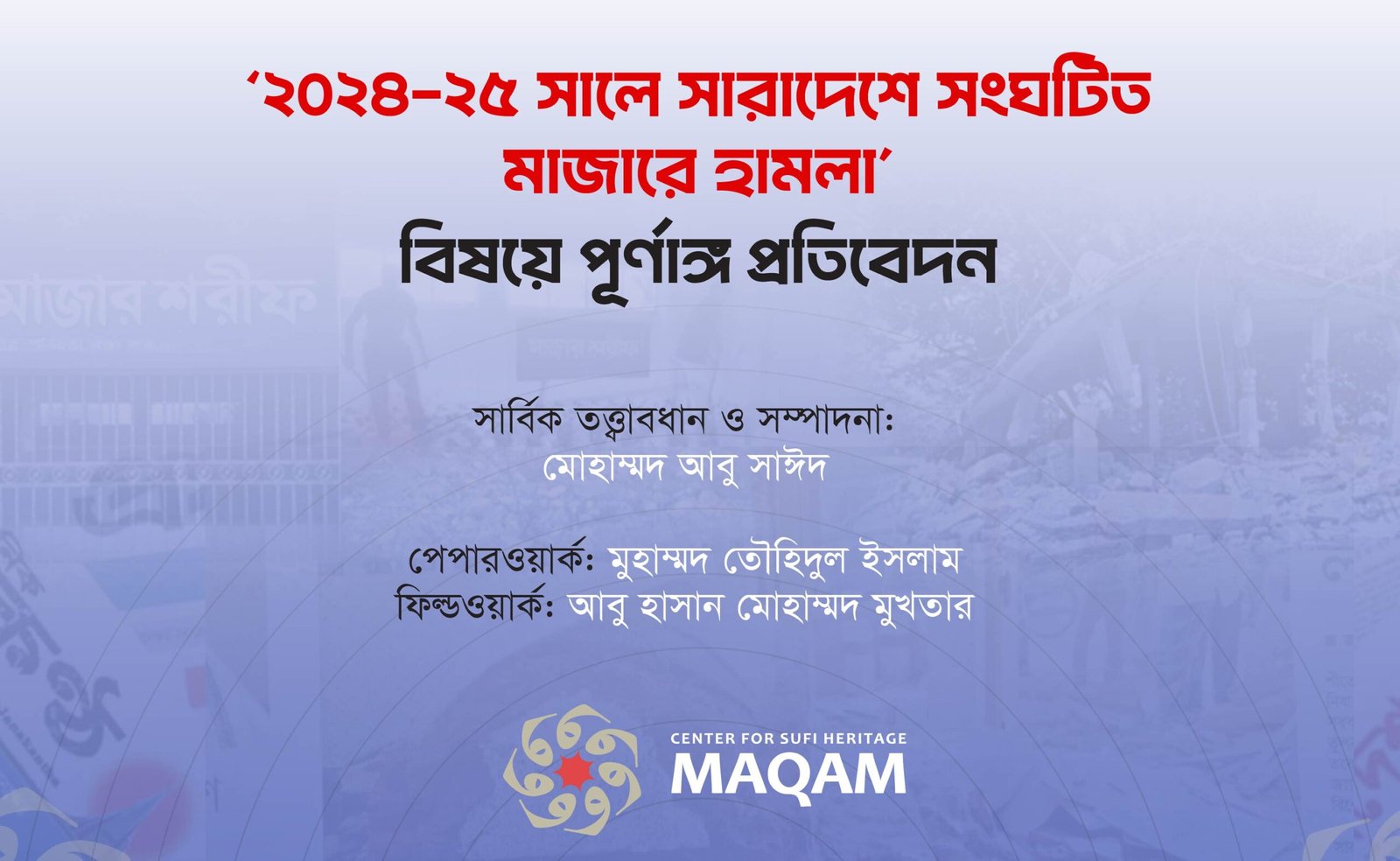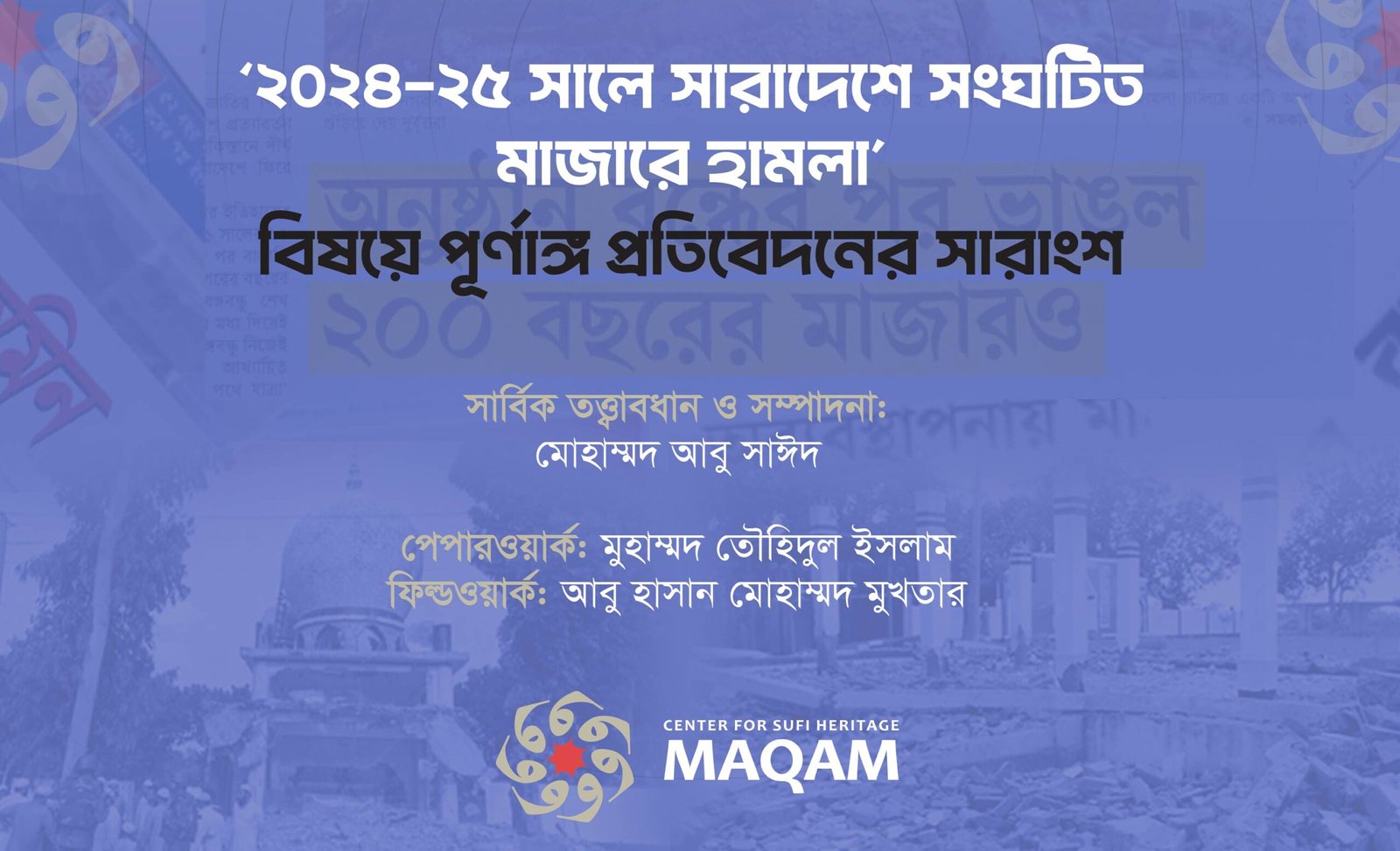ভূমিকা: ইসলামি আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে সুফি ঐতিহ্য একটি অনন্য ও বহুমাত্রিক ধারার নাম, যা কেবল ধর্মীয় অনুশীলনের একটি রূপ নয়, বরং এক গভীর অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধান এবং আত্মিক মুক্তির পথ। সুফি ঐতিহ্য তার জন্মলগ্ন থেকেই মানবীয় সত্ত্বার সঙ্গে খোদায়ীসত্ত্বার মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহ্যের ইতিহাসে পুরুষ সুফিদের নাম যেমন বহুল প্রচলিত, তেমনি নারীর উপস্থিতি ও অবদানও গভীর কিন্তু উপেক্ষিত। নারী সুফিরা শুধু অনুসারী ছিলেন না বরং তারা ছিলেন এই ধারা নির্মানের অন্যতম কারিগর। তারা ছিলেন সুফি ঐতিহ্যিক দর্শনের নির্মাতা, যুগেযুগে পরম্পরা ধরে গড়ে ওঠা আচার-অনুষ্ঠানের ধারক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রবর্তক।
আশ্চর্যজনকভাবে প্রাচ্যের ঐতিহাসিকেরা নারীসুফি বা সুফি ঐতিহ্যে নারীর অবস্থান নিয়ে খুব বেশী দৃষ্টিপাত করেননি। প্রাচ্যবিদরাও বহুবছর যাবত ইসলামে নারীর অবস্থানকে খুবই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। কিন্তু বিগত অর্ধশত বছর জুড়ে এই ধারায় খানিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইসলামী ঐতিহ্যে বিশেষত ইসলামের সুফি ঐতিহ্যে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত বয়ান উৎপাদনে বর্তমানে প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই বয়ান উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সাচুকি মুরাতা, এনিমেরি শিমেল, রিকা ইলারুই কর্নেল, জাহরা তাহেরি, অ্যালেক্সান্ডার পাপাস, ভিনসেন্ট কর্নেল, নাদিয়া মারিয়া, আজিজা সানাজারোভাসহ বেশ কিছু স্কলার। এ প্রসঙ্গে তাদের গবেষণাগুলো নারীত্বের নৈর্ব্যত্তিক সত্ত্বাকে (divine feminine) তুলে ধরেছে। বিশেষ করে নারীর দৈহিক তথা বাহ্যিক সুরতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা খোদায়ী গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[1] ধুলোর আস্তরণ পড়ে থাকা এই আখ্যানগুলোকে নতুন করে উৎপাদন করতে তাদেরকে প্রাচীন টেক্সট ঘাটতে হয়েছে। কিন্তু বিষ্ময়করভাবে এসব টেক্সটগুলোতে নারী/নারী সুফিদের অবস্থান খুবই সীমিত। আশ্চর্যজনক কিন্তু সত্য এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাউরি সিলভার বলেন- ‘প্রথম যুগের সুফি নারীদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা রয়েছে: নারীরা প্রধান উৎসগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত। যে গ্রন্থগুলো সুফি ঐতিহ্যের ইতিহাস, অনুশীলন ও চিন্তাধারাকে সংজ্ঞায়িত করেছে, সেগুলোতে নারীদের উপস্থিতি খুবই সীমিত’।[2]
প্রাচীন যে সকল টেক্সটগুলোর মধ্যে এসকল ধার্মিক ও সুফি নারীর বিবরণ উল্লেখ আছে তার মধ্যে আবু আবদুর রহমান আল-সুলামি’র (মৃ. ৪০২ হি./১০১২ খ্রি.) যিকরুন নিসুয়াতিল মুতাআব্বিদাতিস সুফিয়্যাত, আবু আল-ফারাজ ইবন আল-জাওযি’র (মৃ. ৫৯৭ হি./১২০০ খ্রি.) সিফাত আল সাফওয়া এবং মুহাম্মদ ইবন সা’দের (মৃ. ২৩০ হি./৮৪৫ খ্রি.) তাবাকাত আল কুবরা অন্যতম। তবে এই গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি সুফি ঐতিহ্যের মূল গ্রন্থ এবং সেখানে উল্লেখিত নানা তত্ত্বাবলীতে রাবিয়া আল-আদাবিয়া (বাসরা, মৃ. ১৮৫ হি./৮০১ খ্রি.) ছাড়া খুব বেশী নারী সুফির উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন- আবু তালিব আল-মাক্কি’র (মৃ. ৩৮৬ হি./৯৯৬ খ্রি.) কুত আল-কুলুব, আবু বকর আল-কালাবাদি’র (মৃ. আনুমানিক ৩৮০ হি./৯৯০ খ্রি.) তাআরুফ, আবু নাসর আল-সাররাজের (মৃ. ৩৭৮ হি./৯৮৮ খ্রি.) কিতাব আল-লুমাʿ, আবু আল-কাসিম আল-কুশাইরি’র (মৃ. ৪৬৫ হি./১০৭২ খ্রি.) রিসালাতুল কুসাইরিয়া এবং আবু আল-হাসান আল-হুজভিরির (মৃ. ৪৭০ হি./১০৭৭ খ্রি.)কাশফুল মাহজুব । শুধু তাই নয়, এমনও দেখা যায় যে, প্রাচীন এই টেক্সটগুলোতে নারীসুফিদের অংশগ্রহণ থাকলেও সেখানে নামোল্লেখ করা হয়নি। যেমন- আবু বকর আল কালাবাদি’র গ্রন্থে ফাতিমা নিশাপুর ও জুননুন মিশরীর একটি বাহাসের ঘটনার উল্লেখ আছে কিন্তু বাহাসে অংশ নেয়া জুননুন মিশরির নামোল্লেখ থাকলেও ফাতিমা নিশাপুরীর নাম অনুপস্থিত।[3] একইরকম ঘটনা না হলেও কাছাকাছি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ইমাম কুশাইরির কিতাবে। সেখানে উল্লেখিত অধিকাংশ নারীই নামোল্লেখ ছাড়াই কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী, নইলে মা অথবা বোন। তার বর্ণনায় দেখা যায়- সুফিদের সাথে নারীদের প্রায়শই কথা হয়, এমনকি সুফিরা এসকল নারীদের কাছ থেকে উপদেশও নেন। তিনি এদেরকে নিয়ে কিছুদূর বর্ণনা করেন কিন্তু হঠাৎ করেই এই নারীরা দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যান। ইমাম কুশায়রি নারীদের দ্বারা সুফিদের প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করতেন। তিনি ভক্তদের বলতেন, ‘নারীদের কাছ থেকে সেবা বা সহানুভূতি গ্রহণ করা উচিৎ নয়’।[4] এদের বর্ণনাগুলোর মধ্যে পারিবারিক-সামাজিক ক্ষমতাবলয়ের পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষণীয় যার অন্যতম কারণ হলো এই জীবনীগ্রন্থগুলোর লেখকগণ পুরুষ। এ বিষয়ে সাদিয়া শেখ বলেন-
সুফি জীবনী সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত সমস্যা সামনে আসে। অন্যান্য প্রাক-আধুনিক সাহিত্যের মতোই, তাবাকাত ঘরানার রচয়িতা ও স্রষ্টারা ছিলেন পুরুষ। খুব কম বা প্রায় নেই বললেই চলে এবং ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাচীন সুফি নারীরা শুধু পুরুষ জীবনীকারদের আঁকা চিত্রের মাধ্যমেই ইতিহাসে হাজির হন। নারীবাদী ইতিহাসবিদরা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পাঠগুলোর অধিকাংশই পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পাঠ্গুলোর মধ্যে নারীদের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার যে চ্যালেঞ্জ, তা শুধু ইসলাম বা সুফি ঐতিহ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত সমস্যা।[5]
তবে এই ধারা সকল জীবনীকারের মধ্যে দেখা যায় না। আল-সুলামি ও ইবন আল-জাওযির রচনায় ভিন্ন চিত্র দৃশ্যমান হয়। এদের রচনায় কিছু পুরুষকে দেখা যায়, যারা নারীদের জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের বিবরণে নারীরা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, কখনো নামসহ কখনো নামহীন অবস্থায়। যেমন—আল-হাকিম আল-তিরমিজি (মৃ. ৩২০ হি./৯১০ খ্রি.) দুর্দান্তভাবে তার স্ত্রীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্যদের বর্ণনার চেয়ে সুলামী ও জাওজীর বর্ণনাগুলো অধিক বস্তুনিষ্ঠ এবং ‘পিতৃতান্ত্রিক’ প্রবণতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। সুলামীর কিতাবের অনুবাদক রিকা ইলারুই কর্নেল দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু পুরুষ জীবনীকার নারীত্বের ধারণা ও সুফি নারীদের চিত্রায়ণে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তারা সুফি নারীদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় যোগ্যতায় পুরুষ সুফিদের সমকক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আবার সুলামীর মতো আবু আল-ফারাজ ইবন আল-জাওযি (মৃ. ১২০১) একই নারীদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি আবেগপ্রবণ এবং “নারীসুলভ” হিসেবে চিত্রিত করেছেন।[6]
ঐতিহাসিক সুফি টেক্সটগুলোতে নারী সুফি ও নারীদের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে তুলনামূলক কম একথা অস্বীকারের সুযোগ নেই। তবে একথাও সত্য যে, নারী সুফিদের মতো আরো অনেক পুরুষ সুফির নামও নানা কারণে ঐতিহাসিক টেক্সট থেকে হারিয়ে গেছে। সর্বোপরি সত্য হলো- প্রাথমিক সুফি সাহিত্যে বা ঐতিহাসিক তথ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিবরণ এতটাই কম যে, নারীদের সুফি অনুশীলন, জ্ঞান ও শিক্ষার বিকাশ, সংরক্ষণ এবং প্রচারে প্রান্তিক হিসেবে দেখা হয়।[7] ঐতিহাসিক টেক্সটগুলোতে প্রান্তিক, বেনামা নারীসুফিদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই কিন্তু ইতিহাস জুড়ে তাদের অপ্রকাশিত হাজিরাও ছিলো যার নানা ইশারা পরোক্ষভাবে টেক্সটগুলোতে রয়ে গেছে। এসকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুফি ঐতিহ্যে নারী সুফিদের ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে দুটি প্রক্রিয়াতে। প্রথমটি হলো মেটাফিজিক্যাল দিক— সুফি চিন্তায় নারীত্বকে (ফেমিনিন) শুধু একজন লৈঙ্গিক নারী হিসেবে নয় বরং একটি আধ্যাত্মিক প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই প্রতীকটি দ্বারা বোঝানো হয় —আল্লাহর সত্তা (ধাত), সৃষ্টি, রহস্য, করুণা, কোমলতা এবং প্রেমের উৎসকে। সুফিরা মনে করেন, নারীত্বের ভেতরে এমন কিছু গুণ আছে—যেমন গোপনতা, গভীরতা ও আলোর উৎস—যা আল্লাহর প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি হলো ঐতিহাসিক দিক—যেখানে সুফি সিলসিলার নারী অনুশীলনকারীরা সুফি ঐতিহ্যের বিকাশ ও ইতিহাসে কী ভূমিকা রেখেছেন, তার বিশ্লেষণ করা। যদিও অধিকাংশ নারীদের সামাজিক ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সীমিত ছিল। তবে অনেক নারী সুফি এই আধ্যাত্মিক পথে এমন একটি পরিসর খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পেরেছেন। এমনকি তাদের মৌলিক অবদানও সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও তা সবসময় সহজে গ্রহণ করা হয়নি।[8]
মেটাফিজিক্যাল স্তর: নারীত্বের আধ্যাত্মিক সিম্বোলিজম
সুফি ইবনুল আরাবি, শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, জালালুদ্দিন রুমি, সদর উদ্দিন চিশতী এবং প্রাচ্যবিদ হেনরি করবিনের মতো চিন্তাবিদরা নারীত্বকে আধ্যাত্মিক আয়না, আলোর উৎস এবং আত্মার প্রতিচ্ছবি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, বিশেষ করে ইবনুল আরাবীর মতে, ‘পুরুষের তুলনায় নারীসত্ত্বার মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ও নিখুঁত’।[9] নারীত্ব হলো সেই গর্ভধারণকারী শক্তি, যার মাধ্যমে পরমসত্তা নিজেকে প্রকাশ করে। সুরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ইয়া আইয়ুহান্ নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাজি খালাকাকুম মিন নাফসি ওয়াহিদাতি ওয়া খালাক্বা মিনহা’ অর্থাৎ হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এককসত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে উল্লেখিত ‘এককসত্ত্বা’ শব্দটি এসেছে আরবি ‘ওয়াহিদাতিন’ শব্দ থেকে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এই শব্দটি নারীবাচক। এমনকি আল-কোরানে এই শব্দটির শেষে যে সিম্বল (ة – তামারবুতা) ব্যাবহার করা হয়েছে তাও নারীবাচকতা অর্থেই ব্যাবহৃত হয়। সমসাময়িক কালের সুফি হিলালুজ্জামান হিলাল এ সম্পর্কে বলেন-
‘সুফির বিবেচনায়, [সুরা নেসায় উল্লেখিত] (زوجها)- জাওজুহা শব্দদ্বয়ে থাকা স্ত্রীবাচক ها-হা সর্বনামটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃত কথা হলো, যা সৃষ্টিধর্মী তার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয় ‘নারী’ কে। নারী-ই সৃজনশীল, সৃষ্টিশীলতার মূলাধার। সে কারণে যে মূল সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকেও নারীবাচক সত্ত্বা তথা সৃজনশীল সত্ত্বা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় যাকে বলা হয়েছে ‘একক সত্ত্বা’ তা মূলত (نفس واحدة) – নাফসে ওয়াহিদা, যা স্ত্রীবাচক’ ।[10]
সুফি দর্শনে নারীত্বের সিম্বলিক হাজিরা কেবল সৃষ্টির রহস্য নয়, বরং সৃষ্টির উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ গুণাবলি এবং অস্তিত্বের মৌলিক প্রকৃতির দিকেও গভীর ইঙ্গিত বহন করে। নারীসত্ত্বা যেমন গর্ভধারণের মাধ্যমে নতুন প্রাণের সূচনা করে, তেমনি পরমসত্ত্বা আল্লাহ নিজের রহমত, করুণা ও প্রেমের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধারণ করেন এবং তা অব্যাহত রাখেন। এই গর্ভধারণের ক্ষমতা শুধু জৈবিক নয় বরং আধ্যাত্মিক। এ আধ্যাত্ম ধারণায় নারী হয়ে ওঠে সৃষ্টির ধারক, বাহক এবং রহস্যময় উৎস। সুফি চিন্তায় নারীত্বকে দেখা হয় এমন এক প্রতীক হিসেবে, যা আল্লাহর সত্ত্বার কোমলতা, রহমত ও গোপনীয়তার প্রতিফলন। জালালুদ্দীন রুমি বলেন, ‘নারী সৃষ্ট নয় বরং সৃষ্টিশীল (কারো কারো অনুবাদে স্রষ্টা, যেমন- গবেষক জাহরা তাহেরি)’—এই বক্তব্য নারীত্বকে কেবল একটি সামাজিক বা জৈবিক পরিচয় নয় বরং একটি আধ্যাত্মিক আয়না হিসেবে তুলে ধরে। এই আয়নায় সৃষ্টি নিজের সত্ত্বাকে দেখে, নিজের সত্ত্বার উৎসকে চেনে এবং সেই চেনা প্রতিচ্ছবির মধ্যেই আল্লাহর রহমত, রহমানিয়াত ও গফুরিয়াতের প্রকাশ ঘটে।
সুরা তাওবা বাদে কোরানে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সুরা শুরু হয়েছে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম’ বাক্যের মাধ্যমে। বাক্যটিতে উল্লেখিত ‘রহমান’ ও ‘রহিম’ শব্দ দুটিই মূলত প্রধান এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম শব্দটির অর্থ পরম ক্ষমাশীল এবং দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ পরম দয়ালু। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দদ্বয়ের ধাতুমূল ‘রেহেম’- যার আভিধানিক অর্থ গর্ভাশয়, যা একটি নারীবাচক শব্দ। অর্থাৎ ‘ক্ষমা’ এবং ‘দয়া বা করুণা’ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্টির সকল অস্তিত্বের শুরু, যা মূলত নারীবাচক জায়গা থেকে উদ্ভূত। এ দু’টি শব্দের উৎসগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এনিমেরি শিমেল আধ্যাত্মিক অর্থে সৃষ্টজগতের প্রতি সৃষ্টিকর্তার এসেন্সকে ‘মাতৃসুলভ ভালোবাসা’ বা ‘মাতৃত্বপূর্ণ প্রেম’ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।[11] তিনি রুমির বয়ান এনে দেখিয়েছেন, মানুষ হলো এক গর্ভবতী নারীর মতো, যার অন্তরে খোদায়ী রহস্য লুকিয়ে থাকে—যা প্রতিটি পদক্ষেপে ক্রমশ বড় হয় এবং আরও গভীরতর হয়ে ওঠে।[12]
এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীত্বের যে প্রতীক তা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য বা সৃষ্টির রূপ নয়, বরং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তথা রহমত, ক্ষমা, প্রেম ও আত্মিক সংযোগের প্রতিফলন। ফলে নারীত্ব হয়ে ওঠে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি, যার মাধ্যমে সৃষ্টি কেবল শুরু হয় না, বরং তা আল্লাহর গুণাবলির ধারায় প্রবাহিত হয়। এই উপলব্ধি আমাদেরকে নিয়ে যায় সেই আলোচনায়, যেখানে আল্লাহর সৃষ্টি রহমতের রূপ হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং আমাদের নফসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলোও আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। মানুষ হলো খোঁদার ‘গর্ভাশয়ে’ জন্ম নেয়া মাখলুকাত। জন্ম হওয়ার আগ পর্যন্ত সে ‘স্যাক্রেট’ তথা পবিত্র কিন্তু তার আগমনীর পর থেকে সে ধীরে-ধীরে মামুলি জীবনে প্রবেশ করে। সময়, কাল, পরিবেশসহ নানা প্রভাবকের মাধ্যমে সে ‘কন্টামিনেটেড’ হয়। ‘স্যাক্রেট’ জীবন থেকে ‘কনটামিনেটেড’ জীবনে প্রবেশের এই ধারায় মানুষ নফসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, যার শুরু কোরানে উল্লেখিত নফসে আম্মারার মাধ্যমে (আত্মাকে মন্দের দিকে টানার প্রবৃত্তি)।
ইমাম গাজালী নারীর চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কখনো কখনো নারীসত্ত্বাকে নফসে আম্মারার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে আত্মসংযম, লালসা ও কামনা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি নারীকে সামনে এনেছেন। তার মতে, নারী যেমন পুরুষের জন্য এক ধরনের পরীক্ষা হতে পারে, তেমনি নফসে আম্মারাও মানুষের আত্মার জন্য এক অন্তর্নিহিত পরীক্ষা।
কিন্তু রাবেয়া বসরী দেখাচ্ছেন ভিন্ন আলাপ। একটি বর্ণনা মতে দেখা যায়, কিছু ধার্মিক লোক বহুদূর থেকে রাবেয়ার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। তারা তাকে উসকানি দিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করে। তারা বলে, “সব গুণ পুরুষদের মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের মুকুট পুরুষদের মাথায় পরানো হয়েছে। মর্যাদার বাধন পুরুষদের কোমরে বাঁধা হয়েছে। কোনো নারী কখনো নবী হননি।” রাবিয়া শান্তভাবে উত্তর দেন, “সবই ঠিক, কিন্তু অহংকার, আত্মপূজা, আমিই শ্রেষ্ট এবং ‘আমি তোমাদের খোঁদা’—এ ধরনের কথাগুলো কখনো কোনো নারীর হৃদয় থেকে বের হয়নি… এসব তো পুরুষদেরই বিশেষত্ব।” এভাবে রাবিয়া দেখান যে নফসে আম্মারা কীভাবে পুরুষদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক অহংকার ও আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছে, যা তাদের সত্য ও ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ থেকে অন্ধ করে রেখেছে। বিশেষভাবে, রাবিয়া সুফি দর্শনের মূলনীতিটি তুলে ধরেন, তিনি দেখান আত্মার অবস্থান এবং আল্লাহর প্রতি সঠিক অভিমুখই সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়। এই অভিমুখ থেকে বিচ্যুত করে এমন সবকিছু—যেমন সামাজিক মর্যাদা, লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে।[13]
নফসকে অতিক্রম করে তথা কোরানে উল্লেখিত নফসের তিনটি স্তরকে অতিক্রম করে মানুষ তার মূল বা ‘ধাতে’র দিকে ধীরে-ধীরে ধাবিত হয়। নফসের এই তিনটি স্তর হলো পূর্বে উল্লেখ করা নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়ামা এবং নফসে মুতমাইন্না। নফসে আম্মারা হলো সেই নফস, যে প্রতিবাদ ত্যাগ করে। কাম, রিপু ও প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি চালিত হয় এবং শয়তানের পায়রাবি করে। আল্লামা শাওকানীর মতে, নফসে আম্মারা হলো মানবীয় নফসের কাম প্রবৃত্তি, যার কাজ মন্দ কাজের আদেশ করা। জন্মগত স্বভাবের কারণে কামরিপু দ্বারা প্রভাবিত করা।[14] কোরানে উল্লেখিত নফসের দ্বিতীয় স্তর নফসে লাওয়ামা হলো নফসের সেই অবস্থা যখন মানুষ তওবার স্তরে পৌছায়। অর্থাৎ মানুষ তার নফসে আম্মারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্বকৃত নানা মন্দকাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। সুফিসাধক ছানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, ‘নফসে আম্মারা হলো মন্দ কাজের আদেশ দেয়া। এরপর ব্যক্তি যখন জিকির-আজকারে যত্নবান হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আকর্ষণ তাঁকে টেনে নেয়, তখন তার কাছে (পূর্বেকৃত) মন্দত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে দেখতে পায় যে, সে আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছুর মধ্যে ডুবে রয়েছে। অথচ তা থেকে সে মুক্ত হতে পারছে না। এ সময় সে নিজেকে তিরস্কার করে এবং তখন তার নাম হয় নফসে লাওয়ামা’।[15] নফসে মুতমাইন্না- কোরানে উল্লেখিত নফসের তৃতীয় স্তর। এ হলো সেই স্তর যাকে হেগেল বলেছেন ‘এবসল্যুট রিজন’, হুর্সাল বলেছেন ‘পিওর কনসাসনেস’, হাইডেগার বলেছেন ‘এবসল্যুট বিং’ এবং হোসাইন নসর বলেছেন ‘পিওর এবসলিউট বিং’। এই স্তরে মানুষ ‘পূর্নাংগ সত্ত্বা’ প্রাপ্ত হয়। রুমি’র ভাষ্যে এ হলো সেই সর্বোচ্চ স্তর যেখানে মানুষের ‘ইন্ডিভিজুয়ালিটি’ বিলীন হয়ে যায়, মানুষ খোঁদার মহান একত্বে হারিয়ে যায় কেননা ‘তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ দেবে না! হে প্রাশান্ত আত্মা’![16] ইমাম গাজালির মতে, নফস যখন শান্ত হয় তখন তাঁর পূর্বাবস্থা দূরীভূত হয়। কাম, মোহ ইত্যাদি ভাবনাগুলো চলে যায় এ অবস্থাকে মুতমাইন্না বলা হয়। এ সম্পর্কে মুতাকিল বলেন, এ হলো এমন নফস, যা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ। পানিপথীর মতে নফস যখন “ফানা” (আধ্যত্মিক বিলুপ্তি) ও “বাঁকা” (সত্ত্বার স্থিতি) অর্জিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর জিকিরে শান্তি পায় তখন তাঁকে নফসে মুতমাইন্না বলা হয়[17]।
উপরে উল্লেখিত নফসে আম্মারা শব্দটির ধাতুমূল ‘আমর’, যার অর্থ নির্দেশ করা। নফসে লাওয়ামা শব্দটির ধাতুমূল ‘লাওম’, যার অর্থ নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা। নফসে মুতমাইন্না শব্দটির ধাতুমূল ‘ইতমিইনান’, যার অর্থ শান্ত বা স্থির। আরবি ব্যাকরণানুযায়ী ‘আমর’, ‘লাওম’ এবং ‘ইতমিইনান’ তিনটি শব্দই নারী সত্ত্বাজাত। ফলে এই আলাপ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নারী সত্ত্বাজাত জায়গা থেকেই আদম ভোগবাদী হয়ে ওঠে, কাম-রিপুর তাড়নাপ্রাপ্ত হয় যাকে আম্মারা বলে। ঐ একই জায়গা থেকেই সেই মানুষই আবার নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করে তথা তওবা করে যাকে লাওয়ামা বলে। শেষমেশ মানুষ পূর্নতাপ্রাপ্ত হতে অর্থাৎ তুষ্টপ্রাপ্ত হতে নারী সত্ত্বাজাত ‘প্রাশান্ত আত্মা’য় প্রবেশ করে যাকে নফসে মুতমাইন্না বলে। মানুষের এই লম্বা যাত্রা প্রকৃত সত্ত্বা তথা ‘ধাত’র দিকে চালিত করার যাত্রা।
প্রকৃত সত্ত্বা তথা ‘ধাত’ শব্দটিও ‘ধু’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গিক শব্দ যার অর্থ সেই সত্ত্বা যা ধারণ করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ তায়ালা হলেন প্রকৃত সত্ত্বা তথা ‘ধাত’। ব্যাকরণিক দিক থেকে এটি অবশ্যই নারীসত্ত্বা জাত। কিন্তু ইবনে উসাইমিন থেকে শুরু করে ইবনে তাইমিয়াদের মতো অধিকাংশ স্কলারগণ এই ভাবনাকে পুরোপুরি মানতে আগ্রহী নন। তারা বলতে চান ‘ধাত’ নারী সত্ত্বাজাত, এর মানে এই নয় যে খোঁদার লিঙ্গিক প্রকাশ আছে। আসলে ‘ধাত’ শব্দ দিয়ে খোঁদার লিঙ্গিক ভাবনাকে প্রকাশ করে না বরং খোঁদার মধ্যেই সবকিছু নিমজ্জিত তথা খোঁদা সবকিছুকে ধারণ করেন এই অর্থে তিনি ‘ধাত’। কোন কিছু ধারণ করা- এই ক্রিয়াটি নারীবাচক। ‘মেলার মধ্যে ইদ্রিস মিয়া তার সন্তানকে ধরে রেখেছে’- এ বাক্য দিয়ে এটা বোঝায় না যে, ইদ্রিস নারী। বরং এটা দিয়ে বোঝায় যে, ঐ ব্যক্তি ‘ধরে রাখতে’ সক্ষম। এখানে ‘ধরে রাখা’ ব্যাপারটা নারীসত্ত্বাগত বিষয়। ইবনুল আরাবী বলেন-
‘যদি তুমি বলতে চাও [সে সৃষ্টিকর্তার মূলসত্ত্বা (dhat) থেকে নয়, বরং] কোনো খোদায়ী গুণ (ṣifa) থেকে এসেছে, তাহলে ‘গুণ’ শব্দটিও আরবি ভাষায় স্ত্রীবাচক। যদি তুমি বলো সে খোদায়ী শক্তি (qudra) থেকে এসেছে, তাহলে ‘শক্তি’ শব্দটিও স্ত্রীবাচক। প্রকৃতপক্ষে, তুমি যেই অবস্থানই গ্রহণ করো না কেন, দেখবে নারীত্ব বা স্ত্রীবাচকতা সবসময় অগ্রাধিকার পায়—এমনকি তাদের ক্ষেত্রেও [কালামবিদ] যারা বলেন আল্লাহই এই জগতের কারণ, স্মরণে রাখবে যে, ‘কারণ’ (ʿilla) শব্দটিও আরবি ভাষায় স্ত্রীবাচক’।[18]
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবের মতো মানুষও আল্লাহর করুণার নারীত্বপূর্ণ উপাদানে সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকে। আবার আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়—মানুষ নারীত্বের দুটি মেরুর মাঝখানে অবস্থান করছে। সকল মানুষের জন্য, বিশেষ করে সুফি সাধকদের জন্য, জীবন হলো এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। যে সংগ্রামে একদিকে নফসের তিনটি স্তর, যা নারীত্বের এসেন্স থেকে নিজেকে মুক্ত করা, জয় করা এবং আলাদা করার সফর; অন্যদিকে আল্লাহর ‘ধাত’ বা পরম সত্তার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, যার দ্বারা সাধকেরা জ্ঞানের সন্ধান ও ঐক্যের সাধনা করেন। সুফি গবেষক মারিয়া দাক্কাকীর ভাষ্যে: ‘নফস’ যাকে আত্মিক উপলব্ধির পথে জয় করতে হয় এবং ‘ধাত’- যার দিকে মানুষকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়—আরবি ভাষায় দুটি শব্দই স্ত্রীবাচক এবং স্ত্রীবাচক সর্বনাম দ্বারা নির্দেশিত। এই দুটি “নারীত্বপূর্ণ মেরু” মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রার এমন প্রতীক, যা সুফি কবিতা ও মরমী ব্যাখ্যায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[19]
সত্তাগত ও সিম্বোলিকভাবে নারীত্ব শুধু আধ্যাত্মিকতার নির্দেশক নয় বরং সুফি দর্শনের গভীরতম স্তরের একটি মৌলিক ‘অন্টোলজিক্যাল’ বাস্তবতা। ‘ধাত’ ও ‘নফস’—এই দুটি স্তম্ভের নারীবাচকতা যেমন মানুষের আত্মিক যাত্রার দুইটি মেরু নির্দেশ করে তেমনি নারীসত্ত্বাজাতের দার্শনিক প্রভাবকেও চিহ্নিত করে। তবে সত্ত্বাগতভাবে নারীত্ব এখানে কেবল একটি ব্যাকরণিক বা প্রতীকী বিষয় হিসেবে থেমে থাকেনি বরং তা সুফি ঐতিহ্যের গঠন ও বিকাশে ধীরে-ধীরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, সুফি নারীরা শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় অংশগ্রহণ করেননি বরং সুফি পরিভাষা, অনুশীলন এবং আচার-অনুষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণার জন্ম দিয়েছেন। যেমন— ইশক বা পরম প্রেমের ধারণা কিংবা যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতার চর্চা—এসবই সুফি নারীদের জীবন ও সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়ে সুফি ঐতিহ্যে প্রবেশ করেছে। তারা নিজেদের শরীর, সংসার এবং সামাজিক পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে এমন এক ভাষা ও অনুশীলনের জন্ম দিয়েছেন, যা পরবর্তীতে সুফি ধারার মূল অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ভূমিকা কেবল অনুসারী ও অনুশীলনকারী ভাবনায় আটকে থাকেনি বরং সুফি ঐতিহ্যের উৎপাদক, পরিভাষার নির্মাতা এবং আধ্যাত্মিক পথের পথপ্রদর্শক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।
ঐতিহাসিক পর্যায়: নারীর অংশগ্রহণ ও আচরিক ফর্মেশন
সুফি ঐতিহ্যে নারীর ভূমিকা শুধু মেটাফিজিক্যাল স্তরে সীমাবদ্ধ নয় বরং আচার-অনুষ্ঠান, সাধনা এবং আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতিটি স্তরে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের রাবিয়া আল-আদাবিয়া, ফাতিমা নিশাপুরি, উম্মে হারুন থেকে শুরু করে প্রি-কলোনিয়াল জমানার আইশা আল বাউনিয়া, জাহানারা বেগম, নানা আসমাউ কিংবা বিংশ শতকের কেমালনূর সারগুতসহ অন্যান্য নারী সুফিরা ধ্যান, জিকর, সেমা (সঙ্গীত) এবং রুহানিয়াত চর্চার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অংশ নিয়ে, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে সুফি সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা অনেক সময় নিজস্ব খানকাহ পরিচালনা করেছেন, শিষ্যদের শিক্ষাদান করেছেন এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। রিচুয়াল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ শুধু ব্যক্তিগত সাধনায় সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা ছিল একধরনের সামাজিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা। সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে যেমন- চিশতিয়া, কাদরিয়া ও নকশবন্দিয়া—তাদের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ও ভূমিকা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু অঞ্চলে নারী সুফিরা পুরুষদের মতোই আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়েছেন, আবার কোথাও তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সুফি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।
সুফি নারীদের এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞের তত্ত্বতালাশ গবেষকদের বিশ্লেষণে ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। এই বিশ্লেষণগুলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—সুফি ঐতিহ্যে ‘ইশক’ তথা প্রেমের ধারণা, হাল ও মাকাম তথা আধ্যাত্মিক যাত্রার স্তর সম্পর্কিত ধারণা এবং যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখতার চর্চা। সেইসাথে পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রিক পরিসরে নারী সুফিদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়গুলোও বিশ্লেষণগুলোর চর্চিত অংশ। উল্লেখিত তিনটি ধারণা তথা ইশক, স্তর ও যুহদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রাথমিক সুফি ঐতিহ্যে সুসংগঠিত রূপে উপস্থিত ছিল না; অর্থাৎ এগুলো কোনো নির্দিষ্ট ‘ফর্ম’, ‘স্ট্রাকচার’ বা ধারাবাহিক অনুশীলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে এই ধারণাগুলো সুফি চিন্তার কেন্দ্রে স্থান দখল করে নেয় এবং সুফি ধারার কোনো শাখাই এই তিনটি বিষয়কে উপেক্ষা করে পরিচালিত হয়নি। বরং এগুলো হয়ে ওঠে সুফি সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, আত্মশুদ্ধি এবং পরম প্রেমের সন্ধান সম্ভবপর হয়। এই প্রবন্ধে শুধু সুফি ঐতিহ্যে ‘ইশক’ তথা প্রেম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।
সুফি ঐতিহ্যে ইশকের ধারণা
মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল রাজ্জাক আবু ফাইয়াদ হোসাইনী ইয়ামানী হানাফি (১১৪৫ খ্রি-১২০৫ খ্রি) একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিক। শিক্ষা নিয়েছেন ইয়েমেনে জোবাইদির কাছে, তার লিখিত কিতাব ইত্তেহাফ আল-সাদাত আল-মোত্তাকীন থেকে আব্দুর রাজ্জাক উল্লেখ করেন-
রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘তুমি আল্লাহর নবীকে কতটা ভালোবাসো?’ তিনি বলেছিলেন, ‘নিঃসন্দেহে খুবই ভালোবাসি’, তবে তিনি এটাও বলেছিলেন যে, ‘কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার প্রেম (মোহাব্বাহ) এত গভীর যে, তাঁর সৃষ্টির প্রতি মহব্বতের জায়গা আর থাকে না’।[20]
মোহাব্বাহ বা মোহাব্বত শব্দটি ইসলামী ঐতিহ্যে ব্যবহৃত একটি পরিচিত শব্দ। সুফিধারায় শব্দটিকে ‘ইশক’ হিসেবে ব্যাবহারের প্রচলন রয়েছে। শব্দটির অনুবাদ হিসেবে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ‘প্রেম’ শব্দটি প্রতিষ্ঠা পেলেও এই শব্দটির আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ও গভীরতা ‘প্রেম’ শব্দের সীমা অতিক্রম করে। ঠিক কবে থেকে এবং কাদের মাধ্যমে সুফি ঐতিহ্যে ‘ইশক’ শব্দটি প্রতিষ্ঠা পেলো তা বুঝতে শুরুতেই ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটির উৎপত্তি, ব্যাবহারের ধরণ এবং সময়কালকে বোঝাপড়া করা দরকার। তবে একথা সত্য যে, এই ধারণাটি সুফি ঐতিহ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার পেছনে নারীদের, বিশেষ করে সিরিয়া ও বসরার নারী সুফিদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শব্দটি কুরআনে সরাসরি একবারই সূরা ত্বা-হা’র ৩৯ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ‘আর আমি তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা (মোহাব্বাহ) সঞ্চার করে দিয়েছিলাম এবং যাতে তুমি আমার যত্নে গড়ে উঠতে পারো’। আয়াতটিতে ব্যবহৃত ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি এমন এক আয়াতে এসেছে যেখানে একজন মুমিনাকে অর্থাৎ নারীকে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে বলা হয়েছে—যা আত্মসংযম বা যুহদের একটি মৌলিক দিক। এখানে আল্লাহ মূসা (আ.)-এর মাকে আদেশ দেন, যেন তিনি তাঁর শিশুকে একটি ঝাঁপিতে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেন, যাতে ফারাও সৈন্যদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যায়। এই আয়াতে ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই নারীকে তার সন্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে অধিকতর আশ্বস্ত করেছেন। মুসার জননী আসিয়ার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটিকে গবেষকগণ ‘সিগনিফিক্যান্ট’ হিসেবে দেখেছেন।[21]
কুরআনে উল্লেখিত আরেকজন নারী রয়েছেন যিনি নিজেকে আল্লাহর হাতে সপে দেন, তিনি হলেন ঈসা (আ.)-এর মা মরিয়ম। কুরআনে বলা হয়েছে, “তিনি খোঁদার বাণী ও কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ছিলেন অনুগতদের একজন” (৬৬:১২)। প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে মরিয়ম যখন একটি খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর জন্য পাকা খেজুর ও প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করে দেন (১৯:২৩–২৬)। যদিও মরিয়ম সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি, তবুও আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য ও আস্থা সেই একই ভাবনার প্রতিফলন, যা মূসার (আ.) মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কুরআনে মরিয়মকে ‘অনুগতদের একজন’ বলা হয়েছে, যা আল্লাহর প্রতি নিবেদন ও আত্মসমর্পণের পরিচায়ক। খোঁদার প্রতি এই গভীর আস্থা ও আত্মনিবেদনই তাকে তাঁর জীবনকে পুরোপুরি সৃষ্টিকর্তার হাতে সপে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। সুফি ঐতিহ্যের সুইডিশ গবেষক টর আন্দ্রেয় এই আত্মসমর্পণকে বলেছেন— ‘গভীর একনিষ্ঠতার সমষ্টি’।[22] প্রাচীন কিছু সুফি মরিয়মের এই পথ অনুসরণ করতেন, যাকে বলা হয় ‘তাওয়াক্কুল’ অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা। তারা জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতেন, কারণ মরিয়মের মতো তারাও বিশ্বাস করতেন—আল্লাহই তাঁদের সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। যেমন- ইরাকি সুফি ইবরাহীম আল-খাওয়াস (মৃ- ৯০৪ খ্রিস্টাব্দ), তিনি মনে করতেন-
‘একজন সুফি কখনোই কোনো জিনিস বা সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারেন না। এমন কোন জিনিস তার কাছে থাকা উচিৎ না, যা প্রয়োজনের সময় তিনি ব্যবহার করতে পারেন বা অন্য কাউকে দিয়ে কিছু বিনিময় মূল্য পেতে পারেন। ক্ষুধার্ত হলে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য চোখ বা মুখ ব্যবহার করাও সুফি রীতির মধ্যে পড়ে না। আর বিপদের সময় মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য কোনো কথা বলাও সুফি আদর্শের পরিপন্থী’।[23]
প্রায় একই রকম তাওয়াক্কুল চর্চার নমুনা দেখা যায় আবু সুলাইমান আদ দারানি (মৃ-৮৩০ খ্রি), শাকিক আল বালখি (মৃ-৮ম শতক), আবু ইয়াজিদ আল বিস্তামী (মৃ- ৮৭৪ খ্রি), রাবেয়া বসরি (মৃ- ৮০১ খ্রি) সহ আরো অনেক সুফিদের মধ্যে।
খোঁদার মোহাব্বাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো বিশ্বাসীর প্রেম ও আল্লাহর প্রেমের মধ্যে পারস্পরিকতা বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে। যেমন বলা হয়েছে— “বলো: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে [নবী মুহাম্মদ (দ.) এর] অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।” [24] আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে— “শিগগিরই আল্লাহ এমন এক জাতিকে আনবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।” [25] এই পারস্পরিক প্রেমের ধারণা শুধু কুরআনেই নয়, হাদীসেও এ সম্পর্কিত বয়ান উপস্থিত রয়েছে। এই হাদিসগুলো পাঠে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লাহর প্রেম ও বান্দার প্রেম একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আল্লাহর প্রতি প্রেম নিয়ে হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি পরবর্তীতে সুফি ঐতিহ্যে প্রেম বিষয়ক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দে পরিণত হয়। কিন্তু শব্দটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাধারণ প্রেম বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। যেমন, ইবন হাম্বলের ‘মুসনাদ’-র একটি হাদীসে নবীজী ব্যাখ্যা করেন—কুরআনের “গর্ভের বন্ধন” (সিলাতুর রাহিম, সূরা নিসা ৪:১) বলতে বোঝানো হয়েছে “পরিবারের প্রতি ভালোবাসা” (মোহাব্বাতান ফি-আহল)। এখানে ‘মোহাব্বা’ শব্দটি ‘হুব্ব’-এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আরবি ভাষায় প্রেম বোঝাতে সবচেয়ে প্রচলিত শব্দ। এই হাদীসে নবীজী ‘হুব্বান ফি-আহল’ এবং ‘মোহাব্বাতান ফি-আহল’—এই দুটি শব্দগুচ্ছকে একই অর্থে ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি, যা প্রমাণ করে ‘মোহাব্বা’ শব্দটি তখনও সাধারণ প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হতো।[26]
প্রাচীন মুসলিমরা ‘মোহাব্বাহ’ ও ‘হুব্ব’ শব্দ দুটি পরস্পর বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করতেন। এই ধারণার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রাবেয়া বসরির সমসাময়িক সুফি ইব্রাহিম ইবনে আদহামের একটি উক্তিতে। তিনি বলেন: “আল্লাহর প্রেম (হুব্বুল্লাহ) ও অর্থ বা সম্মানের প্রেম (মোহাব্বাতুল মাল ও আশ-শরাফ) একসঙ্গে খুঁজো না।”[27] এই বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রচলিত ধারণার বিপরীত। সুফিরা সাধারণত ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি আল্লাহর প্রতি প্রেম বোঝাতে ব্যবহার করেন এবং ‘হুব্ব’ শব্দটি দুনিয়াবি জিনিসের প্রতি প্রেম বোঝাতে ব্যবহার করেন। কিন্তু ইব্রাহিম ইবনে আদহামের সময় এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যে কারনে তিনি এই উক্তিতে ‘মোহাব্বাহ’ ব্যবহার করেছেন দুনিয়াবি প্রেম বোঝাতে, আর ‘হুব্ব’ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর প্রেম বোঝাতে। এই ধরনের উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, রাবেয়ার সময়কালে ‘হুব্ব’ ও ‘মোহাব্বাহ’ শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
তবে একথা সত্য যে, খোঁদার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম তথা ‘মোহাব্বাহ’কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন নারী সুফিরা যার উদাহরণ পাওয়া যায় ইবনে আল জুনায়েদের কিতাব আল মুহাব্বাহ গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে রাবেয়ার সমসাময়িক অন্যান্য সুফিদের খোদায়ী প্রেম সংক্রান্ত বয়ান সংকলিত আছে। সেখানে উল্লেখিত আমির ইবনে আল কায়েস (মৃ. ৬৮০) বলেন, “খোদার কসম! খোদা যার প্রতি মোহব্বত করে না, আমিও তার প্রতি মোহাব্বত করি না।” তিনি আরও বলেন, “আমি খোদাকে ভালোবাসি, তিনি মহান ও পরাক্রমশালী। আমি তাঁকে ভালোবাসি কারণ তিনি আমার সমস্যাকে দূর করে দিবেন। আমার প্রতিটি চাওয়াকে তিনি পূরণ করে দিবেন।” এই বয়ান বিশ্লেষণ করে সুয়াদ আলী আব্দুল রাজিক বলেন, কায়েস ছিলেন ইসলামে প্রথম ‘খোদার প্রেমিক’ (মুহিব)।[28]
একটি আগ্রহউদ্দীপক বিষয় হলো, কায়েস গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও খোদা প্রেমের চর্চা দেখা যায়। শায়খ আব্দুর রহমান সুলামির (মৃ-১০২১ খ্রি) রচনায় আফিয়া নামের এক নারী সুফির উল্লেখ আছে, যিনি এই গোত্রেরই সদস্য। তিনি শিষ্যদেরকে মুহাব্বা, মুসতাকা (মোহগ্রস্ত) এবং সউখ (আসক্ত) হওয়ার পরামর্শ দিতেন। আফিয়া বলেন, “একজন প্রেমিক (মুহিব) কখনোই প্রেয়সীর সাথে অন্তরঙ্গ (মুনাজাত) আলাপে ক্লান্ত হয় না। প্রেয়সীই তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রেয়সীকে ছাড়া অন্য কিছু পেতেও সে আগ্রহী হয় না। ওহ! আমি যদি সবসমই তাঁকে কামনা করতে পারতাম”![29]
ইবনে আল কায়েস, আফিয়া এবং রাবেয়া বসরি—তিনজনই প্রাচীন কায়েস গোত্রের সদস্য। এই উদাহরণগুলো ঐতিহ্যগতভাবে খোদার প্রতি প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে কায়েস গোত্রের সংশ্লিষ্টতার বিষয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে আমির ইবনে আল কায়েস ও আফিয়ার ‘মোহাব্বাহ’ সম্পর্কিত ভাবনায় পার্থক্য রয়েছে। আমির বলেন, “আমি তাঁকে ভালোবাসি কারণ তিনি আমার সমস্যাকে দূর করে দিবেন।” এই ‘মোহাব্বাহ’ যেন দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যেখানে প্রেমের বিনিময়ে প্রতিদান প্রত্যাশা করা হয়। গবেষক রিকা এলারুই কর্নেল এধরনের সাধনার ধারাকে বলেছেন ‘যন্ত্রসম সাধনা’ (Instrumental Asceticism) এবং উপযোগবাদী।[30] অন্যদিকে, আফিয়ার ‘মোহাব্বাহ’ সংক্রান্ত বয়ানে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই। সেখানে রয়েছে একনিষ্ঠ, আত্মবিসর্জনমূলক প্রেম—যা সুফি ঐতিহ্যে প্রেমের প্রকৃত রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার ভাবনায় শুধু ঐশী প্রিয়তম ছাড়া আর কাউকেই সে চায় না। মোহাব্বাহ’র এই ধরনটি রাবেয়ার প্রতি আরোপিত আত্মসংযমী মোহাব্বাহ’র স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। মোহাব্বাহ বিষয়ে রাবেয়া মনে করতেন- “প্রেম তথা মোহাব্বাহ চিরআদি (আজাল) থেকে উদ্ভূত এবং অনন্তকাল (আবাদ) প্রবাহিত। আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে কাউকে ‘মোহাব্বা’র শরবতের এক ফোঁটা পান করার যোগ্য মনে হয়নি। শেষ পর্যন্ত যখন মহব্বত সত্যের কাছে পৌঁছাল, তখন শুধু এই বাণীই রয়ে গেল- “তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে”’।[31]
রাবেয়া যে বিশেষ কারণে খ্যাতি অর্জন করেন, তা হলো তিনি আল্লাহর প্রেমিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর টেক্সট পাঠ করলে দু’ধরনের খোদা প্রেমিকের সন্ধান মেলে। যেমন: সেই প্রেমিক, যে জান্নাতের আশায় অথবা জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহকে ভালোবাসে এবং অন্যদিকে সেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক, যার চিন্তা শুধু ঐশী প্রিয়তম। রাবেয়ার কাছে ‘হুব্ব’ বা ‘মোহাব্বাহ’র অর্থ হলো—আল্লাহর প্রতি এমন একাগ্রতা, যেখানে অন্য সবকিছু যেমন- জান্নাত-জাহান্নামসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধার হিসাব বাদ পড়ে যায়। তার এই ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায় সুফিয়ান সাওরি’র প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে। সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করেন, “তোমার ঈমানের প্রকৃত রূপ কী?” রাবেয়া উত্তর দেন: “আমি ভয় থেকে তাঁর ইবাদত করিনি, যেন জাহান্নাম থেকে বাঁচি; জান্নাতের লোভেও ইবাদত করিনি, যেন কোনো মজুরের মতো প্রতিদান পাই। আমি তাঁর ইবাদত করেছি শুধুই তাঁর প্রেমে ও তাঁর প্রতি আকুলতায়।” রাবেয়া উল্লেখিত ‘দুই ধরনের প্রেম’, যার একটির সাথে স্বার্থ যুক্ত, অপরটি নিঃস্বার্থ— সুফি ঐতিহ্যের প্রেম সংক্রান্ত ভাবনা ও পর্যায়গুলো বোঝার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক সূচনাবিন্দু হিসেবে বিবেচিত।[32] রাবেয়া বলেন: ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি দুই রকম ভালোবাসায়— একটি স্বার্থমিশ্রিত। আরেকটি হলো সেই ভালোবাসা, তুমি প্রকৃতপক্ষে যার যোগ্য। যে ভালোবাসায় স্বার্থ জড়িত, তা হলো—তোমার স্মরণ, আর কিছু নয়। কিন্তু যে ভালোবাসা তোমার প্রাপ্য, আহ্! তখন তুমি আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছ, আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি। এই দুই ভালোবাসার কোনোটির জন্যই আমার কোনো গৌরব নেই, বরং গৌরব তো কেবল তোমার—এই প্রেমে, সেই প্রেমেও’।[33]
যদিও তিনি মোহাব্বাহ’র বিশ্লেষণে এই মৌলিক পার্থক্যের বাইরে বিস্তারিত আলাপে প্রবেশ করেননি। অর্থাৎ তার পরবর্তী সময়ে সুফি ঐতিহ্যে প্রেম বা মোহাব্বাহ বিশাল এক মহীরুহ হয়ে উঠবে, এ বিষয়ক নানা দার্শনিক ও মেটাফিজিক্যাল বয়ান উৎপাদন হবে, সেদিক নিয়ে তিনি কোন আলাপ দেননি। তবুও আন্দালুসীয় মহান সুফি ইবন আরাবি রাবেয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—
“তিনি এমন একজন, যিনি প্রেমের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস বিশ্লেষণ করেছেন এতটাই গভীরভাবে যে, তাঁকে প্রেমের সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।”[34] রাবেয়ার এই অবদানকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দুর্দান্তভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জার্মান গবেষক এনিমেরি শিমেলের মতে, সুফি ঐতিহ্যে প্রেম তথা মোহাব্বাহকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার অবদান রাবেয়া বসরির।[35]
যদিও রাবেয়া প্রথম ব্যক্তি নন যিনি ‘মোহাব্বাহ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবে তিনি খোদার দিদার লাভে প্রেমের গুরুত্বকে সুফি চিন্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গবেষক মার্গারেট স্মিথ বলেন, ‘সুফিদের মধ্যে রাবেয়া প্রথম নন, যিনি প্রেমকে খোদা প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রথম সুফি যিনি খোদা প্রাপ্তিতে মোহাব্বাহ তথা প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন’।[36] তাঁকে নিয়ে ফরিদউদ্দিন আত্তারের বর্ণনা অপরাপর সকল বর্ণনাকে অতিক্রম করে যায়। আত্তার মনে করতেন, ‘রাবেয়া হলো প্রেম এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষার নূরে জ্বলতে থাকা একজন নারী… আল্লাহ’র প্রতি তার আবেগ তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিলো’।
তবে একথা সত্য যে, রাবেয়া পরবর্তী সুফি ঐতিহ্যে প্রেম বিষয়ক ভাবনায় ‘ইশক’ শব্দটি তীব্র প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মোহাব্বাহ ও ইশকের আক্ষরিকতা ও নান্দনিকতা পুরোপুরি একইরকম নয়। শব্দটি আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। ‘ইশক’ শব্দের অর্থ হলো—আকাঙ্ক্ষা বা গভীর কামনা। সুফিরা পরবর্তীতে এই শব্দটিকে ‘মোহাব্বাহ’র সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ‘মোহাব্বা’র মতো ‘ইশক’ শব্দটি কোনো প্রধান হাদীস সংগ্রহে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু এর ক্রিয়াপদ ‘আশিকা’ শব্দটি ইবন হাম্বলের মুসনাদ-এ একটি মাত্র হাদীসে এসেছে। হাদিসটিতে ব্যাবহৃত ‘আশিকা’ শব্দটি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন একজন পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ। লুইস ম্যাসিগনন দাবি করেন, ইসলামে আল্লাহর প্রতি প্রেম বোঝাতে ‘ইশক’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রাবেয়ার সমসাময়িক আব্দুল ওয়াহিদ ইবন জায়িদ (মৃ. ৭৯৩)। ম্যাসিগননের মতে, ইবন জায়িদ ‘মোহাব্বা’ শব্দটি ব্যবহার করতে চাননি, কারণ তিনি মনে করতেন—এই শব্দটি খোঁদার আনুগত্যের প্রতি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে।[37] লুইস ম্যাসিগননের এই ভাবনাকে হাল জমানার সুফি চিন্তক কার্ল আর্নস্টও সঠিক বলে মনে করেন।
তবে এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ করেন মিশরীয় গবেষক আব্দুর রহমান বাদাউই। তিনি দেখান, ম্যাসিগনন এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। বাদাউইর মতে, ‘ইশক’ শব্দটি সুফি পরিভাষায় প্রবেশ করে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ রাবেয়ার পরবর্তী প্রজন্মে। এই সময়েই ইবন হাম্বালের মুসনাদ-এ ‘আশিকা’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ফলে, ‘ইশক’ শব্দের ব্যবহার সম্ভবত সুফি ঐতিহ্যে প্রেম সংক্রান্ত দর্শনের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশকে নির্দেশ করে। সার্বিকভাবে, হাদীস এবং ইসলামের প্রাচীন সুফি রচনাগুলোর টেক্সটগুলো বাদাউই’র এই মতকে সমর্থন করে যে, আল্লাহর প্রতি প্রেম বোঝাতে ‘ইশক’ শব্দের ব্যবহার ছিল পরবর্তী সময়ের একটি বিকাশ। এর ফলে বোঝা যায়, রাবেয়া বা অন্যান্য প্রাচীন সুফি ও সংযমীদের যেসব বক্তব্যে ‘ইশক’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা আসল নয়। এই দাবিকে আরও জোরালো করতে বলা যায়—আরবি ভাষায় ‘ইশক’ ও ‘মোহাব্বাহ’ শব্দের মৌলিক অর্থ এক নয়। ‘ইশক’ বলতে বোঝায় আকাঙ্ক্ষা বা কামনামিশ্রিত প্রেম এবং ‘মোহাব্বাহ’ ও ‘হুব্ব’ বোঝায় স্নেহভাজন, কোমল প্রেম। তাই ম্যাসিগননের মতের বিপরীতে বলা যায়, রাবেয়ার সময়কালে আল্লাহর প্রতি প্রেম প্রকাশের জন্য ‘মোহাব্বা’-ই ছিল অধিকতর উপযুক্ত শব্দ, কারণ তা সংযমী জীবনধারার সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রাথমিক মুসলিম সুফিদের মধ্যে খোদাভক্তি ও খোদাভীতি ছিল প্রধান। তারা নামাজ, রোজা, জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমিক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাও তাদের মধ্যে জন্ম নেয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রারম্ভিক যুগে সুফিদের প্রেম সংক্রান্ত অধিকাংশ শিক্ষাই কবিতা ও সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এসকল টেক্সটগুলোতে মানুষের প্রেম আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ এবং সেখানে সুস্পষ্টভাবে একজন মানবপ্রেমিক ও একজন ঐশী প্রেয়সীর মধ্যে দ্বৈততা বিরাজমান। কিন্তু ষষ্ঠ/বারো শতকের শুরুতে প্রেমের আলোচনা নতুন মাত্রা পায়, এ সময়ে প্রেমকে দ্বৈততার ঊর্ধ্বে তথা অদ্বৈত্ব ভাবনায় সরাসরি খোদায়ী সত্ত্বা (Divine Essence) হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়।[38] এ সময়কালে সুফি ঐতিহ্যে চর্চিত প্রেমকে ‘ইশক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ‘ইশক’ শব্দটি এ সময়ের আগে কখনোই সুফি ঐতিহ্যে কেন্দ্রীয় কোন বিষয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মনসুর হাল্লাজ, ফরিদুদ্দিন আত্তার, জালালুদ্দিন রূমির বদৌলতে ধীরে-ধীরে ‘ইশক’ শব্দটি সুফি ঐতিহ্যে ‘সেন্ট্রাল থিমে’ পরিণত হয়। এই ভাবনা পারস্য সুফি সাহিত্যকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, তা আজ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ফলে দেখা যায়, বহু তুর্কি ও ইরানি সুফি আত্তারের সেই বিখ্যাত উক্তি বারবার উচ্চারণ করেন— “লা ইলাহা ইল্লা ইশক” — “কোনো ইলাহ নেই, শুধু ইশক-ই ইলাহ”।[39]
তবে ইশকে’র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার এই যাত্রায় আহাম্মদ আল গাজালী (মৃ-১১২৬ খ্রি) একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর মাধ্যমেই সুফি ঐতিহ্যে প্রেম একটি মেটাফিজিক্যাল স্তরে প্রবেশ করে। তাঁর রচিত অসাধারণ গ্রন্থ সোয়ানিহ হলো প্রথম কোন সুফি গ্রন্থ যেখানে প্রেমের পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি (মেটাফিজিক্স) তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালি’র (মৃ. ১১১১ খ্রি) ছোট ভাই। আবু হামিদ আল-গাজালি যেখানে ফিকহ (ইসলামি আইন), কালাম (আকীদা ও ধর্মতত্ত্ব) ইত্যাদি শাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রেখে ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত হন, সেখানে আহমদ আল-গাজালি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সুফি পথের সাধনায় নিবেদিত করেন। তাঁর সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে হৃদয়ের পরিশুদ্ধি। পারস্য ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি ৫০৮ হিজরি / ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়। সোয়ানিহ-এ তিনি সমগ্র বাস্তবতাকে প্রেমের (ইশক) এক ধারাবাহিক বিকাশ হিসেবে তুলে ধরেন, যেখানে প্রেমিক (আশিকি) ও প্রেমিকত্ব (মাশুকি)—এই দুটি ধারণা প্রেম থেকেই উদ্ভূত এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমের সেই চিরন্তন উৎসে ফিরে যায়। সৃষ্টির অবতরণ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উত্থানের প্রতিটি ধাপকে তিনি প্রেমের ধাপ হিসেবে দেখেছেন। মূলত সোয়ানিহ’র মাধ্যমে আহমদ আল-গাজালি সুফি চিন্তায় এক বিপ্লবী পরিবর্তন আনেন— ইশকের ধারণাকে মেটাফিজিক্সের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেন।[40]
আহমদ গাজালি যে ইশকের কথা বলেছেন, তা সাধারণ মানবীয় প্রবণতার ঊর্ধ্বের ভাবনা। এটি এক ঐশী প্রেম, যা আল্লাহর একটি গুণ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সত্ত্বার সঙ্গে অভিন্ন। এখানে প্রেমিক (আশিক) ও প্রিয়তম (মাশুক)—এই দুই চরিত্র আবশ্যিকভাবে মানুষ মাত্র নয়। প্রেম (ইশক), প্রেমিক (আশিক) ও প্রিয়তম (মাশুক)—এই তিনটি ধারণাকে গাজালী এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা শর্তহীন। অর্থাৎ, প্রেম (ইশক) হতে পারে— সত্ত্বা নিজেই ঈশ্বরীয় গুণ অথবা মানবিক অনুভূতি। এবং প্রেমিক (আশিক) বা প্রিয়তম (মাশুক) হতে পারেন— স্রষ্টা অথবা সৃষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইশক ধারণাকে সুফি ঐতিহ্যে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে, যেখানে প্রেম শুধু অনুভূতি নয়, বরং সৃষ্টির মূল ও চূড়ান্ত বাস্তবতা।[41] আহমদ গাজালি ইশক, আশিক ও মাশুককে দেখেছেন একক এক সত্ত্বা হিসেবে, তার মতে এ হলো প্রকৃত সত্য-
ইশকের মূল উৎপত্তি প্রাক-অস্তিত্ব থেকে। ‘ইউহিব্বুহুম’ (অর্থ: আল্লাহ—তাদের ভালোবাসেন) শব্দের আরবি ‘বা’ অক্ষরের নিচের বিন্দুটি বা নোকতাটি যেন একটি বীজ হয়ে ‘ইউহিব্বুনাহু’ (অর্থ: তারা তাঁকে ভালোবাসে) শব্দের মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নাকি ‘বা’ অক্ষরের সেই বিন্দুটি ‘হুম’ (তাদের) শব্দের উপর ছিটানো হয়েছিল, আর সেখান থেকেই ‘ইউহিব্বুনাহু’ (তারা তাঁকে ভালোবাসে) অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। যখন প্রেমের নার্গিস ফুল প্রস্ফুটিত হলো, তখন দেখা গেল—বীজের প্রকৃতি যেমন, ফলের প্রকৃতিও তেমন। আর ফলের প্রকৃতি যেমন, বীজের প্রকৃতিও তেমন।[42]
আহমদ আল-গাজালি তাঁর সুফি দর্শনে প্রেম (ইশক), প্রেমিক (আশিক) ও প্রিয়তম (মাশুক)-কে একটি ঐশী ত্রয়ী রূপে তুলে ধরেছেন, যেখানে প্রেম শুধু মানবিক অনুভূতি নয় বরং আল্লাহর সত্ত্বার সঙ্গে অভিন্ন এক গুণ। তিনি প্রেমকে সৃষ্টির মূল শক্তি হিসেবে দেখেছেন, যার উৎপত্তি অনন্ত পূর্বঅস্তিত্ব থেকে—যেমন ‘ইউহিব্বুহুম’ শব্দের ‘বা’ অক্ষরের বিন্দু যেন বীজ হয়ে ‘ইউহিব্বুনাহু’-র মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়, আর সেখান থেকে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। এই প্রেমিক ও প্রিয়তম—মানুষ বা আল্লাহ—উভয়ই হতে পারেন, কারণ প্রেমের প্রকৃতি শর্তহীন ও সর্বব্যাপী। গাজালি দেখান, প্রেমিকের প্রেমের শুরুতে প্রিয়তমের মাধ্যমে সে নিজেকেই ভালোবাসে, যা আত্মকেন্দ্রিকতা; কিন্তু প্রকৃত প্রেমে সে নিজের সত্তাকে হারিয়ে দেয় প্রিয়তমের অনন্ত সত্ত্বায়। তিনি রূপক ভাষায় বোঝান যে, প্রেমের বীজ ও ফলের প্রকৃতি একই—যা দ্বারা প্রেমিক, প্রেম ও প্রিয়তম মূলত এক অভিন্ন ঐশী বাস্তবতার তিনটি রূপকে নির্দেশ করে।
মোহাব্বাহ কিংবা ইশক সম্পর্কিত বিষয়াশয় নিয়ে অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ, সুফি তাত্ত্বিকেরা বয়ান-প্রতিবয়ান উৎপাদন করেছেন যুগে-যুগে। যে কারনে সুফি ঐতিহ্যে মোহাব্বাহ বা ইশক একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরিক ও দার্শনিক স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো ‘ধর্মের’ মতো পর্যায়ে চলে গেছে, যেমন রুমি বলেছেন, আমি প্রেম ধর্মের অনুসারী। সুফিধারা বিকাশের সময়কাল, বিশেষ করে ষষ্ঠ হিজরি/দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোহাব্বাহ (খোঁদাপ্রেম) নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। ইসলামের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ করে যারা যুক্তিবাদি, তারা খোঁদা-মানুষ প্রেম সম্পর্ককে অযৌক্তিক বলে মনে করেছেন যেমন আল্লামা–জামাখশারি (মৃ-১১১৪ খ্রি)। তিনি মুতাজিলি ঘরানার একজন আলেম। মুতাজিলি ঐতিহ্য সর্বদা যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝতে সচেষ্ট থাকেন, ফলে সুফি ঐতিহ্যে প্রচলিত খোদাপ্রেম ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই চিন্তকের মতে, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক “অনুচিত এবং গভীরভাবে অযৌক্তিক”। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রিক দর্শনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যেতে পারে। এরিস্টটল তার নিকোমাখিয়ান এথিকস গ্রন্থে বলেন, শারীরিক দূরত্ব বন্ধুত্বের অস্তিত্বে বাধা সৃষ্টি করে, আর বন্ধুত্ব প্রেমের পূর্বশর্ত। তিনি আরো বলেন: “যখন একজন অন্যজন থেকে অত্যন্ত দূরে চলে যায়—যেমন আল্লাহ মানুষের থেকে দূরে—তখন বন্ধুত্ব আর টিকে থাকতে পারে না”।[43]
আবার ফর্মেশন যুগের সুফিদের মধ্যেও অনেকেই ‘ইশক’ শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন না, যেমন- হেরাতের শায়খ খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী (মৃ. ১০৮৯ খ্রি.)। আনসারি যখনই প্রেমের কথা বলতেন তখনই আরবি ‘মোহাব্বাহ’ অথবা ফারসী ‘দোস্তি’ ও ‘মেহর’ শব্দগুলো ব্যাবহার করতেন। তিনি ‘ইশক’ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ ‘আশিক’ বা ‘মাশুক’ শব্দও ব্যবহার করেননি। তাঁর রচিত মানাজিল কিংবা সাদ মায়দান– কোথাও তিনি ইশক শব্দের ব্যাবহার করেননি। তবে তার যে-সকল মুনাজাত কাশফুল আসরার-এ উল্লেখ আছে সেখানে তিনবার ইশক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আনসারির এই সতর্কতা সম্ভবত হাম্বলি মাজহাবের আপত্তির কারণে ঘটেছে। এই মাজহাবপন্থীরা আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম বোঝাতে ‘ইশক’ শব্দের ব্যবহারকে অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। অথবা পঞ্চম হিজরি/একাদশ শতকে ‘ইশক’ শব্দের ব্যবহার সম্ভবত বিতর্কিত ছিল।[44] শব্দটি সুফি সাহিত্যে ষষ্ঠ হিজরি/দ্বাদশ শতকের শুরুতে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে, যখন প্রেমের তত্ত্ব আরও উন্মুক্তভাবে প্রচারিত হতে থাকে। গাজালি ভ্রাতৃদ্বয় এই শব্দটিকে সুফি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। আবু হামিদ আল–গাজালি তার এহিয়াউ-উলুমুদ্দীন গ্রন্থে আল্লাহর প্রতি প্রেম বোঝাতে ‘ইশক’ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং আহমদ গাজালি তার সোয়ানিহ-এ ‘মোহাব্বাহ’ ও ‘ইশক’ শব্দদ্বয়কে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি ‘ইশক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেম বোঝাতে। রশিদ উদ্দিন মায়বুদী ছিলেন পূর্বে উল্লেখিত সুফি আনসারির শিষ্য এবং তিনিই মূলত আনসারির চিন্তাকে কিতাববন্দী করেছেন ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে ‘ইশক’ শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে গেছে এবং সুফিসাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যে কারণে, আনসারি এই শব্দটি ব্যাবহার না করলেও তার ছাত্র রশিদ উদ্দিন মায়বুদি শব্দটি ব্যবহার করতে সামান্যতম দ্বিধা করেননি। তার দৃষ্টিতে ইশক শুধু সৃষ্টিজগত ও মানবসৃষ্টির ব্যাখ্যার কেন্দ্রবিন্দু নয় বরং আদমের পতন, ঐশী অঙ্গীকার (আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সুরা আরাফ, ১৭২) এবং নবীজীর মিরাজ—সবকিছুর ব্যাখ্যায় প্রেমই মূল ভিত্তি। এমনকি মানুষের আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের পথও তাঁর মতে প্রেমের মধ্য দিয়েই সম্ভব।[45]
উপসংহার: সুফি ঐতিহ্যে নারীত্বকে শুধু একটি জৈবিক বা সামাজিক পরিচয় হিসেবে নয় বরং একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। ইবনুল আরাবি, রুমি, হেনরি করবিনসহ বহু সুফি চিন্তাবিদ নারীত্বকে সৃষ্টির রহস্য, আল্লাহর রহমত ও করুণার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোরআনের ভাষাগত বিশ্লেষণে যেমন ‘নাফসে ওয়াহিদা’ শব্দটি স্ত্রীবাচক, তেমনি ‘রহমান’ ও ‘রহিম’ শব্দের ধাতু ‘রেহেম’—যার অর্থ গর্ভাশয়—নারীত্বের আধ্যাত্মিক উৎসকে নির্দেশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীত্বকে সৃষ্টির ধারক, বাহক এবং রহস্যময় উৎস হিসেবে তুলে ধরে। সুফি চিন্তায় নারী হয়ে ওঠে সেই আয়না, যার ভেতরে সৃষ্টিকর্তা নিজের সত্তাকে প্রতিফলিত করেন। রুমির ভাষায়, ‘নারী সৃষ্ট নয় বরং সৃষ্টিশীল’—এই বক্তব্য নারীত্বকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং অস্তিত্বের গভীরতম স্তরের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রতীক নারীত্বকে আল্লাহর সত্ত্বার কোমলতা, রহমত ও গোপনীয়তার ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে, যা সুফি দর্শনের মেটাফিজিক্যাল স্তরে নারীর অবস্থানকে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদানে পরিণত করেছে।
অন্যদিকে, সুফি ঐতিহ্যে মোহাব্বাহ বা ইশকের ধারণায় নারীর অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক ও অনালোচিত থেকেছে, যদিও তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অবদান ছিল গভীর ও বহুমাত্রিক। প্রাচীন সুফি টেক্সটগুলোতে নারীদের উপস্থিতি সীমিত, অনেক সময় নামহীন বা পুরুষ সুফিদের স্ত্রী, মা বা বোন হিসেবে উল্লেখিত। তবে আল-সুলামি, ইবন আল-জাওজি এবং আল-তিরমিজির মতো কিছু জীবনীকার নারীদের আধ্যাত্মিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। আধুনিক গবেষকরা যেমন লাউরি সিলভার, রিকা ইলারুই কর্নেল, এনিমেরি শিমেল ও সাদিয়া শেখ এই প্রান্তিক নারীদের আখ্যান পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা দেখিয়েছেন, নারী সুফিরা কেবল অনুসারী ছিলেন না বরং সুফি দর্শনের নির্মাতা, ধারক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রবর্তক ছিলেন। মোহাব্বাহ বা ইশকের ধারণায় নারীরা প্রেমের সেই অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেছেন, যা আত্ম-অতিক্রম, আত্ম-পরিশুদ্ধি এবং সত্ত্বার সঙ্গে মিলনের পথ দেখিয়েছে। এই প্রেম শুধু মানবিক আকর্ষণ নয় বরং এক ঐশী আকাঙ্ক্ষা, যেখানে নারীর হৃদয় হয়ে ওঠে আল্লাহর প্রেমের আবাসস্থল। ফলে সুফি ঐতিহ্যে নারীর অবস্থান কেবল ঐতিহাসিক নয় বরং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক স্তরেও গভীরভাবে প্রোথিত, যা আমাদেরকে নারীত্বের নতুন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের পথে আহ্বান জানায়।