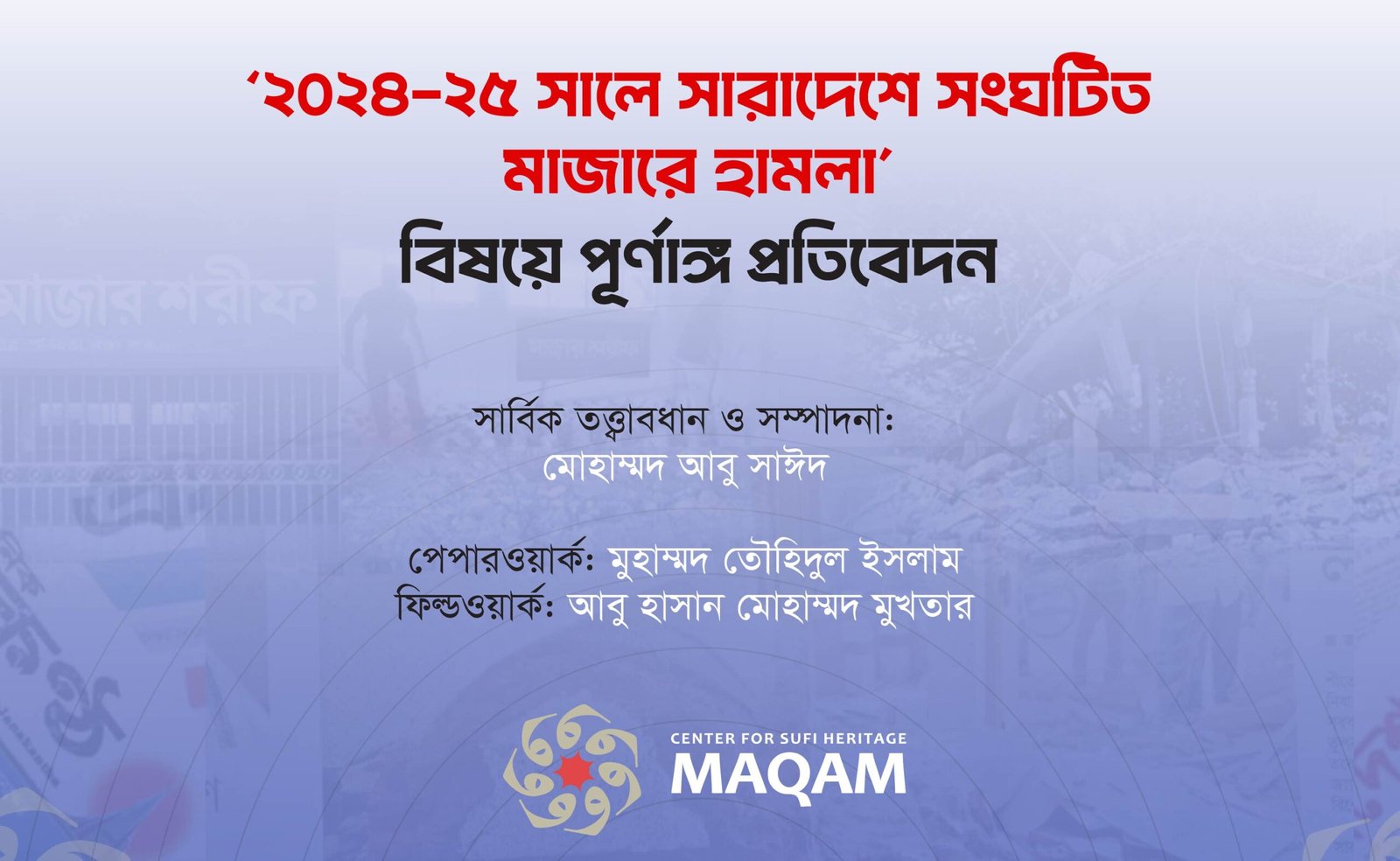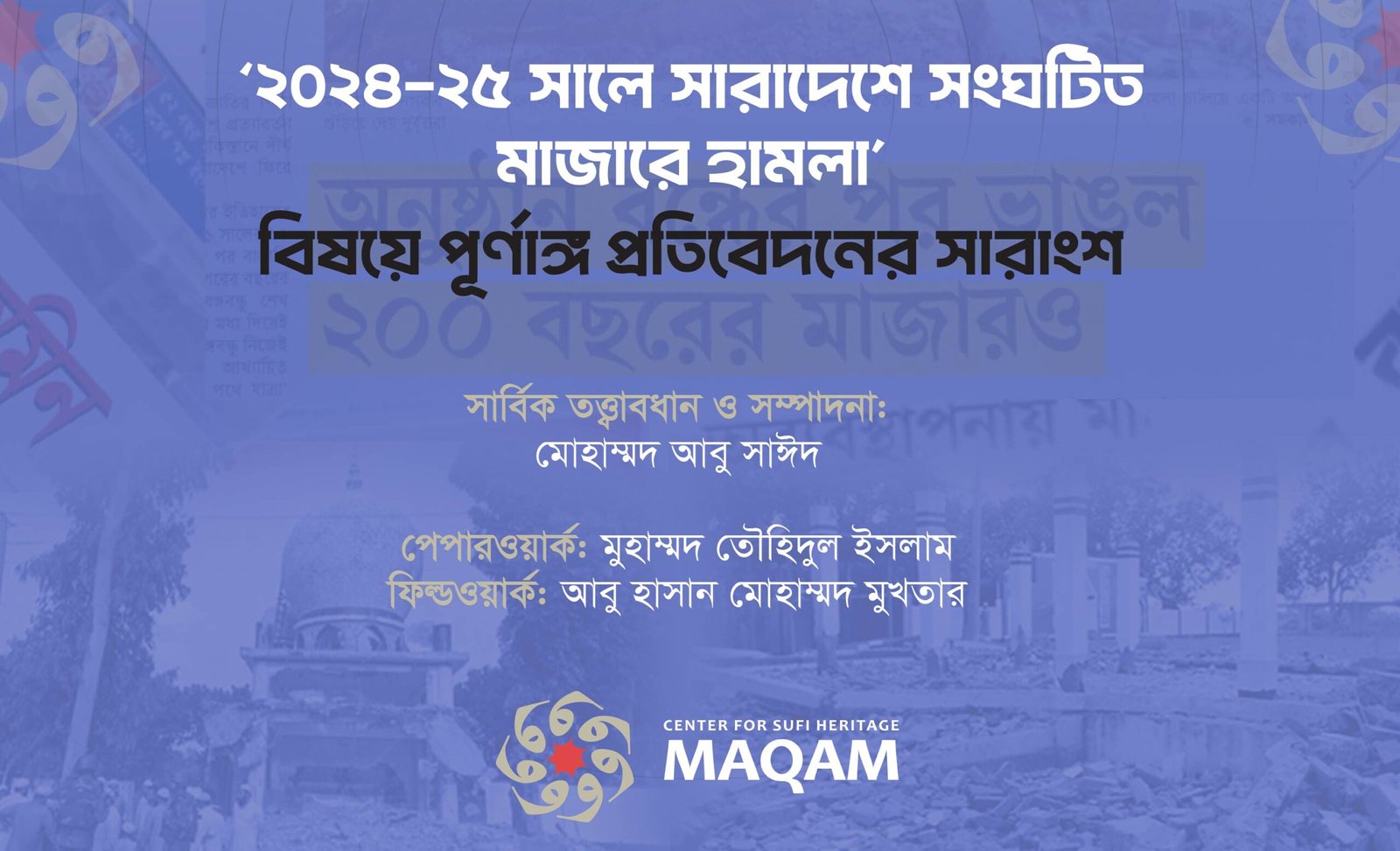১২০৪ সালের বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ অভিযানের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটলেও, বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ঘটে ভিন্ন ধারায়। অসংখ্য সুফি সাধকের সাধনা, আন্তরিক উপস্থিতি ও মানবিক কার্যকলাপের মাধ্যমেই ইসলাম বাংলার জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কৃষিভিত্তিক ‘ফ্রন্টিয়ার’ অঞ্চলে জাতপাত, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিপরীতে সুফিদের সরল জীবনচর্চা জন্ম দেয় এক নতুন সমাজচিন্তার। এই প্রেক্ষাপটে হযরত শাহ মাখদুম রূপোশের আগমন স্রেফ একজন ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব নয়, বরং বরেন্দ্র ভূমির –বর্তমান রাজশাহী, রংপুর ও পশ্চিমবঙ্গের মালদাহ বিভাগ– আর্থ-সামাজিক সংকট ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বাস্তবতায় তিনি এসেছিলেন ত্রাণকর্তারূপে।
শাহ মখদুম রূপোশের জীবন ও কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট তথ্য ইতিহাসে সংরক্ষিত নেই, কিন্তু লোকস্মৃতি ও দরগা সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা যেটুকু পাই, তা থেকেই তথ্যগুলো পেশ করছি। শাহ মখদুম রূপোশ ১২১৬ (হিজরী ৬১৫ সালের ২রা রজব) সালে বাগদাদের এক বিখ্যাত সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- প্রখ্যাত সুফি সৈয়দ আজাল্লা শাহ (রহঃ), যিনি শায়খূল মাশায়েখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর সাতাশ পুত্রের একজন। বাদশাহ হালাকু খাঁর বাগদাদ লুণ্ঠন ও শহর উৎসন্নের শিকার হয়ে তৎকালীন ফিরোজ শাহের জমানায় হিন্দুস্তানে আসেন। পরবর্তীতে তার পুত্ররা ধর্ম প্রচারে হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়লেও হালাকু খাঁর মৃত্যুর পর সৈয়দ আজাল্লা শাহ বাগদাদে ফিরে যান। (আমিন : ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩) শাহ মখদুম রূপোশ এর বংশ পরিচয় নিয়ে ড. মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী তার “রাজশাহীতে ইসলাম” গ্রন্থে গবেষক আবু তালিবের বরাতে বলেন, “উপাখ্যান ও সাম্প্রতিককালে তার জীবনী সম্পর্কে মূল ফারসী হতে বাংলা ভাষায় অনুদিত একটি গ্রন্থের সূত্রে বলা যায়, শাহ মখদুম বাগদাদের শায়খুল মাশায়েখ হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ)-এর একজন বংশধর ছিলেন।” (আলী : ১৯৯২, ৩৬)
সাল ১২৫৮, তাতার সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রা যখন আব্বাসীয় খেলাফতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, ফলত একটি রাজধানী ও রাজত্বের পতনের পাশাপাশি বিলুপ্ত ঘটায় জ্ঞান-আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমিরও। এই ভূ-রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই শাহ মখদুম রূপোশের পরিবারিক নির্বাসন। বাগদাদ থেকে তাঁদের পরিবার প্রথমে সিন্ধু ও পরবর্তীতে দিল্লিতে বসতি গাড়েন। (ইসলাম : ২০০৮, ৫১)
এভাবে অতিক্রম হয় আরো ২০ বছর, শাহ মখদুম রূপোশের বয়স তখন ষাটে, ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দ। এরই মধ্যে, দিল্লির মামলুক সুলতানদের সাথে সৈয়দ আজাল্লা শাহ পরিবারের দারুন সখ্যতা গড়ে ওঠে। সৈয়দ আজাল্লা শাহ তার তিন পুত্রকে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব ভারত (বর্তমান বাংলাদেশ) গমনের আদেশ দিয়ে তিনি বাগদাদে ফিরে যান। সেকালে তৎকালীন বাংলার শাসক ছিলেন- তুর্কি শাসকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান মুঘিসউদ্দিন তুঘরিল খান (১২৬৮- ১২৮১ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি পূর্ব বাংলার মসনদ জয় করতে সক্ষম হন এবং এই অঞ্চলকে স্বাধীন ঘোষণা করে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বলবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সুফি নেতৃত্বের অনুমোদনে পিতা আজাল্লা শাহের নির্দেশে তুঘরিল খান বিরোধী অভিযানে শাহ মখদুম রূপোশ ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে শতাধিক অনুসারীসহ পূর্ব ভারত (বর্তমান বাংলা) অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে গৌড়ে অবস্থান করে পরে দক্ষিণ বাংলার নোয়াখালী অঞ্চলে খানকা স্থাপন করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, নোয়াখালীর শ্যামপুর গ্রামে তিনি প্রথম আস্তানা গড়েন, সেখান থেকেই ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি কাঞ্চনপুর এসে একটি খানকা স্থাপন করেন। (পূর্বোক্ত, ৫৩)
বর্তমান রাজশাহী অঞ্চল- যার প্রাচীন নাম মহাকালগড়, মধ্যযুগে তা ‘রামপুর বোয়ালিয়া’ নামে পরিচিতি পায়। তৎকালীন মহাকালগড় ছিলো তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পীঠস্থান। রাজা জানকি রায়ের অধীনস্থ তান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী দুই সামন্ত জমিদার দ্বারা অঞ্চলটি শাসিত হতো, যারা দেওরাজ নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। দুই দেওরাজদ্বয় কর্তৃক তাদের আরাধ্য দেও বা দৈত্যের বিশালকার কৃষ্ণবর্ণের মূর্তি (মহাকালী মূর্তি) এই গড়ে স্থাপন করেছিলো। এই মহাকালীর গড় থেকে মহাকালগড় নামের উৎপত্তি। প্রতিবছর মহা আড়ম্বরের সময় মহাকাল দেও মূর্তিকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে একাধিক নরবলি দেওয়া হতো। গড়ের নিম্নবিত্ত কোনো পরিবার থেকে জোরপূর্বক শিশু এনে নিষ্ঠুরভাবে বলি দেওয়া হতো। তান্ত্রিকদের আচরণ এতো বেশি ভয়ংকর ও কুৎসিত ছিল যে, বলি দেওয়া মানুষের বা মৃত মানুষের দেহের উপর বসে লাশের মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষ একত্রে সুরাপান করতো। অনেকটা বনবাসী হিংস্র কাপালিক সম্প্রদায়ের মতোই। এই পরিস্থিতিতে গৌড় অঞ্চলের কিছু মুসলমানদের বলিদানের উদ্দেশ্যে মহাকাল দেও মন্দিরে নিয়ে আসলে, তাদের উদ্ধারের লক্ষ্যে হযরত তুরকান শাহ (রহঃ) কিছু অনুসারীদের নিয়ে মহাকালগড়ে আসেন। তার আগমনের পাশাপাশি এ জনপদে পদার্পন ঘটলো প্রথম ইসলাম প্রচারকের। কিন্তু গড়ের তান্ত্রিক রাজার আদেশেই তুরকান শাহ (রহঃ)কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, সময় তখন ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দ। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ ও প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যই শিষ্য ও সঙ্গীসাথী-সহ হযরত শাহ মখদুম রূপোশ নোয়াখালী হয়ে রাজশাহীর বাঘা নামক স্থানে আগমন করেন, পরবর্তীতে যার নামকরণ হয় মখদুমনগর। (তালিব : ১৯৬৯, ৫৪)
দীর্ঘ সময় ধরে সামন্তরাজ কাপলিক তন্ত্রে বিশ্বাসী দুই দেওরাজ- আংশুদেও খেজ্জুর চান্দভন্ডীও বর্মভোজ ও আংশুদেও খেজ্জুর চান্দখড়্গ গুজ্জভোজের চরম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা লালন করতো, তারা শাহ মখদুম রূপোশের আগমনী বার্তা পেয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেন। এবং প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শাহ মখদুম রূপোশের অধীনে এক বৃহৎ সম্মিলিত বাহিনী জালেম দেওরাজদ্বয়ের পতন নিশ্চিত করতে মরিয়া হয়ে উঠে। ফলস্বরূপ, পরপর তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে রামপুর বোয়ালিয়ার জনসাধারণ পায় ধর্মীয় জীবনযাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা, নিশ্চিত হয় বিজয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রচার প্রসারের অবারিত সুযোগ তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে এবনে গোলাম সামাদ বলেন – “শাহ মখদুম অবশ্য কেবল মোরাকাবা করেই সময় কাটাননি। রাজশাহীর লোক কথায় বলে, তিনি নরবলি প্রদান বন্ধের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক সুফি দরবেশ প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছেন এদেশে। এঁরা যুদ্ধ করেছেন নরবলি প্রদানকারী তান্ত্রিক সাধুদের বিরুদ্ধে। এদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল অনেক পরিচ্ছন্ন ও মানবিক।” (সামাদ : ১৯৯৯, ১২৭) কয়েক বছর ধরে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধের মাধ্যমে সামন্তদের পরাজয় হলে পরবর্তীতে দুই সামন্ত জমিদারসহ বেশ কয়েকটি হিন্দু নাপিত ও বহু কৈবর্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।
মহাকালগড়ে নরবলি প্রথার বিপরীতে ইসলামের মানবিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজগঠন নিশ্চিত হওয়ার পর শেষ জীবন পর্যন্ত বেশ চুপচাপ সময় কাটিয়েছেন এবং বেশিরভাগ সময় কুরআন পাঠ, মোরাকাবার মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তার ইন্তিকালের সময় নির্ধারণে ২৭ রজব তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষণ করলেও, ইন্তেকালের বছর নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, ইতিহাসবিদ আবু তালিবের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেন, “অধ্যাপক আবু তালিব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তার আগমনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন, এবং ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর বছর নির্দেশ করেছেন।” তাঁকে বর্তমান রাজশাহী শহরের দরগাপাড়ায় তার নির্দেশিত স্থানে দাফন করা হয় এবং তার সমাধির উপর ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মির্জা আলী কুলি বেগ কর্তৃক একটি গম্বুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। তিনি একজন অবিবাহিত ছিলেন। এখনো প্রতি চন্দ্র বছরের ২৭ রজব তারিখে তাঁর দরগায় ‘উসর’ বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। তাঁর দরগাকে ঘিরে গড়ে উঠা সংস্কৃতিগুলো নিয়ে মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন,
“People of all walks of life not only believe that Shah Makhdum is the guardian saint of Rajshahi (old Rampur-Boaliya), but also an invisible power still existing to exert an influence on those. who came to Rājshāhi, the land of Makhdum Shah, to earn their liveihood. They never went back from Rajshaht disappointed and many of them often settled here permanently.” (Haque: 1975, 227)
শাহ মখদুম রূপোশ এর জীবন ও কর্মপ্রণালী ইতিহাসধারায় ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে মুক্ত। তিনি কখনো কোনো শাসকের দ্বারস্থ হননি বরং স্বতন্ত্রভাবে সমাজের ভিতরেই নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। স্বতন্ত্র অবস্থান নির্মাণ করেছেন তন্ত্র-নিপীড়িত জনপদে, নিপীড়িত জনতার হৃদয়ে। তাঁর সেই ইতিহাস রাষ্ট্রের নথিতে যতটা নেই, তারচেয়ে ঢের বেশি আছে মাটির ভিতরে, জনস্মৃতিতে, আর লোকজ বিশ্বাসে। এখানেই রূপোশের প্রকৃত বিজয়: তিনি ইসলামকে সামরিক বিজয়ের পতাকা বানিয়ে মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি, বরং মানুষকে তাদের আভ্যন্তরীণ অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাইতো আজও জনতার ভীড়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় গভীর আস্থার সঙ্গে— রাজশাহীর বাতাসে, দরগাপাড়ার ধূপে, আর মজলুমের নিস্তব্ধ আর্তনাদে।