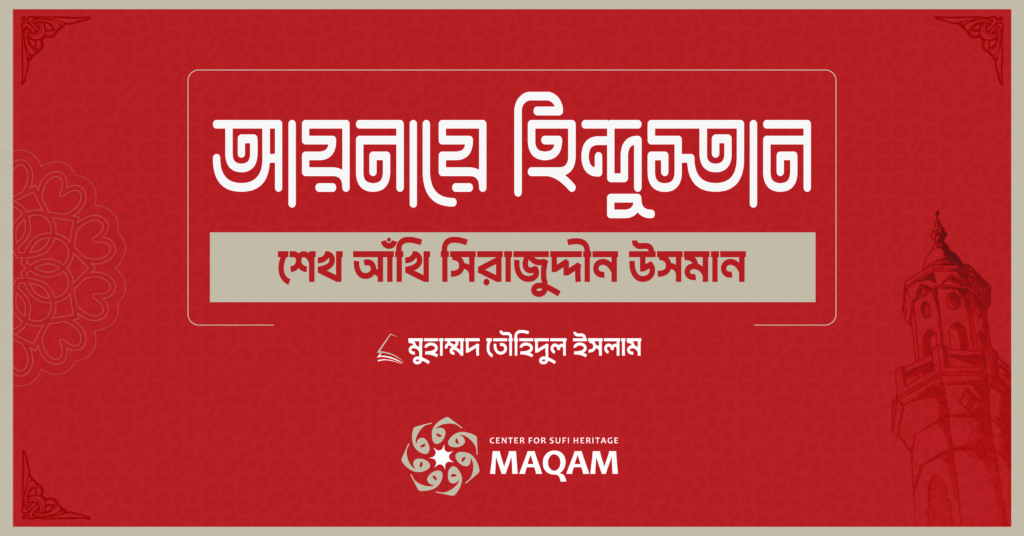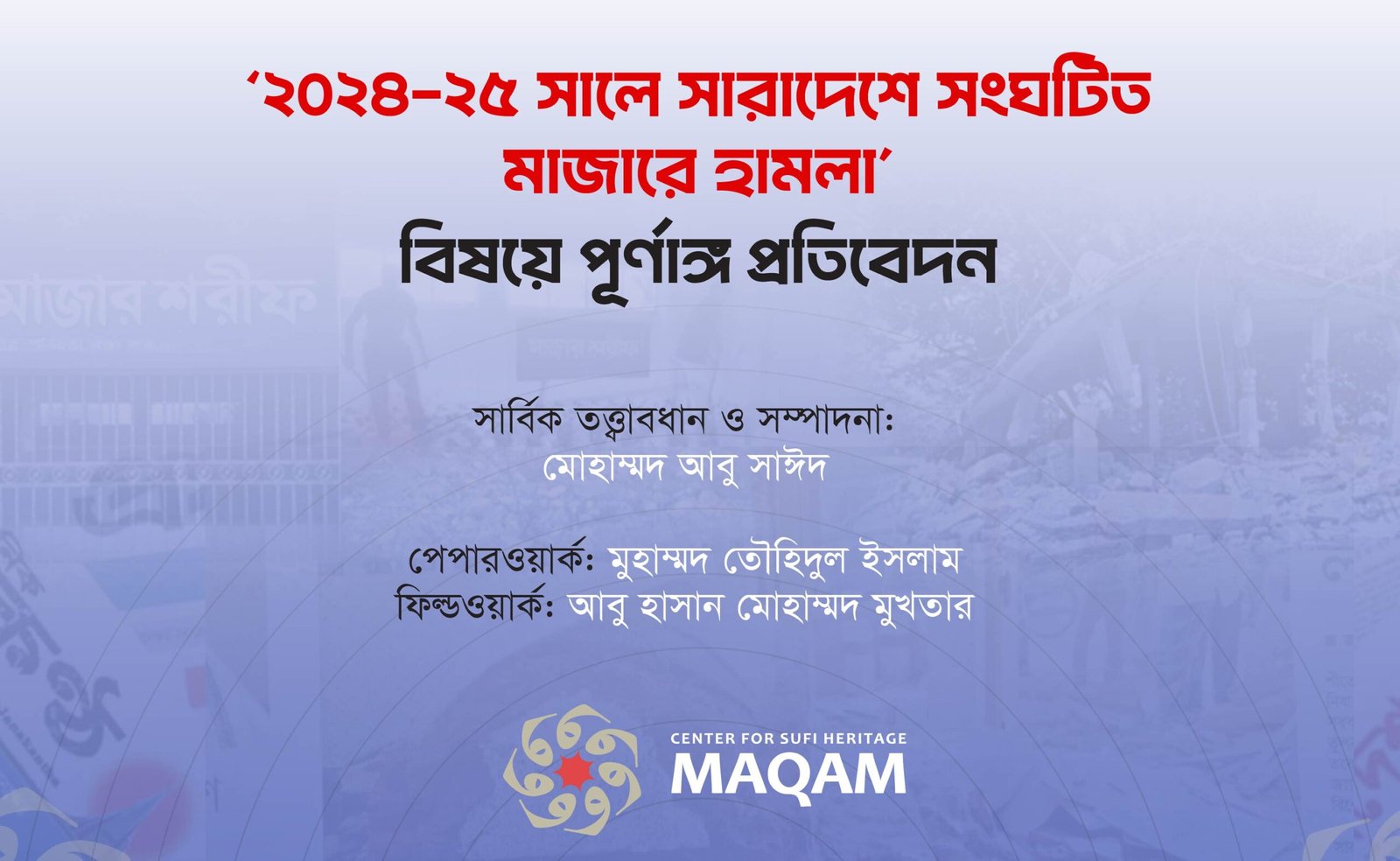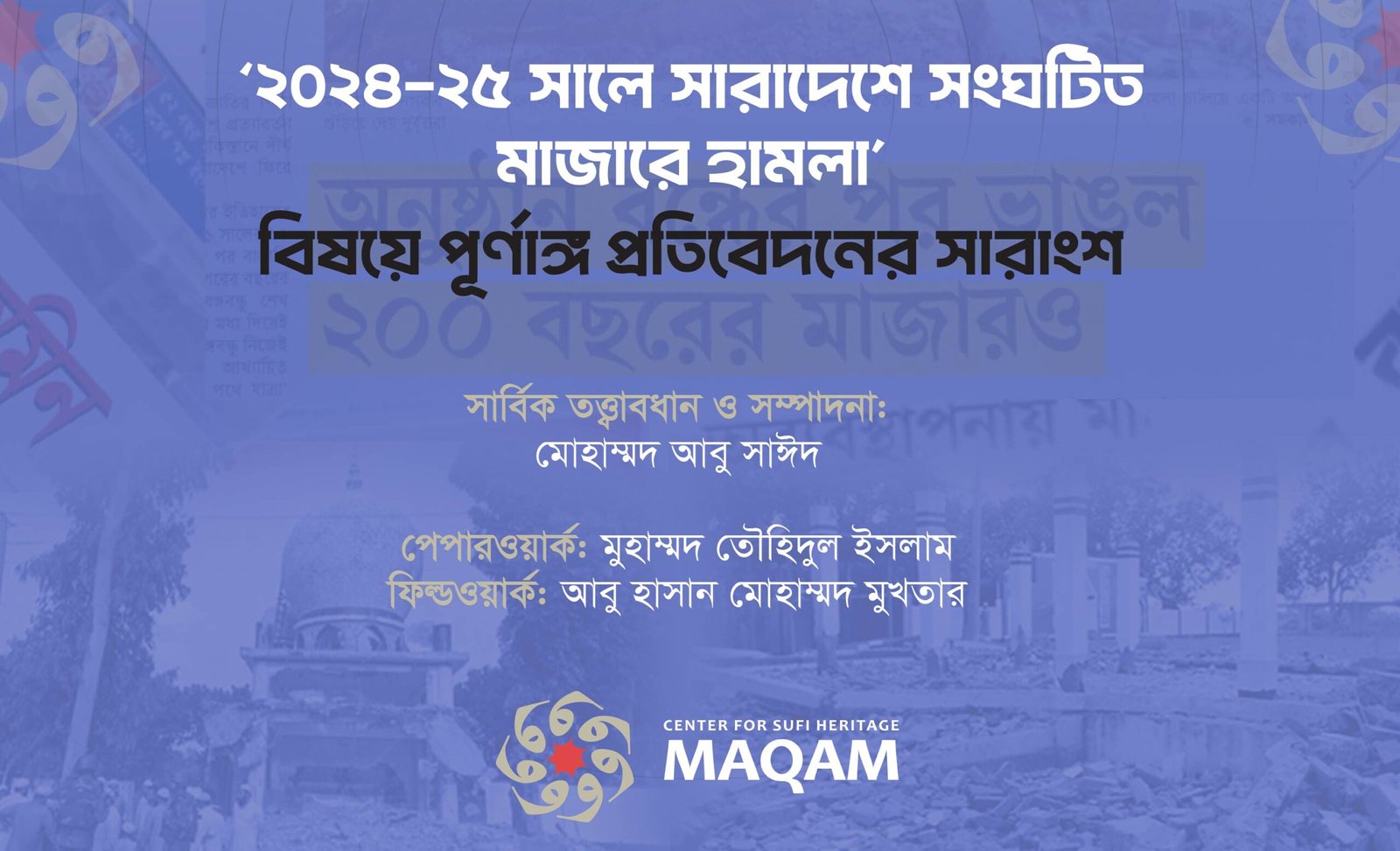যিনি দিল্লির আধ্যাত্মিক শিকড় থেকে এসে বাংলার জনমানসে আল্লাহর একত্ববাদ, মানবতা ও সংযমের শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলে রাখা জরুরী যে, বাংলার জনমানসে ভক্তিবাদ ছড়িয়ে পড়ার এটিই একমাত্র মাধ্যম নয়। অন্যপথটি ছিল নদিয়ার গৌড়ীয় বাঙাল পল্লিতে— যেখানে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৪) আবির্ভূত হয়েছিলেন হিন্দুধর্মের নবজাগরণকে নেতৃত্ব দিতে। এই দুই পথ — তাওহিদের ও ভক্তির— ছিল মূলত দুটি ভিন্ন জগৎদর্শনের বাহক: একপথ মানুষকে আহ্বান করে এক আল্লাহর দিকে আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাধ্যমে। অপরপথ ডাকে প্রেম, রস, রীতি ও আবেগে ভগবানের অনন্ত সান্নিধ্যে বিলীন হওয়ার জন্য। যদিও ইতিহাসে তাদের মধ্যে ছিল- দেড়শত বছরের সময়ের ব্যবধান। তবুও আজ—ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিতে তাদের দর্শনের প্রভাব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। আঁখি সিরাজুদ্দিনের শিক্ষা ও প্রভাবকে চৈতন্য ভক্তিবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে বলে মত দিয়েছেন অনেকেই। (আশরাফী: ২০১৮, ২৪৬-২৫০)
তবে এই বিতর্কের আবর্তে জড়িয়ে পড়াই আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের লক্ষ্য সেই মহাপুরুষকে বুঝে নেওয়া— যাঁর নামকে এক পক্ষ বানাতে চায় চৈতন্য ভাবধারার পূর্বসূরি, অন্যপক্ষ তুলে ধরে ইসলামি আধ্যাত্মিকতার নির্ভেজাল এক আলোকবর্তিকা হিসেবে। এই দুই বিপরীত বয়ানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শায়খ আঁখি সিরাজকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে তাঁর নিজস্ব ইতিহাস, আভ্যন্তরীণ সাধনা ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার অনুসারে। এখানে স্মরণ করা জরুরি যে, বাংলার সুফি ইতিহাসে চিশতিয়া তরীকাই ছিল সবচেয়ে সুসংগঠিত ও প্রভাব-বিস্তারকারী। বাঙালি সূফিদের অধিকাংশই এই তরিকার সাধক ছিলেন, যারা বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই ধারারই প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় আবির্ভূত হন শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমান— দিল্লির আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে যাঁর আগমনের মাধ্যমে বাংলায় চিশতিয়া তরিকার সূচনা হয়েছে।
শায়খ আঁখি সিরাজের প্রকৃত নাম- উসমান। ডাকনাম ছিল সিরাজুদ্দীন। উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়- সিরাজুদ্দীন উসমান। সৈয়দ নিজামুদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত, আঁখি (আমার ভাই) এবং আয়নায়ে হিন্দুস্তান (ভারতবর্ষের দর্পণ) হলো তার উপাধি। এভাবে তাঁর নাম দাঁড়ায়, আয়নায়ে হিন্দ আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমান। যদিও ইতিহাস ও সাহিত্যে “আঁখি সিরাজ” নামেই তিনি অধিক সুপরিচিত। তাঁর মাজারের সদর দরজায় লেখা সম্পূর্ণ নাম- খলিফা হজরত সুলতানুল মাশায়িখ হজরত শায়েখ আঁখি সিরাজুল হক উদ্দিন ইবনে শায়েখ উসমান অউধি। (সিমনানী: ১৯৮৪, ৩৫৫) অযোধ্যা অঞ্চলে জন্মগ্রহণের ফলে অন্যান্যদের মতো তিনিও আওধি উপাধিতে ভূষিত হন। কতিপয় ইতিহাসবিদ তাঁকে বাদায়ুন অঞ্চলের অধিবাসী দাবি করে “বাদায়ুনী” বলেও সম্বোধন করেন।
ঐতিহাসিক প্রমাণ বিস্মৃত হওয়ার কারণে বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, প্রাথমিক জীবনসহ বর্ণনায় প্রতিটি পর্বে পর্বে মতপার্থক্য বিদ্যমান। স্বতন্ত্রভাবে ঐতিহাসিকগণ অনুমান ও সম্ভাব্য ধারণার উপর আঁখি সিরাজের জন্মস্থান – বাদায়ুন/ মাকনপুর/ লখনৌতি/ অযোধ্যসহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী- তিনি ৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। (কিরমানি: ১৯৭৮, ৪০৪) শৈশবকাল অযোধ্যায় অতিবাহিত করে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে মায়ের সান্নিধ্যে বাংলার লখনৌতিতে আসেন। (আশরাফী: প্রাগুক্ত, ৬৬-৬৮)
তাঁর জন্ম ছিল এমন এক পরিবারে— যা জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক বংশধারা থেকে আগত। পারিবারিক পরিবেশ ও জ্ঞানচর্চার ফলে অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে রূহানিয়্যতের চেতনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গৌড়ের তৎকালীন পরিবেশ তাঁর আত্মিক পরিপূর্ণতার পথে সহায়তা করতে পারে নি। সে-সময়ে ভারতবর্ষের ইসলামি আধ্যাত্মিকতা একটি নতুন মাত্রায় পৌঁছেছিল। ১৩শ শতকের শেষভাগ থেকে দিল্লি হয়ে ওঠেছিল ভারতবর্ষের ইসলামী-আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাণকেন্দ্র। বিশেষত, খাজা মইনুদ্দীন চিশতির প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকার সম্প্রসারণ ঘটে তাঁর শিষ্য বখতিয়ার কাকির মাধ্যমে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ও আত্মিক পরিপক্বতার সন্ধানে মাত্র ১৪ বছর বয়সে আঁখি সিরাজ মায়ের অনুমতিক্রমে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী তার লাতায়েফে আশরাফি গ্রন্থে বলেন, দিল্লি যাত্রার সময় আঁখি সিরাজ তখন এতটা ছোট ছিলেন যে, তাঁর মুখে দাঁড়ি-গোঁফ কিছুই ছিল না। (সিমনানী: প্রাগুক্ত, ৫৪৮)
দিল্লিতে এসে তিনি খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। এই বায়আত গ্রহণ প্রসঙ্গে সিরুল আউলিয়া বলেন, “অযোধ্যা ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাঁরা সুলতানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আঁখি সিরাজই ছিলেন সর্বপ্রথম।” (আশরাফী: প্রাগুক্ত, ২০১৮) তিনি দিনের সর্বোচ্চ সময় সুলতানের সান্নিধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। অধিকাংশ সময় তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, দুনিয়াবি চিন্তামুক্ত অবস্থায় নিজেকে একান্তে সুলতানের দরবারে নিবেদিত রাখতেন। প্রতিবছর, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাঁর মাকে দেখতে লখনৌতি যেতেন এবং পরে পুনরায় দিল্লিতে ফিরে এসে সুলতানুল মাশায়িখের সেবা করতেন। তিনি দরগাহ’র জামাআতখানা’র এক কোণে বসবাস করতেন এবং বাকি অংশটা জমায়েত ও মজলিসের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাঁর কাছে কেবল কাগজ ও কিছু বই থাকত—এ ছাড়া কোনো বস্তুগত সম্পদ বা ভোগবিলাস ছিল না। তাঁর সেই বইগুলো কিতাবতখানা ও জামাআতখানাতেই সংরক্ষিত থাকত। (কিরমানি: প্রাগুক্ত, ৪০৪)
এমনভাবেই সুলতানের সেবায় ও সান্নিধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, যেন জীবনের কোনো মূল্যই নেই। একমাত্র মাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পার্থিব বিষয়াদি থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। এভাবেই কাটছে সময়, কতটুকু- তার অনুমান করা বেশ মুশকিল। এই যাত্রার একপর্যায়ে সুলতানুল মাশায়িখ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের উদ্দেশ্যে কিছু যোগ্য শিষ্যদের খেলাফতের জন্য মনোনীত করেন, সেখানে আঁখি সিরাজকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁদের নাম যখন সুলতানুল মাশায়িখের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন:
“খেলাফতের প্রথম শর্ত- জ্ঞানের পূর্ণতা। আঁখি সিরাজের জ্ঞানের স্তরে কিছুটা কমতি রয়েছে।…. অজ্ঞ পীর শয়তানের খেলনা স্বরূপ”।
(প্রাগুক্ত, ৪০৪ ; আশরাফী, প্রাগুক্ত, ১০৬)
কিশোরকাল থেকেই দীর্ঘ সময় নিজামুদ্দীন আউলিয়ার খেদমতে ব্যয়ের পরেও পীরের এমন নির্দেশ আঁখি সিরাজ নতশিরে গ্রহণ করলেও উপস্থিত শ্রোতাগণ হতবাক হয়েছিলেন। সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী বলেন, “আঁখি সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর মধ্যে জ্ঞানের অলংকারের ঘাটতি ছিল না, এরপরও জ্ঞানের ঘাটতিকে তিনি কখনোই লজ্জাজনক মনে করেননি। আধ্যাত্মিক দীক্ষায় আঁখি সিরাজ ইলমে লাদুন্নি বা আভ্যন্তরীণ জ্ঞানে সিদ্ধ হলেও বাহ্যিক, ধর্মীয় বিদ্যায় (প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা পুঁথিগত জ্ঞান) অপূর্ণতা ছিল।” (সিমনানী: প্রাগুক্ত, ৫৪৮)
মুরশিদের এই মন্তব্য আঁখি সিরাজের জীবনের গতানুগতিক গতিবিধি ভেঙ্গে দেয়। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন পুঁথিগত বিদ্যার। বাহ্যিক জ্ঞানের কমতির কারণে খেলাফতের মর্যাদা না দেওয়ার বার্তা সবাইকে বেশ হতবাক করে। বিষয়টি সভায় উপস্থিত থাকা মাওলানা ফখরুদ্দিন জাররাদিকে (যিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন ও তৎকালীন বিখ্যাত পন্ডিত) আশ্চর্য করে, এবং খানিকটা গর্বের সাথে তাৎক্ষণিক খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট আবদার করে বসেন, “আখিঁ সিরাজ অত্যন্ত গুণসম্পন্ন। বাহ্যিক জ্ঞান অধ্যয়নে সে পরিপূর্ণ ও জগৎ-বিখ্যাত হয়ে উঠবে। অনুমতি প্রদান করলে, আমি তাঁকে ছয় মাসেই এক পরিপূর্ণ জ্ঞানী হিসেবে গড়ে তুলবো।” (আশরাফী, প্রাগুক্ত, ১০৮)
সুলতানের অনুমতিক্রমে ফখরুদ্দিন জাররাদির নিকট তিনি অধ্যয়ন শুরু করেন। এ-সময় আঁখি সিরাজের সহপাঠী ছিল সিরুল আউলিয়ার লেখক শায়েখ সৈয়দ মুহাম্মদ কিরমানি। তাঁর সিরুল আউলিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন, “শিক্ষার সূচনালগ্নে আমি ও সিরাজুদ্দিন একইসাথে মিজান, তসরিফ, ক্বাওয়াইদ ও মোকাদ্দিমায়ে তাহকিক অধ্যয়ন করি। শায়েখ ফখরুদ্দিন তাঁর জন্য ‘তসরিফ’ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের নাম দেয়া হয় উসমানি। পাশাপাশি শায়েখ রুকনুদ্দিন ইন্দরপাতির কাছে কাফিয়ায়ে মুফাসসাল (কবিতা ও বাক্য গঠনের উচ্চতর নাহু), কুদুরি (ফিকাহ) ও মাজমাউল বাহরাইন (ফিকাহ ও কালাম সংমিশ্রিত গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেন। এবং স্বয়ং পাঠদানে পারদর্শী হয়ে উঠেন।” (কিরমানি: প্রাগুক্ত, ৪০৪) আঁখি সিরাজ এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেন যে, পরবর্তীতে খোদ আঁখি সিরাজের নিকটই শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাতে লাগলেন।
ফখরুদ্দিন জাররাদি ওয়াদা মোতাবেক, উপযুক্ত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আঁখি সিরাজের ছয়মাসের মধ্যেই আরবি ভাষাজ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানে মাধ্যমিক স্তরের সব কিতাবাদি আয়ত্তের ঘটনা সহপাঠী ও উস্তাদদের আশ্চর্য ও মুগ্ধ করে। পাঠদান শেষে ফখরুদ্দিন জাররাদি, আঁখি সিরাজকে সুলতানের দরবারে উপস্থিত করেন। তখন নিজামুদ্দীন আউলিয়া, আঁখি সিরাজকে পঠিত কিতাবাদিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা থেকে নানা প্রশ্ন করলেন এবং পরীক্ষা নিলেন। তিনি সকল প্রশ্নের যথাযথ ও প্রত্যাশিত উত্তর প্রদান করলে, সুলতান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। (লাহোরী: ১৯৯৪, ২২৬) তখনই নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন এবং একইসাথে তাঁকে ‘আয়নায়ে হিন্দ’ তথা (ভারতবর্ষের দর্পণ) উপাধিতে ভূষিত করেন। খেলাফত প্রদানপূর্বক তাঁকে সম্মানসূচক দরবেশি টুপি ও ‘খিলআত’ (উত্তরীয় বা পাগড়ি) প্রদান করা হয়। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এই খিলআত সবর্দা সাথেই রাখতেন।
খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন এবং সবর্দা “আঁখি” (আমার ভাই) বলেই সম্বোধন করতেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কাছ থেকে ইরাদত ও খেলাফতের শিরোপায় ভূষিত হন।
(আশরাফী, প্রাগুক্ত, ১২৫)
এমতাবস্থায় সুলতান কর্তৃক প্রাপ্ত খিলাফতনামা— যেখানে স্বয়ং সুলতানের মোহর ছিল, তা শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমুদের (চিরাগে দিল্লি) মাধ্যমে মাতৃভূমি অযোধ্যায় পাঠিয়ে, নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে পুণরায় শিক্ষা দীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। (আশরাফী: প্রাগুক্ত, ১২৯) ধর্মজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর নিখাদ আন্তরিকতা। হযরতের ওফাতের পরও তিনি আরও তিন বছর জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং এই সময়টুকু তিনি সুলতানুল মাশায়িখের রওজার গম্বুজের নিচে অবস্থান করেন। তাঁর জ্ঞানলাভের এই অনবদ্য অগ্রগতি সম্পর্কে মুফতি আবদুল খবির, তার সিরুল আউলিয়া গ্রন্থে সৈয়দ মুহাম্মাদ আশরাফি কিসওয়াসাভির সূত্রে বলেন, “তাঁর জ্ঞানপরিধি বোঝার জন্য দেখতে হবে, যুগের প্রথম দিক অতিবাহিত হওয়ার পর, আঁখি সিরাজ শায়েখের নির্দেশ পেয়েই কীভাবে জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হন। আর কীভাবে শায়েখের দোয়ায় নিজেকে কোন্ স্তরে নিয়ে গেলেন।” (কিসওয়াসাভি, ১৯২৪)
সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী আঁখি সিরাজ যখন বাংলার পান্ডুয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখনই ইন্তেকাল করেন তাঁর মুরশিদ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া। মুর্শিদপ্রেমে উদ্বেল সিরাজ তৎক্ষণাৎ দিল্লি ফিরে যান। এবং তাঁর মুরশিদের দরগাহ শরিফেই লাগাতার অবস্থান করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা শায়েখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চিরাগ-ই-দিল্লির নিকট আরও শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। এভাবেই মুরশিদের ইন্তেকালের পর আরো তিন বছর জ্ঞান-সাধনা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও খেলাফতের আরও গভীর স্তরে উপনীত হন। পরবর্তীতে বাংলার খেলাফত পেয়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে সম্মানিত হন। (কাসিম: ২০০৮, ৭৭৬)