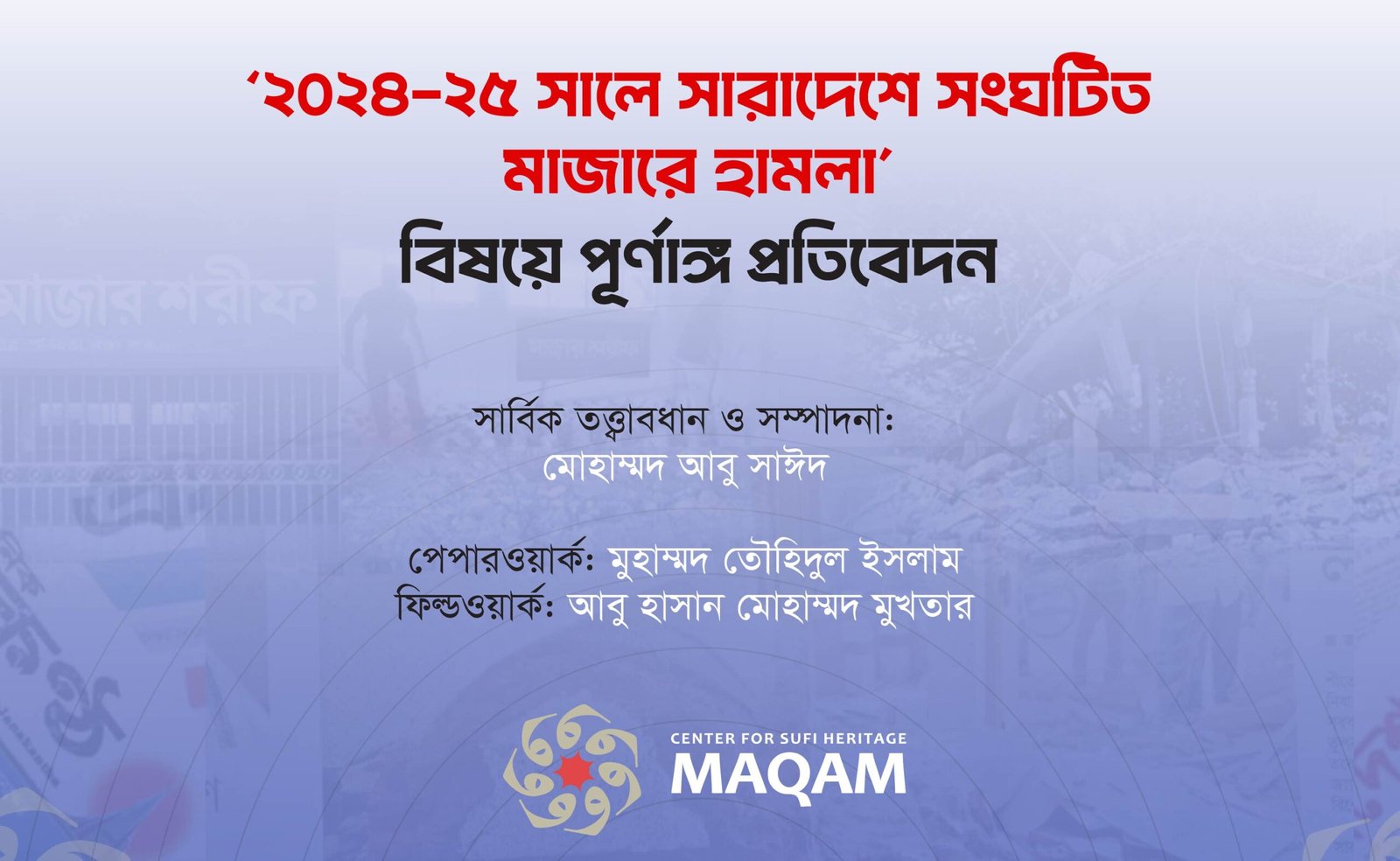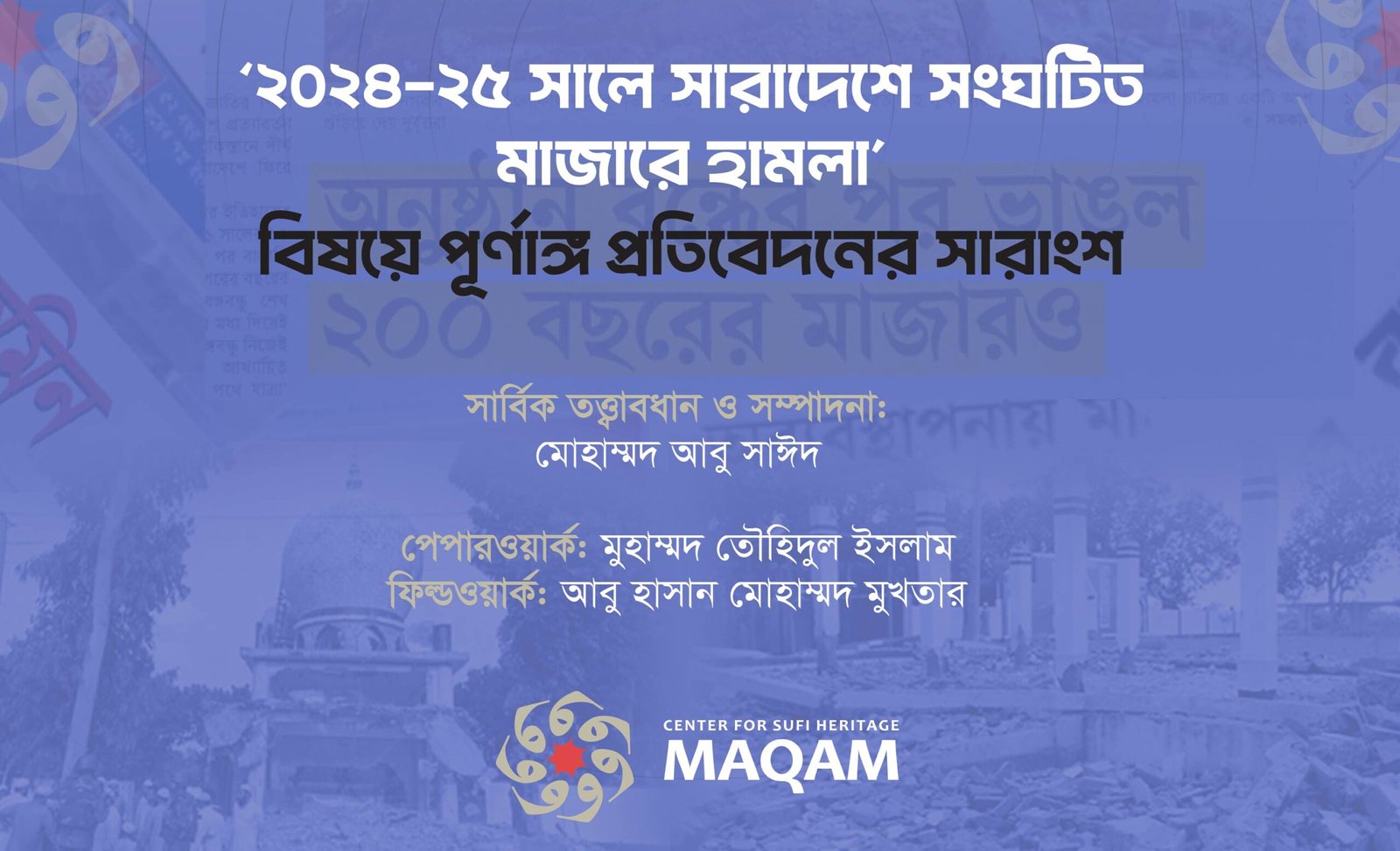১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম। ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর এই ৯ মাসের ইতিহাস কতটা হৃদয়বিদারক তা অবর্ণনীয়। মহান মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির সাথে উঠে আসে ইতিহাসের বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশী দোসরদের কীর্তি নজিরবিহীন গণহত্যার চিত্র। খোদ পাকিস্তানি জান্তা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান সদম্ভে ১৯৭১ সালের মার্চেই ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘ওদের ত্রিশ লাখ হত্যা কর, বাকিরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।” (রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, ১৯৭৩) অর্থাৎ, হত্যার টার্গেট বা নির্দেশক সংখ্যাটি পাকিস্তানিরাই নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো ‘চরমপত্র’। সেই চরমপত্রের শেষ প্রচার দিবস অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি: ‘…২৫ মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালিগো বেশুমার মার্ডার করনের অর্ডার দিয়া কি চোটপাট! জেনারেল টিক্কা খান সেই অর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করল। তারপর বঙ্গাল মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মইদ্দে তৈরি হইল বিচ্ছু…’।
জীবন্ত মানুষের হাত পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলা। চোখ উপড়ে ফেলা। হাত পা বেধে জবাই করা। জীবন্ত মানুষকে জলন্ত চুল্লির মধ্যে ডুকিয়ে দেয়া। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করাসহ নারী ধর্ষণ ছিলো ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশী দোসরদের দৈনন্দিন রুটিন। এই রকম রুটিন ফলো করা একজন বাগেরহাটের রাজাকার নেতা সিরাজ মাস্টার। ১২ আগস্ট ২০১৫ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। ২০১৫ সালে ১২ আগস্টের দৈনিক যুগান্তরের প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ওনার রুটিন ছিল প্রতিদিন সকালে কিছু হিন্দু আর মুক্তিদের নিজ হাতে জবাই করা। তারপর সিরাজ মাষ্টার নাস্তা করতে বসতেন। তার সম্পর্কে খুব প্রচলিত একটা উক্তি ছিলো, জবাই করার আগে সে বলতো, “বাবারা নড়াচড়া করিস না, তোদেরও কষ্ট হয় আমারও কষ্ট হয়”।
সারাদেশে ৯৪২টিরও বেশি বধ্যভূমি না জানি কত নির্মম-নিদারুণ যন্ত্রনা বুকে ধারণ করে আছে। অনেক রক্তের দামে কেনা স্বাধীনতার এই রক্তিম সুর্যোদয়ের পিছনে আছে হাজারো ত্যাগের গল্প। ধর্মের দোহাই দিয়ে যেমনি গণহত্যার পক্ষে বৈধতা উৎপাদন করা হয়েছিলো। তেমনি ঠিক সময় সেই বাংলার সুফি সমাজ মুক্তিযুদ্ধকে জালিম ও মজলুমের লড়াই বলে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে যখন সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল পাকিস্তানের দোসররা। মুক্তিযোদ্ধাদের মালাউন বলছিল; পাকিস্তান রক্ষা না হলে ইসলাম থাকবে না এমন সব মিথ্যা অপপ্রচার করে রাজাকার, আল-বদর, আসশামস, কওমীদের মুজাহিদ বাহিনী সু-সংগঠিত করার চেষ্টা চলছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার গণহত্যার পক্ষে একদল অবস্থান নিয়েছিলো। ঠিক সেই সময়ে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়েও সিরিকোট দরবার শরীফের তৎকালিন পীর গাউছে জামান আল্লামা সৈয়দ তৈয়্যব শাহ রহ.’র ভূমিকা ছিলো নিপীড়িত মজলুম জনতার পক্ষে।
১৯৭১’র এক পত্রে তিনি জানান যে, “ইয়ে দ্বীনি লড়াই নেহী, ইয়ে লোক হক্ব্কে লিয়ে লড় রাহা হ্যায়”- অর্থাৎ: পূর্বপাকিস্তানের মানুষ তাদের অধিকারের জন্য লড়ছেন, এটা কোন ধর্মযুদ্ধ নয়। তাঁর এই একটি চিঠিতেই ছিল সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, যা দরবারে সিরিকোটের মুরীদ-ভক্তদের জন্য ছিল যথেষ্ট।
চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন আল্লামা মুসলেহ উদ্দিন রহ.। তিনি প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে এই চিঠি পাঠ করান, এমনকি হাতে বেত নিয়ে ক্লাস রুম পাহাড়া দিতেন, যেন কেউ মাদরাসা এবং হোস্টেল’র বাইরে গিয়ে দেশ বিরোধীদের সাথে যুক্ত না হতে পারে, রাজাকার-আলবদরে যেতে না পারে।
আল্লামা সৈয়দ তৈয়্যব শাহ’র এমন চিঠি, আর জামেয়ার অধ্যক্ষ’র এই চিঠি অনুসরণে দৃঢ় অবস্থানের কারণে, এশিয়া খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ছাত্ররা রাজাকার না হয়ে, বরং মুক্তিযোদ্ধা হতে পেরেছিলেন। এমন মুক্তিযোদ্ধাদের একজন বর্তমানে চট্টগ্রামের প্রবীনতম আইনজীবী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল সাহেব, যিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য, এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি। অন্য একজন সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, শামসুল হক হায়দারী। যাঁরা উভয়েই এ মাদরাসার ছাত্র ছিলেন, এবং চট্টগ্রাম জামেয়া ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনা কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী কর্মকর্তা ডাক্তার টি হোসেন চৌধুরী পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরী। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তৎকালীন জাতীয় নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ জামেয়ার বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, এবং মুক্তিযুদ্ধে এই মাদরাসার অবদান নিয়ে প্রশংসা করে বক্তব্য রেখেছিলেন।
আল্লামা সৈয়দ তৈয়্যব শাহ কেবল একটা চিঠি দিয়েই দায় সারেননি। বরং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শাহ্ আহমদ নূরানী মারফত তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানে জুলুম বন্ধ করুন এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করুন। পাকিস্তানকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন’। পরবর্তীকালে তিনি নওশেরায় বন্দী শিবিরে আটক সেনাবাহিনীর বাঙালী সদস্যদের দেখতে যান এবং তাদের দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করেন ও আশু মুক্তির জন্য দোয়া করেন।”[1]
তিনি পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশীদের খোঁজ-খবর নেয়া হতে শুরু করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অকৃপণভাবে। সেই কথাই উঠে আসে কর্ণেল (অব) মহসিন সাহেবের মুখ থেকে। কর্ণেল (অব) মহসিন সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের পাথরঘাটায়। থাকেন ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএসে। একবার কোরবানিগঞ্জের বলুয়ারদীঘিপাড়স্থ খানকাহ-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া অফিসে তিনি বলেছিলেন যে, ১৯৭১’র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তানের নওশেরার বন্দিশিবিরে আটক ছিলেন। এসময় হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বন্দী বাঙালিদের দেখভাল করতে নিয়মিত সেই জেলখানায় যেতেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করতেন। তিনি (কর্ণেল মহসিন) সেই অসহায় সময়ে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ হুজুরের সহায়তা এবং সান্ত্বনার কথা স্মরণ করে এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলেন।[2]
চট্টগ্রামের আরেকটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হলো আহলা দরবার শরীফ। এই দরবারের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তি ও পরিবার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিশেষত চট্টগ্রাম বোয়ালখালী অঞ্চলে গোপাল কৃষ্ণ দাশের মতো মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আহলা দরবার শরীফের পীর সাহেব আল্লামা সৈয়দ আবু জাফর মোহাম্মদ সেহাব উদ্দিন খালেদ রহ. হতে। এই দরবারটি মাইজভাণ্ডারের সিলসিলা থেকে আগত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার শরীফের ভূমিকা ছিলো ব্যাপক। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও রুহানী ভূমিকার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্বস্ত বিবরণ উঠে এসেছে খ্যাতিমান পেশাদার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোঃ মাহবুবউল আলমের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গ্রন্থে।
একাত্তরের মার্চের শেষভাগ এবং এপ্রিলের শুরুর সময়টা ছিল ভয়াবহ। অপারেশন সার্চলাইটের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখনো পুরো নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, চারদিকে চলছে কারফিউ, হত্যা আর অগ্নিসংযোগ। ঠিক এই সময়েই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে আসে এক ঐতিহাসিক ও সাহসী নির্দেশনা। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল (২২ চৈত্র), হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান শাহ (বাবাভাণ্ডারী)-এর পবিত্র ওরশ শরিফ।
তৎকালীন আধ্যাত্মিক নেতা বা গদিনশীন পীর ভক্তদের নির্দেশ দিলেন, পরাধীন দেশে থেকেও বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা তৈরি করে মিছিল সহকারে ওরশে আসতে হবে।[3] সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা সেদিন হাতে লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে মাইজভাণ্ডারে সমবেত হয়েছিলেন।
দরবার প্রাঙ্গণে ওই পতাকা প্রকাশ্যে উত্তোলন করা হয়। শুধু তাই নয়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের শাখা দরবারসহ প্রত্যেকটা মাইজভাণ্ডারী ভক্তের গৃহ হয়ে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টার, ঘাঁটি।
খাগড়াছড়ি জেলার ময়ূরখিলে দরবারের খামারগুলো এবং ফটিকছড়ির খিরামের সৈয়দ লকিয়ত উল্লাহর খামারগুলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ট্রানজিট ক্যাম্প। যুদ্ধের ময়দানে রসদ বা লজিস্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাইজভাণ্ডার দরবারের নির্দেশে এসব খামারের পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাক-সবজি, হাঁস-মুরগি এবং গবাদিপশু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অপারেশন শেষ করে এসব খামারে বা খানকায় আশ্রয় নিতেন, বিশ্রাম নিতেন এবং পরবর্তী অপারেশনের পরিকল্পনা করতেন। এই আশ্রয় ও খাবারের যোগান দিতে গিয়ে দরবারকে চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একাধিকবার এসব কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে বহু মাইজভাণ্ডারী ভক্ত ও মুরিদকে নির্যাতন সইতে হয়েছে, এমনকি অনেকে শহীদও হয়েছেন। তবুও এই ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব রেজিস্ট্যান্স’ বা প্রতিরোধের অবকাঠামো ভেঙে পড়েনি।
শাহ সুফি হযরত সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা সহ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। ফটিকছড়ি নানুপুর নিবাসী মুক্তিযোদ্ধা মন্টু কাওয়াল বলেন, ‘হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী আমাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) নিয়ে হজরত কেবলা ও বাবাভাণ্ডারী কেবলার মাজারে জেয়ারত করে সকল মুক্তিযোদ্ধা সহ দেশের জন্য দোয়া করতেন’। যুদ্ধকালীন ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’ লেখা একটি পোস্টার মাইজভাণ্ডারে লাগানো ছিল। অসিয়ে গাউসুল আজম বৃদ্ধাবস্থায় নিজ হাতে তুলে নিয়ে পেরেক ঠুকে দেয়ালে লাগিয়ে দেন। শাহানশাহ হজরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর নিকট মুক্তিযোদ্ধারা দোয়া চাইতে আসলে তিনি বলতেন, ‘অধিকার কেউ সহজে দেয় না, কেড়ে নিতে হয়’। তিনি যুদ্ধে সাহস রাখার জন্য প্রেরণা দিতেন।
মুক্তিযুদ্ধে সুফিদের অবদানের ধারাবাহিকতায় ফটিকছড়ি পূর্ব ফরহাদাবাদ (নাজিরহাট) মতিভাণ্ডার দরবার শরিফও ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ও ট্রানজিট ক্যাম্প। এ দরবারের অগণিত ভক্ত মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। মতিভাণ্ডার দরবার শরিফের সুফি (দরবারের সাজ্জাদানশিন) হযরত মওলানা আবুল ফয়েজ শাহ্ রহ. ও হযরত আবুল কাসেম মিঞা শাহ্ রহ. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়সহ আহার-আপ্যায়ন করাতেন।[4]
লেখক সিরু বাঙালি তার বাঙাল কেন যুদ্ধে গেল বইয়ে অকৃপণভাবেই তুলে ধরেন মহান মুক্তিযুদ্ধে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া এবং এই মাদরাসা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে বিশ্বাসী সুন্নী আলেমদের অবস্থান: “সকল মৌলবি মৌলানাকে গড়পরতা রাজাকার-আলবদর বলে দোষারোপ করলে, ১৯৭১ সালে যে সব মৌলানা মৌলবি স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন, রাজাকার-আলবদর গঠনের ব্যাপারে যারা বাধা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি চট্টগ্রামের স্বনামধন্য পীরে তরীকত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আল্লামা আলহাজ্ব কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী, মৌলানা আব্দুর রহমান আল কাদেরী, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মৌলানা মোসলেহ উদ্দিন সাহেবের নাম স্মরণ করতে পারি। যাঁরা ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের ৩টি বৃহৎ মাদ্রাসা জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও ওয়াজেদীয়া আলিয়া মাদ্রাসায় রাজাকার গঠনে বাধা প্রদান করেছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন।”[5] ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী রহ. ছিলেন দরবারে হাশেমীয়া আলিয়ার সাজ্জাদানশীন পীর এবং বাংলাদেশে সুফিধারার সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আমৃত্যু সভাপতি। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও পরামর্শে এক বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। যা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। তদানিন্তন আলেম সমাজের চিরচারিত পাকিস্তান তোষন নীতির ব্যতিক্রম হিসেবে স্বাধনীতার সরাসরি সমর্থন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-পশ্রয় দিয়েছেন ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশেমী।[6]
আরো অনেক দরবার তাদের ভক্ত-মুরিদানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী দরবার সাতগাছিয়া। এই দরবারের সদ্য প্রয়াত পীর হযরত সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মোস্তাক বিল্লাহ সুলতানপুরী রহ. নিজেও মুক্তিযুদ্ধের একজন সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন। কুমিল্লার সাবুরিয়া দরবারের পীর গাজী এম.ওয়াহিদ সাবুরী সাহেব মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন সম্মুখযোদ্ধা।
রণাঙ্গনের আরেক সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ঢাকার দেওয়ানবাগের পীর বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী। তার আকিদা এবং বক্তব্যের বিষয়ে বেশ কিছু দ্বিমত ও জোরালো আপত্তি থাকলেও, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণ ও সাহসী ভূমিকার স্মরণ না করলেই নয়। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর তিনি প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে রিফিউজি বা শরণার্থীদের সহায়তা ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে কেবল দেশীয় অস্ত্র ও মনোবল দিয়ে যে টিকে থাকা সম্ভব নয়, তা তিনি দ্রুতই অনুধাবন করেন। ফলে সশস্ত্র যুদ্ধের পথ বেছে নেয়া তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একাত্তরের ১১ এপ্রিল, অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠনেরও পূর্বে, তিনি ৭২ জন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেড্ডায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। তার এই যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুপরিকল্পিত। পরবর্তীতে তিনি তেলিয়াপাড়ায় ৩ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে যান এবং সেখানে নির্বাচিত ৬০ জন যুবকের একটি প্লাটুনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার অবদানের বিষয়টি কেবল মুখের কথা নয় বরং দালিলিক প্রমাণসিদ্ধ। ভারতীয় রেকর্ড অনুযায়ী, তার ক্রমিক নম্বর এমএফ ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা নং-১১। অন্যদিকে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর ক্রমিক নম্বর ৩৪০৬৬। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র এবং সমসাময়িক সেনা কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, তিনি ছিলেন ৩ নম্বর সেক্টরের ‘এস’ ফোর্সের অধীনে একজন অত্যন্ত সক্রিয় প্লাটুন কমান্ডার। মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তিনি দীর্ঘ আড়াই মাস সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।
দেওয়ানবাগীর যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর তিনি সফল ‘টার্গেট অ্যাটাক’ পরিচালনা করেন। এই অপারেশনের সাফল্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এরপর মে মাসজুড়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নেন। এর মধ্যে ১১ মে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে অ্যামবুশ, ১২ মে মাধবপুরের বাগসাইর গ্রামে অ্যামবুশ এবং ১৬ মে তেলিয়াপাড়া ও চুনারুঘাট মহাসড়কে অ্যামবুশ পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ২৮ এপ্রিল মাধবপুর যুদ্ধ এবং ১৫ জুন মনতলা-হরষপুর যুদ্ধে তিনি সম্মুখভাগে থেকে লড়াই করেন। প্রতিটি অপারেশনে তার রণকৌশল এবং সাহসিকতা ছিল প্রশংসাযোগ্য। যুদ্ধের একপর্যায়ে ৩ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহ ১ নম্বর সেক্টরে (ত্রিপুরা/ধর্মনগর) একটি কোম্পানি পাঠানোর কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই বিশেষ কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে মাহবুব-এ-খোদা তথা দেওয়ানবাগী হুজুরকে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানের সান্নিধ্যে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন।[7]
ঢাকার অন্যতম প্রাচীন দরবার নারিন্দার মশুরীখোলা। এই দরবারটি পাশেই গৌড়িয় মঠ। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর হামলা থেকে মশুরীখোলা দরবার শরীফের তৎকালীন পীর সাহেব সেই মঠ রক্ষা করেছিলেন এবং অসংখ্য মানুষকে দরবারে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কে দরবারে পীর আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আহছানুজ্জামান রহ. বলেন, “১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে একদিন বিকাল বেলা (বাদ আছর) শাহ সাহেব লেনের পশ্চিম মাথায় হিন্দু মন্দিরে হামলা করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনির কিছু সংখ্যক সৈনিক আসে। তখন একদল বিনা অনুমতিতে দরবার শরীফে তাদের গাড়ী নিয়ে প্রবেশ করে। গাড়ী ঘুরিয়ে রাখার পর মসজিদ, মাজার শরীফ দেখে চলে যেতে চাইল, এমন সময় তাদের গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়! অনেক চেষ্টার পরও গাড়ী স্টার্ট নেয় না এবং জায়গা থেকে সরাতে পারছিল না, তখন তারা দরবারের তৎকালিন পীর হযরত শাহ আবদুল লতিফ রহ.’র নিকট এসে ক্ষমা চায়। তিনি বলেন হযরত কেবলার মাজার শরীফে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। গাড়ি ধাক্কিয়ে গেইটের বাহিরে নিয়ে যায়, গেইটের বাহিরে নেওয়ার পর গাড়ী স্টার্ট নেয় এবং তারা চলে যায়, এরপর আর কখনও পাকিস্তানী সেনারা দরবার শরীফে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক প্রতিবেশিও দরবার শরীফে আশ্রয় নিয়েছিল।”[8]
শুধু মশুরীখোলা দরবারই নয় এই দরবারের আরেকটি শাখা হযরত ক্বেবলা শাহ মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ রহ.’র খলিফা সৈয়দ শাহসুফি আবু আহমদ রহ.’র প্রতিষ্ঠিত ফেনীর ঐতিহ্যবাহী নিজপানুয়া দরবার শরীফও মুক্তিযুদ্ধের আরেক শেল্টার হাউজ। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় এবং সাহায্য সহযোগিতার কথা ছাগালনাইয়ার সকলেরই জানা ছিলো। দরবারের শাহজাদা সৈয়দ আবুল ফজল মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ লিখেন, “১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আমিও বাড়ী ছিলাম। একদিন হঠাৎ বড় এক কাফেলা পাঞ্চাবী মিলিশিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী ঘেরাও করিল। কমাণ্ডার কেবলা পাকের খানকার সমানে ভারী অস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অপরদিকে বাড়ীর ভিতর আনাচে কানাছে অন্যান্য সেনারা তল্লাশী করিতেছিল। বাড়ীর উঠানে প্রত্যেক ঘরের সামনে ২/১ জন করিয়া মোতায়েন ছিল। বড় ভাই সাহেব এবং আমি বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে ছিলাম এবং কমান্ডারকে লক্ষ্য করিতে ছিলাম। বাড়ীর সব অনড়। কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। বাড়ীর পিছনে ঝোঁপ ঝাড় তল্লাশী হচ্ছিল। কেবলা পাক নিজ খাটের উপর চাদর মোড়াইয়া শুইয়া আছেন। কমান্ডার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল এবং কেবলা পাকের থাকার দিকে ইশারা দিল। ইয়ে কেয়া দোকান হায়। কমাণ্ডার বলিল কোন পীর সাহেব। উত্তর দিলাম জাকে দেখো (যাইয়া দেখ) সে ভিতর গেল কেবলা পাকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল হুজুর হামকো দোয়া করো। (আমাদের দোয়া করুন) এই বলিয়া বন্দুকের নল নিচের দিকে দিয়া বাহিরে আসিয়া হুইসাল দিয়া সকলকে যাইবার আদেশ দিল। আমাদের অকস্মাৎ এই ঘেরাউয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল- এখানে মুক্তির খুঁটি আছে বলিয়া আমাদের রিপোর্ট ছিল।”[9]
প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীরে শরীয়তপুরের নড়িয়াতে অবস্থিত ‘সুরেশ্বর দরবার শরীফ’ ছিল তেমনই এক অলিখিত দুর্গ, যা পাকিস্তানি হানাদারের চোখের সামনে থেকেও হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক অদৃশ্য অভয়ারণ্য। একাত্তরের উত্তাল সময়। পদ্মা তখন কেবল নদী নয়, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ। সেই পদ্মার পাড় ঘেঁষেই সুরেশ্বর দরবারের অবস্থান। ভৌগোলিকভাবেই এই স্থানটি কৌশলগত কারণে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে উত্তাল নদী, অন্যদিকে স্থলপথ—গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য এর চেয়ে আদর্শ ট্রানজিট পয়েন্ট আর হতে পারতো না।
সুরেশ্বর দরবার শরিফ শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর গ্রামে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন শামসুল উলামা আল্লামা হজরত শাহ সুফি সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হজরত জান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী রহ.। তাঁর দর্শন ছিল, “জালেমের কাছে মাথা নত করা সুফিবাদ নয়।” একাত্তরে তাঁর বংশধর এবং দরবারের খাদেমরা সেই দর্শনকেই বুকে ধারণ করেছিলেন।
যখন নড়িয়া ও পালং থানার বিভিন্ন গ্রামে পাকিস্তানি আর্মি আগুন জ্বালাচ্ছে, তখন রাতের অন্ধকারে নদী সাঁতরে বা ছোট নৌকায় করে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধারা ভিড় জমাতেন এই দরবারের ঘাটে। দরবার শরীফ তখন আর কেবল জিকির-আসকারের জায়গা ছিল না, এটি হয়ে উঠেছিল এক বিশাল ‘লঙ্গরখানা’ ও ‘লজিস্টিক হাব’। শত শত মুক্তিযোদ্ধার খাবারের ব্যবস্থা হতো দরবারের পাকশালা থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষ্যমতে, সুরেশ্বর দরবার ছিল তাদের জন্য ‘মানসিক রিচার্জ সেন্টার’।[10]
ঢাকার ক্র্যাক প্লাটুনের একজন গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন আজাদ। মুক্তিযুদ্ধের মাঝখানে আগস্ট মাসে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লেন তিনি। হানাদাররা তথ্য জানার জন্য অকথ্য নির্যাতন করত। নির্মম অত্যাচারের মুখেও আজাদ কিছু বলেননি। তখন তার মাকে বলা হয়, ছেলে যদি সবার নাম-পরিচয় বলে দেয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তা শুনে আজাদের মা ছুটে গেলেন আজাদের কাছে। না, ছেলেকে মুক্ত করার জন্য নয়! বরং তিনি আজাদকে বললেন, “বাবারে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থেকো। সহ্য করো। কারো নাম যেন বলে দিও না।” আজাদ তাকে কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন জেলের দুর্বিষহ জীবনের কথা, প্রচণ্ড নির্যাতনের কথা। আরও বলেছিলেন, “মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুইদিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিয়েছিল, আমি ভাগে পাই নাই।” আজাদের মা তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, “কালকে আমি ভাত নিয়ে আসবো।”
কথামতো ভাত নিয়ে গিয়েছিলেনও তিনি। কিন্তু আজাদ চলে গিয়েছিল না ফেরাদের দেশে। আর কখনোই তিনি আজাদকে খুঁজে পাননি। আজাদের মা যাওয়ার পরপরই আজাদকে জেল থেকে সরানো হয়। তারপর ১৪ বছর বেঁচেছিলেন সাফিয়া বেগম। প্রতীক্ষায় ছিলেন তার ছেলের ফিরে আসার জন্য। কিন্তু আজাদ আর ফেরেননি। আজাদের শোকে স্বাধীনতার পর যে ক’বছর বেঁচে ছিলেন আর কখনও তিনি ভাত খাননি, হাপাঁনী থাকা সত্ত্বেও শোতেন মাটিতে, মাদুর বিছিয়ে। কারণ তার ছেলে মৃত্যুর আগে জেলে মাদুরে শুতেন। ১৯৮৫ সালের ৩০ শে আগস্ট, মারা যাওয়ার আগেই তিনি বলে গিয়েছিলেন তার কবরের ফলকে পরিচয় হিসেবে লিখতে ‘শহীদ আজাদের মা’। তাই আজও জুরাইনে একটি কবর দেখা যায়। যাতে লেখা ‘মোসাঃ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা’। মুক্তিযুদ্ধের আরেক গেরিলা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কাছে থেকে সংগৃহীত এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে আনিসুল হক রচনা করেন তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘মা’। এই উপন্যাসে উঠে আসে মুক্তিযদ্ধের আরেক ইনফ্লুয়েন্সার ঢাকা ঐতিহ্যবাহী জুরাইন মাযার ও দরগাহ্’র পীর হযরত কামরুজ্জামান চিশতী রহ.’র কথা। আনিসুল হক লিখেন, “সাফিয়া বেগম যতটুকু বোঝেন, রেডিও শুনে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে, ছেলেদের আলোচনা শুনে, বাসায় আগত লোকদের কথাবার্তা যতটুকু তার কানে আসে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে, আর পুলিশ সুবেদার খলিলের বয়ান শুনে, তাতে পাঞ্জাবিদের এই জুলুম মেনে নেওয়া যায় না, মেনে নেওয়া উচিত না। তিনি ছেলেকে মানুষ করেছেন কি নিজে ছেলের আয়-রোজগার আরাম করে ভোগ করবেন বলে! কখনো নয়। এটা তিনি ছেলেকে চিঠিতেও লিখে জানিয়েছেন, ছেলেকে তিনি মানুষ করেছেন মানুষের যা কিছু কর্তব্য তাই করবে বলে। দেশ আর দশের কাজে লাগবে বলে।
অমঙ্গল-আশঙ্কায় আবার তাঁর বুক কেঁপে ওঠে, সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। যদি ছেলের কিছু হয়। তিনি কল্পনা করার চেষ্টা করেন, কেউ এসে তাঁকে খবর দিচ্ছে যে তার ছেলের গায়ে গুলি লেগেছে, না, তিনি কল্পনা করতে পারেন না, অশ্রুর প্লাবন এসে তাঁর দু’চোখ আর সমস্ত ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
একজন কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কার সঙ্গে। হঠাৎই মায়ের মনে পড়ে যায় জুরাইনের পীর সাহেবের কথা। বড় হুজুর আর তাঁর স্ত্রী দুজনই বড় ভালো মানুষ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই তো চলে। মা সকালবেলা রওনা দেন জুরাইন মাজার শরিফ অভিমুখে। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ছেলে যুদ্ধে যেতে চায়, তিনি কি অনুমতি দেবেন?
পীরসাহেব বলেন, ‘ছেলেকে যেতে দাও। পাকিস্তানিরা বড় অন্যায় করতেছে। জুলুম করতেছে। আর তা ছাড়া, ছেলে বড় হলে তাকে আটকায়া রাখার চেষ্টা করে ফল নাই। তুমি না করলেও সে যুদ্ধে যাবেই।’ মায়ের মন থেকে সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়। ফিরে এসে তিনি আজাদকে ডাকেন। বলেন, ‘ঠিক আছে, তুই যুদ্ধে যেতে পারিস। আমার দোয়া থাকল।’ ছেলে মায়ের মুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে, মা কি অনুমতিটা রেগে দিচ্ছেন, নাকি আসলেই দিচ্ছেন। ‘মা, তুমি কি অন্তর থেকে পারমিশন দিচ্ছ, নাকি রাগের মাথায়?’ ‘আরে রাগ করব ক্যান। দেশ স্বাধীন করতে হবে না?’ ‘থ্যাঙ্ক ইউ মা। আমি জানি তোমার মতো মা আর হয় না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটা গান হয় না, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা… তুমি হলে সেই মা।’[11]
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বহু দরবার-খানকাহ ও মাযার পরিণত হয় শেল্টার হাউজে। এর পরিণয়ে তাঁদের উপর নেমে আসে নির্মমতা। তেমনি বর্বরতার শিকার হয়েছিলো কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার গোলাপনগরের শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সোলাইমান শাহ্ চিশতী রহ.। তিনি ছিলেন একাত্তরের রণাঙ্গনের এক নিভৃতচারী শহীদ। তাঁর সম্পর্কে আরিফ রহমান লিখেন, ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কুষ্টিয়া অঞ্চল ছিল এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধ বা ‘ব্যাটল অব কুষ্টিয়া’র কারণে পাকিস্তানি বাহিনী তখন দিশেহারা এবং ক্ষিপ্ত। তারা তখন কেবল মুক্তিযোদ্ধা খুঁজছে না, খুঁজছে ওইসব মানুষদের যারা সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় (সম্ভাব্য ১২ এপ্রিল)। পাকশী ব্রিজ বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দিক থেকে পাকিস্তানি হানাদারেরা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করে ভেড়ামারায়। তাদের গন্তব্য ছিল গ্রামগুলো তছনছ করা। একপর্যায়ে এই নরপিশাচদের দল হানা দেয় গোলাপনগরের সেই শান্ত কুঁড়েঘরটিতে। সাধারণত যুদ্ধের সময় মানুষ জান বাঁচাতে পলায়ন করে। কিন্তু সোলাইমান শাহ্ ছিলেন ভিন্ন ধাতের মানুষ। তিনি জানতেন, তার ভক্তরা, তার মুরিদরা ভীতসন্ত্রস্ত। তিনি পালিয়ে গেলে এই সাধারণ মানুষগুলোর মনোবল ভেঙে যাবে। তাই তিনি তার আস্তানাতেই অবস্থান করলেন। সঙ্গে ছিলেন তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৮ জন সহচর বা মুরিদ। হানাদার বাহিনী যখন তার কুঁড়েঘর ঘেরাও করল, তখনো তিনি শান্ত। কোনো অনুনয় নয়, কোনো বিনয় নয়। একাত্তরের সেই বিকেলে গোলাপনগরের মাটি সাক্ষী হলো এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডের। পাকিস্তানি হায়েনারা সোলাইমান শাহ্ এবং তার ৮ জন নিরস্ত্র সঙ্গীকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সাধকের বুক। লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং তার সহচরেরা। পদ্মা তীরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে বারুদের গন্ধে আর শহীদের রক্তে।[12]
আরেক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় বগুড়া শহর থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার উত্তরে গোকুল ইউনিয়নের রামশহর গ্রামে। এই গ্রামেই অবস্থান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত পীর পরিবারের, যার গোড়াপত্তন করেছিলেন সুফি সাধক ডা. কহর উল্লাহ রহ.।
১৯৭১ সাল মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করাও ইমানের অঙ্গ। পরিবারের চারজন সদস্য, শহীদ বেলায়েত হোসেনের ছেলে মাকসুদুর রহমান ঠান্ডু, ভাতিজা শহীদ আব্দুস সালাম লালু, জিল্লুর রহমান জলিল ও ভাগ্নে তোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ সরাসরি যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। পীর বাড়ির ছেলেরা ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করছেন- এই খবরটি পাকিস্তানি বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকারদের জন্য হজম করা কঠিন ছিল। কারণ, তারা চেয়েছিল পীর-মাশায়েখদের ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু রামশহরের পীর পরিবার ওই ছকে পা দেয়নি; তাঁরা ছিলেন মজলুম জনতার পক্ষে।
১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর। রমজান মাস। রামশহর পীর বাড়িতে চলছে সেহরির প্রস্তুতি। তখন বাড়িতে ঢুকেই হায়েনারা চিৎকার করে খুঁজতে থাকে, “মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়? বন্দুক কোথায়?” ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান সবাই। পীর সাহেবের ছোট ভাই মো. তবিবুর রহমান পরিস্থিতি বুঝে খাবার রেখেই প্রাচীর টপকে পালানোর চেষ্টা করেন। হানাদাররা তাকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি ছোড়ে। অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান এবং অন্ধকারের থাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনিই পরবর্তীকালে এই রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হন। পীর সাহেব শহীদ বেলায়েত হোসেন, তার ভাই দবির উদ্দীন, হাবিবুর রহমান এবং সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোর জাহিদুর রহমান মুকুলসহ মোট ১১ জনকে পিঠমোড়া করে বেঁধে উঠানে দাঁড় করানো হয়। এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় তখন।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পীর বেলায়েত হোসেন হানাদারদের কাছে শেষ মিনতি করলেন, “আজান হয়েছে, আমাকে অন্তত দুই রাকাত ফজরের নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। আমি আমার রবের পায়ে সিজদা দিয়ে মরতে চাই।” কিন্তু যারা ধর্মের নামে মানুষ মারে, তাদের কাছে ধর্মের কোনো মূল্য নেই। পাকিস্তানি জল্লাদরা ওই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। যে বাহিনী নিজেদের ‘মুসলিম আর্মি’ বলে দাবি করত, তারা একজন রোজাদার পীরকে ফজরের নামাজটুকুও পড়তে দেয়নি।
আজান শেষ হওয়ার আগেই পীর বাড়ির পুকুর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয় ১১ জন মানুষকে। ডা. কহর উল্লাহর তিন ছেলে, বেলায়েত, দবির ও হাবিবুর; নাতি সালাম, খলিলুর ও কিশোর মুকুল; এবং প্রতিবেশী আরও চারজন। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে ওঠে অটোমেটিক মেশিনগান। ব্রাশফায়ারের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে রামশহরের মাটি। সেহরির পবিত্র মুহূর্তে ১১টি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ে পুকুর পাড়ের মাটিতে। পুকুরের পানি আর ভোরের শিশিরভেজা ঘাস লাল হয়ে যায় শহীদের রক্তে। লাশগুলো ওভাবেই ফেলে রেখে উল্লাস করতে করতে চলে যায় হানাদাররা।[13]
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ জালিম ও মজলুমের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিলো। সুফি-সাধকরা শান্তি সৌহার্দ্য আর ইসসাফের জন্য কাজ করেন। হযরত শাহ্ জালাল ইয়েমানী রহ., বাবা আদম শহীদ রহ., শাহ মখদুম রূপোশ রহ.’র মত অগণিত আউলিয়ায়ে কেরাম জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁদের উত্তরসুরীগণ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও ছিলো সোচ্চার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়লে সেখানে দেখা যায়, এটা একটা ধর্ম যুদ্ধ। যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী। কিছু ধর্মীয় নেতা, কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলাম-নেজামে ইসলাম পার্টি আর ধর্মীয় পরিভাষাযুক্ত পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল বদর ও আলশামসকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিল, তখন বাংলার আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বা সুফি দরবারগুলো কেবল নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি, বরং বাংলার মুসলমানকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এটা জালেম-মজলুমের লড়াই এবং এখানে যারা ধর্মরক্ষার নামে গণহত্য চালাচ্ছে তারাই জালেম। উল্লেখিত দরবারগুলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তরিকত-নেটওয়ার্ক একাত্তরে গড়ে তুলেছিল এক অনন্য ‘আধ্যাত্মিক ও লজিস্টিক ফ্রন্ট’। এই দরবারগুলো স্টেনগানধারীদের রুটি, আশ্রয় এবং মানসিক সাহস যুগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এক শক্ত খুঁটি হিসেবে কাজ করেছেন।
বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট মুক্তিযুদ্ধে জালেম পাকিস্তানী জান্তার বিরুদ্ধে মজলুম জনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে বাংলার সুফি সমাজ ইতিহাস সৃষ্টি করেননি, বরং ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। সিলেটে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেভাবে ইনসাফের জন্য লড়াই করেছেন হজরত শাহজালাল, বাবা আদম শহীদ যেভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে, রাজা গণেশের সঙ্গে যেভাবে সুলতানী আমলের রাষ্ট্ররক্ষার লড়াই করেছেন হজরত নূর কুতুবুল আলম তেমনি তাঁদের উত্তরসূরী পীর-মাশায়েখ মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর মজলুম জনতার পাশে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। এত দেশি, বিদেশি ষড়যন্ত্রের পরও কেন বাংলাদেশের গণমানুষের কাছ থেকে সুফি সমাজ ও তাঁদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাজার, দরগাহ, খানকাহকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তার উত্তর এখানেই নিহিত রয়েছে।